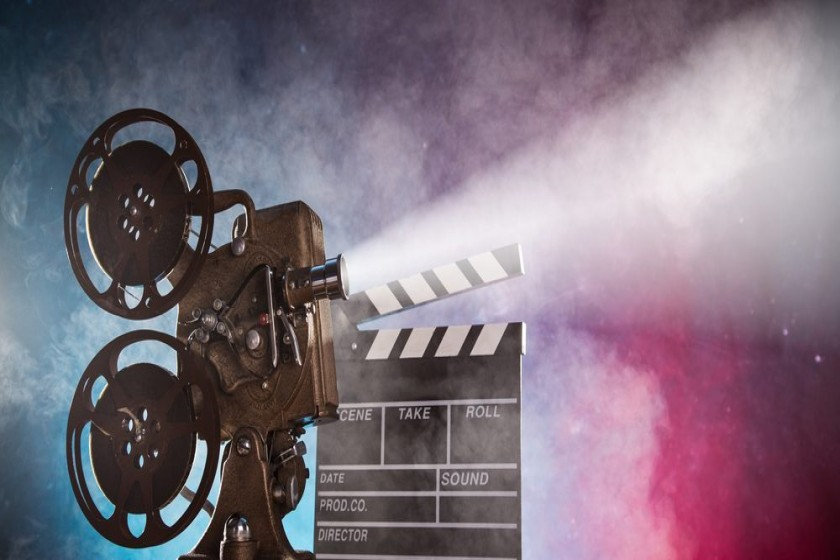
রাষ্ট্র, রাজনীতি ও তথ্যচিত্র
রাজনৈতিক তথ্যচিত্র নির্মাণ ও চলচ্চিত্রের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছিল সেই হীরালাল সেনের সময় থেকেই। তিনি ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জের আগমন এবং কলকাতা ও দিল্লির দরবারের ছবি তুলেছিলেন সরকারি আমন্ত্রণে। সেই ছবি ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে দু’দিন দেখানোর পর নিষিদ্ধ হয়েছিল। আবার বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ওই বিষয়ের ওপর ছবি হলে রক্তচক্ষু দেখায় সরকার। অর্থাৎ প্রথম থেকেই ছবি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের বাধার সম্মুখীনও হয়েছে।
শুধু ব্রিটিশ আমলে নয়, স্বাধীনতার পরেও গণতান্ত্রিক ভারতেও ছবি করতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন রসোলিনি, সুখদেব, আনন্দ পট্টবর্ধন, তপনকুমার বসু, সত্যজিৎ রায়, সুমন ঘোষের মতো আরও অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন পরিচালকের ছবি। কারণ রাজনৈতিক ছবি সব সময় একটি পক্ষকে সমর্থন করে এবং অবশ্যই সমাজের নিপীড়িত শ্রেণিকেই সমর্থন করে। আর নিপীড়ক যদি হয় রাষ্ট্র নিজেই সেক্ষেত্রে ছবি হয়ে যায় নিষিদ্ধ। ছবির মধ্য দিয়ে জনজীবনের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরলে পরোক্ষ ভাবে শাসক দলের প্রকৃত চেহারাও প্রকাশ পায়। আর শাসকের ব্যর্থতা জনসমর্থন হ্রাস করতে পারে বলে ভয়ে রাজনৈতিক চক্রান্ত শুরু হয়, তথ্যচিত্র নিষিদ্ধ হয়।
বিদেশেও রাজনৈতিক তথ্যচিত্রের প্রদর্শনকে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বারবার। বাধা পেয়েছে আমেরিকার ফ্রেডরিক ওয়াইজম্যান, চার্লি চ্যাপলিন, আর্জেন্টিনার রাইমুন্দ, ফারনান্দো সোলোনাস, রাশিয়ার আন্দ্রেই তারকোভস্কি, বাংলাদেশের জহির রায়হান, তারেক মাসুদ, চেকোস্লোভোকিয়ার ভেরা চিটিলোভা, ইরানের জফর পানাহি, চিলির মিগুয়েল লিটনের মতো বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকের ছবি। নব্য ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যে লড়াইটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়েছিল সে লড়াইটা গোটা বিশ্বে চলছে আজও। ‘ডিরেক্ট সিনেমা’র প্রবর্তক মার্কিন পরিচালক ফ্রেডরিক ওয়াইজম্যান ১৯৬৭ সালে ‘টিটিকাট ফলিজ’ ও ১৯৬৮ সালে ‘হাই স্কুল’ ম্যাসাচুসেটসের সরকার প্রতিশ্রুত মানসিক হাসপাতালের অসুস্থ অসহায় মানুষগুলি সেবা যত্নের পরিবর্তে হেনস্থা ও লাঞ্ছনার শিকার এবং ফিলাডেলফিয়ার একটি স্কুলের বিদ্যালয়কর্মীদের সংকীর্ণ মানসিকতা ও শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্য দেখিয়ে প্রশাসনের মুখোশ খুলে দিয়েছিল। এই ছবিগুলো শাসকদল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে শাসক পরিচালককে চিহ্নিত করে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। ‘হাউ টু মেক মুভিজ’ (১৯১৮) তথ্যচিত্রের পরিচালক চার্লি চ্যাপলিন চক্রান্তের শিকার হন ‘ব্যতিক্রমী’ কাহিনিচিত্রের মাধ্যমে শাসককে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে কাঠগড়াই দাঁড় করানোর জন্য। বিশ্ববাসীকে ছবি দেখার নতুন দৃষ্টি দান করেছেন যে পরিচালক তিনি বার বার অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবার পর শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ছেড়ে সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ‘দিস ইজ নট এ ফিল্ম’ তথ্যচিত্র খ্যাত ইরানের নব চলচ্চিত্র ধারার অন্যতম পরিচালক জফর পানাহি সর্বাধিপত্যকামী অগণতান্ত্রিক শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে শাসকেরই নির্দেশে বার বার কারাবন্দি হয়েছেন। তাঁর ছবি আন্তর্জাতিক সম্মানে সম্মানীত হলেও ইরানে নিষিদ্ধ হয়েছে।
আর্জেন্টিনার পরিচালক ফারনান্দো বিররি, রবার রোচা, কারলোজ আলভারেজ, হুগো জারা মিলো, মারিও আরিয়েতা, হাম্বারত রিয়োজ ও রাইমুন্দ গ্লিজার শুধু বাধা পাননি, শিকার হয়েছেন নির্যাতনের। বেলজিয়ামের ওয়াসমেসের কয়লাখনির শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে ছবি ‘বরিনেস’এর শুটিং এ বেলজিয়ান পরিচালক হেনরি স্টর্ক ও সঙ্গী ডাচ পরিচালক জরিস ইভেন্স পুলিশের প্রহার উপহার পেয়েছেন। আরজেন্টিনার রাইমুন্দ গ্লিজার ১৯৯৬ সালে ‘আফটার সেরামিক অফ সিয়েরা’ ও পরে ‘আওয়ার মালভিনাস আইল্যান্ড’ ছবিতে কারডোবা অঞ্চলের সীমান্তে বসবাসকারী আদিবাসীদের ও মালভিনাস দ্বীপের মানুষের জীবন, শিল্পকলা, দুঃখ-কষ্ট কথা এমন ভাবে তুলে ধরেছিলেন শাসক শ্রেণির কপালে ভাঁজ পড়েছিল। পরিচালক রাইমুন্দ তথ্যচিত্রকে প্রতিবাদের হাতিয়ার করে তুললেন যা আঘাত করল আর্জেন্টিনার জুন্টা সরকারকে। ১৯৭০ সালে মেক্সিকান বিপ্লবের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মেক্সিকোর সমাজ ও রাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে তৈরি ছবি ‘মেক্সিকো:দ্য ফ্রোজেন রেভোল্যুশন’ নিষিদ্ধ হল। ১৯৭১ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গোপনে এই ছবি দেখাতে উদ্যত হলেন রাইমুন্দ। এভাবেই ১৯৭৬ সালের ২৭শে মে হারিয়ে গেলেন, গোপনে প্রোজেক্টর নিয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখাতে গিয়ে গোপনেই খুন হলেন রাইমুন্দ।১২ এরকয়েক বছর আগে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি করা পরিচালক ও সাহিত্যিক জাহির রায়হানও গুম হয়েছিলেন।
সেই তখন থেকেই দগদগে যন্ত্রণা নিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজনৈতিক তথ্যচিত্র। জাহির রায়হান হারিয়ে গেলেও প্রতিবাদের জন্য যেমন ছিলেন শাহিন দিল রিয়াজ, তারেক মাসুদ তেমন রাইমুন্দ হারিয়ে গেলেও আর্জেন্টিনায় ছিল ফারনান্দো সোলানাস সহ আরও একঝাঁক রাজনৈতিক পরিচালক।
ভারতে সত্তরের দশকেই নিউ ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি ধারার প্রচলন হয় আর তথ্যচিত্রের নির্মাণ-কৌশল ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আসে। ফিল্মস ডিভিশন সরকার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সেখানে পরিচালককে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছকে ছবি তৈরি করতে হত। সেখানে সরকারি কর্মসূচী প্রচারের জন্য প্রচারমূলক ছবি তৈরি হত বেশি। এই সত্তরের দশকে বেশ কিছু পরিচালক ফিল্মস ডিভিশনের ছকের বাইরে বেরিয়ে ছবি তৈরির সাহস দেখালেন। তাঁদের তথ্যচিত্রের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠল নিম্নবিত্ত বা দলিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণ আন্দোলন। তবে তখনও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত দূরদর্শন তথ্যচিত্র প্রদর্শনে বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করত, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে জনগণের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবার মতো ছবিগুলো দূরদর্শনে প্রদর্শিত হত। কিন্তু সত্তরের দশকেই ভারত ও বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতি রাজনৈতিক অস্থিরতায় উত্তাল হয়ে উঠলে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রবণতা বেড়ে গেল। রাজনৈতিক তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু ও প্রকাশের তীক্ষ্ণতা সরকারকেই ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। ইন্দিরা গান্ধির শাসনকালে সরকার জরুরি অবস্থা জারি করলে তথ্যচিত্র নির্মাণ ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনের উপরেও তার প্রভাব পড়ল, বহু তথ্যচিত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত হল, দূরদর্শন মুষ্টিগত হল। সরকার পছন্দমত তথ্যচিত্র নির্বাচন করে দূরদর্শনে দেখাতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গের জরুরি অবস্থার ওপর নির্মিত এক ডকুমেন্টারি ‘দুঃস্বপ্নের দিনগুলি’ নিষিদ্ধ হল।
স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় পরিচালক এস সুখদেব (সুখদেব সিংহ সাঁধু) ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যাকে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই বিতর্কিত রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাতা ভারতের দারিদ্র ও জনবিক্ষোভ নিয়ে ১৯৬৫ সালে তৈরি করলেন ‘এন্ড মাইলস টু গো’ এবং ১৯৬৭ তৈরি করলেন ‘আন ইন্ডিয়ান ডে’ (যে ছবিটি ‘ইন্ডিয়া ‘৬৭’ নামে পরিচিত)। সত্তরের দশকের ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বেআব্রু হয়ে যায় তাঁর ছবিতে। আর সুখদেবকে, এই প্রতিবাদী চলচ্চিত্র-পরিচালককে রাষ্ট্র ব্যবহার করতে চাইল নিজের স্বার্থে। তত্কালীন সরকার তাঁকে দিয়ে এমন ছবি করালেন যাতে ছবির মধ্য দিয়ে সরকারি প্রকল্পের প্রশংসা করা হয়। সরকারের ইচ্ছায় ফিল্মস ডিভিশনের হয়ে তত্কালীন সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রশংসা করে তিনি তৈরি করলেন ‘বিহাইন্ড দ্য ব্রেডলাইন’ (১৯৭৪)। ১৯৭৪ সালের রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আরও কিছু ছবির দায়িত্ব পেলেন সুখদেব। সরকার থেকে তাঁকে সমাদরে বিমানে করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু তিনি শেষ ছবি করলেন ‘বাঁধা-শ্রমিক প্রথা’র উচ্ছেদ নিয়ে। শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনি তুলে ধরতে চাইলেন আর সরকার তা ধামাচাপা দিতে চাইল। ছবির নাম ‘আফটার দ্য সাইলেন্স’। এই ছবিতে যেহেতু দেখানো হয় বিহারে তেজারতি ব্যাবসা করে কয়েকজন কংগ্রেসের নেতা, বেআইনি ভাবে বেশ কিছু বাঁধা-শ্রমিককে আজীবন দাসত্বে বাধ্য করেছে, সেহেতু পরিচালককে ছবি থেকে ওই বিশেষ অংশ বাদ দিতে বলা হল। আর মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টায় পরিচালক সম্মত না হওয়ায় ছবিটি বাতিল করা হল। শুধু শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করা হল না তথ্যও গোপন করা হল। তত্কালীন সরকারের সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল তা তিনি খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারলেন। শেষ পর্যন্ত জীবন হয়ে উঠল যন্ত্রণাময়, তিনি ছবি করতে অস্বীকার করলেন। সরকারি নির্দেশে ছবি করার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে শুকদেব বলেছেন- “ওরা আমাকে কোনোদিনই স্বাধীনতা দেয়নি। আমি এই সময় বড় যন্ত্রণা ও অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছি। মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লার সঙ্গে আমার প্রায় রোজই কথা কাটাকাটি হত। ঝগড়া করতে করতে আমি মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সর্বদাই তিনি ফোনে আমাকে নির্দেশ দিতেন এটা করো, ওটা কোরো।”

এদিকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেমে আসে ষাটের দশকের শেষ থেকেই —১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে ১৯৭১ এ শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি জাতির উপর আকস্মিক ভাবে শুরু হয় নজিরবিহীন বর্বরতা, নিষ্ঠুর গণহত্যা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বাধীনতার দাবি তুললে, তা চিরতরে নির্মূল করতে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকবাহিনী দীর্ঘ আটমাস দু-সপ্তাহ ও তিনদিন ধরে (২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর) প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং অসংখ্য বাঙালি মহিলাকে পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করে। সে দেশের বাঙালি জাতিকে চরম দুর্দশা, আর নৃশংস অত্যাচারের মুখে পড়তে হয়। বাঙালির এই দূরাবস্থাকে ক্যামেরাবন্দি করে রাখার কথা ভেবেছিলেন অনেকেই। তবে পরিচালক সুখদেব ছবি করলেন ‘নাইন মান্থস টু গো’। ছবিটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর যন্ত্রণা, ভাষা আন্দোলনের ছবির ফুটেজ ও সাক্ষাত্কার তুলে ধরেন দর্শকের সামনে।
১৯৭৯ সালে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা যান, ততদিনে সুখদেব পরিচালনা করে ফেলেছেন ষাটটি ছবি আর ঘরে আনেন পঁয়ত্রিশটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার।
সত্তরের দশকের ভারতের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কয়েকজন নির্ভিক পরিচালক তথ্যচিত্র নির্মান করেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, কখনও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠস্বর গর্জে উঠেন, রাজনৈতিক মন্তব্য জায়গা করে নেয় ছবিতে। রিয়ালিটিকে পুনরাবিষ্কার করার চেষ্টা করে, ফিকশন ভেঙে, আখ্যানধর্মকে ভেঙে তারা তথ্যচিত্র তৈরি করলেন নতুন ভাবনায়। এমনই একদল তথ্যচিত্র পরিচালকের মধ্যে অন্যতম হলেন আনন্দ পট্টবর্ধন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আনন্দ পট্টবর্ধন একজন সাহসী রাজনৈতিক তথ্যচিত্রকারের নাম।

আনন্দ পট্টবর্ধনের সবচেয়ে বিতর্কিত, উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র হল ‘ওয়েভস অফ রেভোল্যুশন’। ছবিটিতে ১৯৭৪ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিহারের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবিটিকে স্বয়ং পরিচালক ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ ছবি বলে অভিহিত করেছেন। বিহারের জয় প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সর্বাত্মক বিপ্লবের কর্মসূচিকে ঘিরে ছবিটি তৈরি করা হয়। বিহার তখন এক বড়সড় দুর্গে পরিণত হয়েছে। বিক্ষোভ সামলাতে চারিদিক পুলিশে ছেয়ে গেছে। সাধারণ জীবনযাপন বন্ধ হয়ে গেছে, সেই সময় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে ছবিগুলি তুলতে হয়েছিল। গোপনে রেকর্ড করা ভিখারি, রিক্সা চালক, পুলিশসহ সাধারণ মানুষের সাক্ষাত্কারের মাধ্যমে ঘটনার বিবরণ দিয়ে নির্মান করা হল ‘এইট মিমি’ ও ‘সুপার এইট’ ক্যামেরায় তোলা হিন্দি তথ্যচিত্র। এক আন্দোলন আর অনেক অসন্তোষের ছবি ‘ওয়েভস অফ রেভোল্যুশন’ নিষিদ্ধ হল কারণ শাসকদল চায়নি এই আন্দোলন, এই অসন্তোষ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলে এই ছবির প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে পরিচালকের কথা স্মরণ করা যাক—
“এই ছবির প্রদর্শন খুব গোপনে করতে হত। আমাদের পরিচিত বন্ধু ছাড়া অচেনা কাউকে অনুমতি দেওয়া হত না। কারণ যে কোনও মুহূর্তে ছবি প্রদর্শনের সময় বিপদের সম্ভাবনা ছিল। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে সরকারের কোনো পদস্থ কর্মচারীর দৃষ্টিগোচর হলেই এই ছবিকে তারা ক্ষমতাবলে বাজেয়াপ্ত করতেন এবং ছবি দেখতে উপস্থিত প্রত্যেককে জেলে ভরতেন”।
ভারতে এই ছবির প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা জারি হলে একটি প্রিন্ট বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়ার পর গোপনে ছবির দ্বিতীয় প্রিন্ট করিয়ে পরিচালক তাঁর বন্ধুর ব্যাগে আলাদা আলাদা করে বিদেশে পাচার করেন। ছবিটি ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করার সামর্থ্য না থাকায় একটি ভিডিয়ো কপিতে হিন্দির উপর ইংরেজি সংলাপ চাপিয়ে প্যারাডাব করে ছবিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। জরুরি অবস্থা কেটে গেলেও পরবর্তী সরকার এই ছবির শেষ অংশের কথাগুলি কেটে বাদ দিতে বলে। পরিচালক রাজি না হওয়ায় ফিল্ম পাবলিসিটি বিভাগের ডিরেক্টর ছবিটি কিনতে অস্বীকার করে। পরে কয়েকজন সাংবাদিকের আন্তরিকতায় ভারতের আঞ্চলিক দূরদর্শনে ৫০০ টাকা সাম্মানিক সহ দেখানোর ব্যবস্থা করেন।
আনন্দ পট্টবর্ধনের আর-একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র হল, ‘প্রিজনার্স অফ কনশায়েন্স’ (১৯৭৮)। এই ছবিতে তিনি দেখিয়েছেন জেলবন্দি মানুষের ছবি। ভারতের নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মেরি টেলর নামে এক ব্রিটিশ স্কুল শিক্ষিকার পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়। তাঁর স্বামী (ভারতীয় বংশদ্ভূত) একই কারণে হাজত বাস করেন। এ ছবিতে স্কুল শিক্ষিকার সাক্ষাত্কারের সঙ্গে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত কিছু জেলবন্দির সাক্ষাত্কারও নেওয়া হয়েছিল যা ছবিতে দেখানো হয়। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে এই ছবির কাজ শেষ হলে প্রথমে সেন্সরবোর্ড ছাড়পত্র দিতে আপত্তি করে। কিন্তু ছবিটি বাণিজ্যিক চ্যানেলে প্রদর্শন করানো সম্ভব হয়নি। প্রথম দুটো প্রিন্ট নষ্ট হয়ে গেলে পরের দুটো প্রিন্ট বিক্রি করা হয়। অন্য চারটি প্রিন্ট একটি সংস্থাকে দানও করা হয়। গণতান্ত্রিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ‘দ্য পিপল ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক রাইটস’ নামক সংস্থাকে প্রদান করা হয়। তবে জরুরি অবস্থা কেটে গেলে নতুন সরকার ছবিটি ছাড়পত্র পায়।
এর আগেই আনন্দ পট্টবর্ধন আর-একটি ছবি করেছিলেন, নাম ‘এ টাইম টু রাইজ’। তাতে কানাডায় প্রবাসী ভারতীয়দের ইউনিয়ন করার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ছবিটির প্রদর্শনের ছাড়পত্র নিয়ে বেশ সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ভারত সরকার কানাডার সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারমূলক ছবি প্রদর্শন করতে রাজি হয়নি—যা এই ছবির বিষয়বস্তু ছিল। তাঁর ছবি বিতর্কিত হলেও পুরস্কৃত হয়েছে।
তাঁর ‘বম্বে: আওর সিটি’ (১৯৮৫) ছবিতে বোম্বেতে বস্তিবাসীদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সমস্যাকে তুলে ধরেন। দেখিয়েছেন সামাজিক সম্পদ গড়ে তোলার কাজে ওদের অবদান থাকলেও বর্ষায় ফুটপাতবাসীর মাথাগোঁজার জায়গা পর্যন্ত নেই। তাদেরও যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার আছে, আবাসনের অধিকার আছে সে কথা মনে করিয়ে দেয়। ছবিটি প্রদর্শনের জন্য আদালতে চার বছর ধরে মামলা চলার পর পট্টবর্ধনের পক্ষে রায় হলে দূরদর্শনে দেখানো হয়।

তাঁর জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি ‘ইন মেমরি অফ ফ্রেন্ডস’ (১৯৯০)। ‘উনা মিত্রান দি ইয়াদ প্যায়ারি’ নামেও পরিচিত ছবিটি পাঞ্জাবে সরকারি সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনর্গঠনের উপর নির্মিত। ছবিটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯০), মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে রৌপ্য শঙ্খ (১৯৯০) লাভ করেছিল। এছাড়া বিশেষ জুরি পুরস্কার ম্যানহাইম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে (১৯৯০) লাভ করে।
‘ইন দ্য নেইম অফ গড’ নামে ১৯৯২ সালে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংস নিয়ে রাজনৈতিক ও বিতর্কিত ছবি করেন। ছবিটি শ্রেষ্ঠ অনুসন্ধানী চলচ্চিত্রের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯২), শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার (১৯৯৬) সহ বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়। তাঁর ‘ইন দ্য নেইম অফ গড’ বা ‘রাম কে নাম’ যত পুরস্কার ও প্রশংশা পেয়েছে ততটাই বাধা পেয়েছে শাসকের কাছ থেকে প্রদর্শনের জন্য। তাঁর বক্তব্য ছিল বাবরি মসজিদ কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়, তা ভারতবাসীর। বাবরি মসজিদকে জাতীয় স্মারক ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি তথ্যচিত্রকে রাষ্ট্রের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁর রাজনৈতিক ছবি প্রতিবাদ হয়েই প্রতিপন্ন হয়েছে সব সময়। এই ছবিতে অযোধ্যার রাম মন্দিরের পূজারি লালদাশের কয়েকটি কথা শোনানো হয় যেখানে লালদাশ বলেন ‘রাজনৈতিক স্বার্থ এবং অর্থের লোভেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি এসব করছে’। বলাবাহুল্য তথ্যচিত্র দেখানোর কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৯৩ সালে লালদাশ নামে ওই পূজারি খুন হন।
আবার তাঁর ‘ফাদার সন এন্ড হোলি ওয়ার’ (১৯৯৫) মুক্তির জন্য দীর্ঘ দশ বছর আদালতে মামলা চলে। শেষ পর্যন্ত এগারো বছর পর আদালতের নির্দেশে শুধুমাত্র দূরদর্শনে দেখানো হয়।
পরের বছর গুজরাটের আবর্জনায় মজে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া ক্ষীণতনু নদী নর্মদার করুণ অবস্থার ছবি তুলে ধরে ‘এ নর্মদা ডায়েরি’ যা ‘নর্মদা বাঁচাও’ আন্দোলনকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। ছবিটি ১৯৯৬ সালে আর্থ ভিশন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্র্যান্ড পুরস্কার পেয়েছে, পেয়েছে ১৯৯৬ সালের শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার।
ওই বছরই তাঁর ‘অকুপেশন : মিল ওয়ার্কার’, ছবিতে মিল শ্রমিকদের কর্মের বিবরণ দেওয়া হয় যারা চার বছরের লক-আউটের পরে জোরপূর্বক ভারতের নিউ গ্রেট ইস্টার্ন মিল দখল করেছিল।
তাঁর ২০০২ সালে তৈরি ‘ওয়ার এন্ড পীস’ যা স্বাধীনতার পর পর মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ড (১৯৭৪) ও ভারতের পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা (১৯৯৮), ধর্মীয় উগ্রবাদ, গ্লোবাল পিস মার্চ, সঙ্ঘ পরিবারের বিরোধিতাকে স্পষ্ট করায়। বর্তমান ভারতকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছবিটিও একবছর ধরে নিষিদ্ধ থকার পর আদালতের নির্দেশে ২০০৫ সালে দূরদর্শনে ও মাল্টিপ্লেক্সেও মুক্তি পেয়েছিল। এত বাধা পেয়েও তিনি থেমে থাকেননি, অপ্রতিরোধ্য গতিতে পরিচালনা করলেন ‘চিলড্রেন অফ মান্দালা’(২০০৯), এর দু’বছর পর পরিচালনা করেন আবার এক বিতর্কিত ছবি ‘জায় ভীম কমরেড’। ১৯৯৭ সালে মুম্বাইয়ে পুলিশের দ্বারা দশজন দলিত হত্যার ওপর ছবিটি নির্মিত ছবিটি রাম বাহাদুর গ্র্যান্ড পুরস্কার, নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ফিল্ম সাউথ এশিয়া পুরস্কার (২০১১) পায়। মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (২০১২) শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের পুরস্কার, হংকং ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে (২০১২), বিশেষ জুরি পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (২০১২) সহ একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়।
২০১৮ সালে ‘রিজন/ভিভেক’ নামে একটি তথ্যচিত্রে বিশ্বাস এবং যুক্তির লড়াইকে তুলে ধরেন। মোট আটটি পর্বের ছবিটি সেরা বিশিষ্ট-দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রের জন্য ২০১৮ সালে IDFA পুরস্কার পায়।
এদেশে রাজনৈতিক তথ্যচিত্র করার সাহস দেখিয়েছেন আর এক পরিচালক কলকাতার তপনকুমার বোস। সুহাসিণী মুলেকে সঙ্গে নিয়ে পরিচালনা করেছেন বেশ কিছু ছবি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘আন ইন্ডিয়ান স্টোরি’। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক চাঞ্চল্যকর তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই ছবির চিত্রনাট্য সাজিয়েছিলেন পরিচালক তপনকুমার বসু নিজেই। সাংবাদিক অরুণ সিনহা মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে তদন্ত করেন কীভাবে চৌত্রিশ জন বিচারাধীন বন্দির চোখে অ্যাসিড ঢালা হয়! সংবিধান স্বীকৃত আইন সম্পর্কে প্রখ্যাত আইনজীবী গোবিন্দ মুখুটির বক্তব্য এবং সাসপেন্ডেড পুলিশ অফিসার ও ভাগলপুর চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদলের নেতিবাচক সাক্ষাত্কার রাখা হয় ছবিতে। এই নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে জেহাদ ঘোষণা করতে অনুপ্রাণিত করে এই ছবিটি। ছবিটি স্বাভাবিক ভাবেই নিষিদ্ধ হয়। পরিচালক আদালতের দ্বারস্থ হলে বোম্বে হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্তি পান। এভাবেই ভারতীয় সাংবাদিকতায় একটি নতুন শব্দও যোগ হয়, তা হল “ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম”। সাংবাদিকতার এই প্রবনতা তথ্যচিত্র পরিচালকদের অনুপ্রাণিত করে।
তপনকুমার বসু ও সুহাসিনী মুলের পরবর্তী প্রযোজনা ‘বিয়ন্ড জেনোসাইড’ (১৯৮৫)এ ইনভেস্টিগেশন জার্নালিজম-এর মূর্ত প্রকাশ ঘটে। ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার দু’দিন পর তপনকুমার বসু তার টিম নিয়ে ভোপালে যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছ থেকে সত্য ঘটনা জানতে পারেন। গ্যাস দুর্ঘটনা বিরোধী কমিটির সঙ্গে তপন বসুর টিমও সক্রিয় হয়ে ওঠে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই তথ্যচিত্রটি তৈরি করতে হয় বলে এই তথ্যচিত্রের বিন্যাসেও পরিবর্তন আনতে হয়, প্রথা বহির্ভূত ভাবে ভাষার ব্যবহার কম রাখতে হয়। পরবর্তীতে এই বিন্যাস বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই ধারা অনুসরণ করে ‘মুক্তি চাই’ তথ্যচিত্র তৈরি করেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী—নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে যে ছবি বিনা শর্তে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি করে। আনন্দ পট্টবর্ধনও বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র করেছেন ন্যারেশন বা ভাষ্য ছাড়া।
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল একসময়, দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠল তথ্যচিত্রও। প্রকাশ চন্দ্র ঝাঁ বিহারের নালন্দা জেলার দাঙ্গার প্রেক্ষিতে ‘ফেসেস আফটার দ্য স্টর্ম (১৯৮১)’ ছবি করলেন আর প্রকাশ চন্দ্র সি শর্মা গুজরাটের বিভান্ডি দাঙ্গার প্রেক্ষিতে ‘পিপল অফ বিভান্ডি স্পিক (১৯৯০)’ ছবি করলেন। এই ছবিগুলি কলকাতার দাঙ্গার উপর তৈরি ‘চেনা শহর অচেনা সময়’ ও শেখর মুখার্জির ‘পুরস্কার’ ছবিকে মনে করায়। আবার ২০০২ সালের গুজরাটের দাঙ্গার কারণ খুঁজেছেন পরিচালক রাকেশ শর্মা। তাঁর ‘ফাইনাল সলিউশন (২০০৪)’ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে গুজরাট কেন দাঙ্গার কবলে পড়ল! হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণই তাদের মতামত জানিয়েছে, জানিয়েছে বিদ্বেষের কথা। গোধড়ার ট্রেন পোড়ানোর প্রতিশোধ নিতেই নাকি গুজরাটের দাঙ্গা হয়েছিল, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা গণতন্ত্রকে হত্যা করছে পরিকল্পিতভাবে। হায়দ্রাবাদের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে দীপা ধনরাজ ‘হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দ্য সিটি’ (১৯৮৬) ছবি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শাসকের নিষ্কৃয়তা ও ব্যর্থতা প্রকাশ করেন। কথোপকথন ও সাক্ষাৎকারের ছবিটি ১৯৮৪ সালে দাঙ্গার সময় শুটিং করা হয়, দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক হিংসা যে শুধু সমসাময়িক বীভত্সতা দান করে না, পরবর্তীতে জীবনে ও দেশের অর্থনীতিতে তার ভয়ংকর প্রভাব পড়ে তাও দেখিয়েছেন।
তথ্যচিত্র হয়েছে কাশ্মীর নিয়েও, কাশ্মীর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিতর্কিত নাম। তার রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব গোটা কাশ্মীরকেই বিধ্বস্ত করে তুলেছে। প্রতিনিয়ত অস্ত্র, ত্রাস, কার্ফু, রক্ত, লাশ দেখে শঙ্কিত কাশ্মীরবাসী। সঞ্জয় কাকের “জশন ই আজাদি-হাউ উই সেলিব্রেট ফ্রিডম” (২০০৭) স্বাধীনতার ষাট বছর পূর্তি উদযাপন ও কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামকে দেখিয়েছেন-স্বাধীনতার সময় যে ভূখণ্ড ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। গত দুই দশক ধরে সন্ত্রাসবাদী বনাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত, ভীত, সন্ত্রস্ত্র। ২০০৪-০৬ সাল পর্যন্ত শুটিং করে দেখালেন কবরের সারি, রক্তাক্ত লাশ উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, স্বাধীনতার ষাট বছর পূর্তি তাদের কাছে কতটা অর্থবহ থাকে!
এই একই কাশ্মীরের ছবি অন্যভাবে দেখতে পাওয়া যায় অশ্মিন কুমারের ‘ইনশাল্লা কাশ্মীর’ (২০১২) ছবিতে। অবধারিত এনকাউন্টার, গণকবর, রক্তাক্ত লাশ প্রতিনিয়ত দেখে চলেছে সাধারণ মানুষ। দুই পক্ষের সংঘর্ষে প্রভাবিত হয়েছে এখানকার সামাজিক জীবন। অশ্মিন কুমারের আর এক ছবি ‘ইনশাল্লা ফুটবল’ (২০১০), যেখানে তুলে ধরেন কীভাবে কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাস এক উদীয়মান সপ্রতিভ ফুটবলারের স্বপ্নপূরণে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সেকথা। প্রতিনিয়ত জমতে থাকা উদ্বেগ সারা কাশ্মীরবাসীকে কীভাবে গ্রাস করে, কীভাবে রাজনৈতিক চক্রান্তের স্বীকার হয় তরুণ প্রজন্ম তা নিয়ে অশ্বীন কুমারের ছবি। তরুণ ফুটবলার “বাশা” কাশ্মীরের অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশেই বড় হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বাশার বাবা তার পরিবার ও দু মাসের বাশাকে কাশ্মীরে রেখে পাকিস্তান চলে গিয়েছিল সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী “হিজবুল মুজাহিদিন”এ যোগ দিতে। বাশা পরবর্তীতে একজন ফুটবল খেলোয়াড় ও ফুটবল প্রেমী হয়ে ওঠে। সে ফিফা স্বীকৃত কোচ জুয়ান কার্কোস স্টোয়ার কাছে প্রশিক্ষণ নেয়। বাশা ব্রাজিলে পেলের পুরানো ক্লাব সন্তোষ এফ সি তে প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে বাবা সন্ত্রাসবাদি হওয়ার কারণে ভারত সরকার অনুমতি দেয় না। পরে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার হস্তক্ষেপে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। ছবিতে বাশার বাবার বিশ্বাসের লড়াই, বাশার কঠিন জীবন, কোচের চেষ্টা যেভাবে উঠে এসেছে তা ভূয়ষী প্রশংসা ও পুরস্কার পেয়েছে। তবে ভারতের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর ভূমিকা, রাজনৈতিক পর্যালোচনা যেভাবে করা হয়েছে তা সকলের দেখার উপযুক্ত নয় বলে আপত্তি জানিয়েছিল সেন্সরবোর্ড। শেষ পর্যন্ত তিনবার পর্যালোচনা করে “A” চিহ্নিত শংসাপত্র দেয়। রাজনৈতিক অস্থিরতায় ও সন্ত্রাসে কাশ্মীরের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে, খুন ধর্ষণের পরিবেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম এক স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখে। আর ভারত -পাকিস্তানের সম্পর্কের কথা নিয়ে সুপ্রিয় সেনের স্বল্প দৈর্ঘের ছবি ‘ওয়াঘা’ সম্প্রীতির নতুন স্বপ্ন দেখায়। দেশভাগের পঁচাত্তর বছর পরেও তা সাধারণ মানুষকে কতটা যন্ত্রণা দেয় তা দেখিয়েছেন।
তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন পরিচালকেরাও সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক প্রভাব বা সরাসরি রাজনীতি নিয়ে ছবি কাজ করে চলেছেন। তৈরি হয়েছে কলকাতার সাউথ সিটির জন্ম রহস্য ও ঊষা কম্পানির আবাসনে থাকা এক শ্রমিকের লড়াইয়ের কথা নিয়ে রাণু ঘোষের ‘কোয়ার্টার নম্বর ৪/১১’ (২০১১) ছবিও। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেনকে নিয়ে সুমন ঘোষের ‘দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান’ (২০১৭) ছবিতে গুজরাটের দাঙ্গার উল্লেখ থাকায় ছাড়পত্র পায়নি। গুজরাট সহ ‘হিন্দু’, ‘গোরু’, ‘হিন্দুত্ব’ শব্দগুলোও বাদ দিতে বলা হয়।
পরিচালক খুশবু রাংকা ও বিনয় শুক্লা—দিল্লির আম আদমি পার্টির অরবিন্দ কেজরিওয়ালের একজন সাধারণ মানুষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী হবার কাহিনি নিয়ে ছবি করেন ‘আন ইনসিগ্নিফিক্যান্ট ম্যান’(২০১৭)। কেমন করে তাঁর পার্টি গঠিত হল, কেমন করে একটি অরাজনৈতিক পার্টি জনসমর্থন পেয়ে ধীরে ধীরে একটি রাজনৈতিক পার্টিতে পরিণত হল এবং একজন সাধারণ মানুষ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হলেন তা দেখানো হয়, সেই সঙ্গে এও দেখানো হয় যে এই আম আদমি পার্টি পরবর্তীতে তার লক্ষ্য থেকে সরে যায়। সেই সঙ্গে যোগেন্দ্র যাদবকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও বিতর্কিত বিষয়কে তুলে ধরার কারণে ছবিটি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ও শীলা দীক্ষিতের সম্মতি পত্র আনতে বলা হলে পরিচালক গররাজি হন। শেষে ছবিটি ২০১৭ সালে আমেরিকায় প্রথম প্রদর্শিত হয়। পরিচালক শাহিদা তুলাগানোভা সম্প্রতি তৈরি করেন ‘এক্সলড রোহিঙ্গিয়া (২০১৯), বার্মার রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার, রোহিঙ্গাদের গণহত্যার প্রতিবাদের ছবি।
কিছু তথ্যচিত্র বরাবর মানুষের লড়াইয়ের কথা বলে, শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে। সুতরাং শিল্পের মাধ্যমে লড়াইটা চলছে, সত্য কথনের লড়াই, শ্রেণি সংগ্রামের লড়াই…। শুধু দক্ষতা নয় এ ছবি করতে লাগে সাহসও। লাগে সত্য কথনের স্পর্ধা। তথ্যচিত্রের পরিচালকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পরিচালক ও চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক বেসিল রাইট বলেছিলেন—
‘ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাতা একজন বিপ্লবী ছাড়া আর কিছু না। তিনি আশেপাশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যই মাধ্যমকে ব্যবহার করে থাকেন…সেই অর্থে তাকে নিরপেক্ষ থাকলে চলে না। তাকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিতেই হয়।’
আর বিখ্যাত তথ্যচিত্র ‘হাংরি অটম’-র পরিচালক গৌতম ঘোষ বলেছেন—
‘কোনো শিল্পীরই বাস্তবতা থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে তার শিল্পকে ব্যবহার করা উচিত নয়। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন সেই পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত, দায়িত্ব হল শোষণহীন মানবিক শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি করা।’
তথ্যচিত্র নির্মাতারাও দার্শনিকের মতো দর্শকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় ন্যায় অন্যায়ের ভেদাভেদকে। তাঁর শিল্পসত্তা সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষিতের পাশে দাঁড়াতে শেখায়। যে শিক্ষা সুষ্ঠু সমাজ গড়ার দায়বদ্ধতাকে টেনে আনে। তাই যত বাধাই আসুক বিপ্লব আনতে রাজনৈতিক তথ্যচিত্র আগেও তৈরি হয়েছে ভবিষ্যতেও হবে।
তবে কেন সেনসর বোর্ড?
মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারতসহ ব্রিটিশের বিশাল সাম্রাজ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের ওপর আইন তৈরি হয়েছিল। ১৯০৯ সালেই দ্য সিনেমাটোগ্রাফ এক্ট চালু হলেও ‘British Board of film censors’ ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর চার বছর পর টি পি ও’ কনরের অবদানে নিয়মবিধির স্বচ্ছতা আসে। যে বিধি আরো এক বছর পর কার্যকরী হয়। জনসাধারণের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় পরিষদ (National Board of Public Morals) এই সেন্সর বোর্ড গঠন করে। এই বোর্ডেরই অন্যতম সভাপতি টি পি ও’ কনর মূলত প্রোপাগান্ডামূলক ছবির বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রোপাগান্ডা ছবি তৈরি হয় বিশেষ কোনো মতাদর্শের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য। তখন ছবির বিষয়বস্তু নারীব্যবসা, রেস, সুইসাইড, কালোবাজারি বিশেষ কোনো বংশগত রোগের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা ও নিরাময়ের অনুসন্ধান হলেও ছবিতে বিনোদন বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকলে ব্রিটিশ সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিত না। তবে এই ব্রিটিশের চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড অর্থাৎ ‘ব্রিটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সর’-এর তেতাল্লিশটি ধারার মধ্যে উনিশটি ছিল যৌন-আবেদন সম্পর্কিত।
১৯১৮ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র তৈরি হলে তা মান্য করা হচ্ছে কিনা তারও পরিদর্শনের জন্য থানার বড়োকর্তার অধীনে একটি আঞ্চলিক চলচ্চিত্র বোর্ড তৈরি করা হয়। এমনকি ছবি দেখানোর আগে প্রি-সেন্সরশিপ চালু করা হয়, ফলে নির্দিষ্ট সরকারি অফিসারের কাছ থেকে প্রাথমিক ছাড়পত্র নিতে হত। ১৯১৮ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র আইনের প্রথম দুটি সংশোধনী হয়। ওই আইন অনুসারে ১৯২০ সালে দেশে পাঁচটি প্রাদেশিক সেন্সর বোর্ড গঠিত হয়। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ ও রেঙ্গুনে আলাদা বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সর প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিল্ম ইনস্পেক্টরের জন্য যে বিধি নির্দিষ্ট হয় তা হুবহু ও’কনরের তেতাল্লিশটির মধ্যে বিয়াল্লিশটি বিধি। মূলত ও’কনরের সেই বিধিই ভারতের চলচ্চিত্র আইনের ভিত্তি হয়েছিল আটের দশক আবধি। অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও কিছু বিধিনিষেধ, যেমন—সামাজিক অসন্তোষ ও উত্তেজনা বাড়ানো যাবে না, রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিবাদ প্রতিরোধমূলক অসন্তোষ ছড়ানো যাবে না, সরকারি আইন-শৃঙ্খলা অমান্য করা যাবে না। এমনকি সরকারি সৈন্যবাহিনী, ধর্মপ্রচারক, রাজমন্ত্রী, ব্রিটিশদের দূত, সরকারি প্রতিনিধি, বিচারক, পুলিশ, সরকারি কর্মচারীদের অশ্রদ্ধা করা যাবে না। ১৯১৮ সালের ভারতীয় চলচ্চিত্র আইনের ৮/২ ধারায় এও বলা হয় কোনো ছবিতে কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার বা শ্বেতাঙ্গদের প্রতি কৃষ্ণাঙ্গের নির্যাতন দেখানো যাবে না।আসলে এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত, আমেরিকা, ইউরোপের স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের আন্দোলন থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে আড়াল করে রাখা। দর্শকের নিরাপত্তা, নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির অজুহাতে সেই মূল উদ্দেশ্যকে প্রতিপালন করা হত। ব্রিটিশ সরকার কঠোরভাবে সেন্সর ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত যেন তাদের শাসন, শোষণ, অত্যাচার কোনো ভাবেই চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত না হয়। কোনোভাবেই যেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জনমত সমর্থন আদায় করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকত। সেই কারণেই ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে হীরালাল সেনের ‘ভিজিট ফিল্ম’ ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আবার ভারতের রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের একটি প্রতিনিধিদল লেনিনের সঙ্গে দেখা করারএবং ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে গোপনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার খবর ব্রিটিশ সরকারের কাছে পৌঁছালে ভারতসহ সারা বিশ্বে সেন্সরশিপের কড়াকড়ি শুরু হয়। বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব যাতে কোনোভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে না পড়ে তার জন্য তত্পর ছিল বলেই সেন্সরশিপের কড়াকড়ি শুরু হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছু প্রচারমূলক ছবি নিজেরাই নির্মাণ করেছিল, তথ্য বিকৃত করে জনগণকে ভুল বোঝাতে। এই সময় সঠিক তথ্য পরিবেশনকে ভয় পেয়ে যে ছবিকে গুম করল সেটি হল ‘কল অফ বেঙ্গল’। ছবির নির্মাণ ও পরিবেশন পুরোপুরি ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন ছিল বলে তারা যুদ্ধকালীন ছবিগুলির মাধ্যমে তথ্যের বিকৃতি করে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনগনকে ভুল বোঝাত এবং তা ‘ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া’ আইনের দ্বারা কার্যকর করত। এর একটি উদাহরণ হল ‘কল অফ বেঙ্গল’ ছবি। সরকারি উদ্যোগে তথ্যমন্ত্রক থেকে ১৯৪৩ সালের বাংলার মর্মান্তিক মন্বন্তরের ওপর তোলা ছবি যেটি ব্রিটিশ সরকারের আমলারাও অনেক চেষ্টা করে রিলিজ করাতে পারেনি। সরকারি আমলা ও রাজনীতিবিদরা বাংলার ভয়াবহ মন্বন্তরের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন মানুষের দুর্দশার ছবি দেখিয়ে ব্রিটিশ সরকারের খাদ্য সরবরাহ আইনের পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। সেই সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছবি দেখিয়ে সেখানকার মজুতদার, জমিদার, কৃ্ষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনে বাংলায় পাঠাতে চেয়েছিল। তাই গোপনে ছবিটি তৈরি করা হয়েছিল।
এই ‘কল অফ বেঙ্গল’ ছবিটি কেন নিষিদ্ধ হল তা বুঝতে গেলে জানতে হবে তত্কালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ষড়যন্ত্রকে। বাংলার এই মন্বন্তরকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে চার্চিল। কিন্তু এই মন্বন্তরের প্রকৃত কারণ শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল না। ছিল যুদ্ধের ইতিহাস, ছিল চার্চিলের বর্ণবিদ্বেষী, ভারতবিদ্বেষী মনোভাব। গবেষক মধুশ্রী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুপরিকল্পিতভাবে বাধ্য করা হয়েছিল বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে না খেয়ে মরতে। যুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যদের খাবারের জোগান দিতে এবং মজুত রাখতে সরকার অত্যাধিক খাদ্য মজুত করেছিল। খাদ্যশস্য বন্টন ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছিল, ফলে কালোবাজারের সুবিধা হয়েছিল। খাদ্যদ্রব্য ও তা সরবরাহকারী নৌকা ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। শহর থেকে যাদের রিলিফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের থেকেও কম খাবার দেওয়া হত বলে এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জানিয়েছেন। এই সময় ক্ষুধার্ত বাংলাকে খাদ্য সরবরাহ করার সমস্ত উদ্যোগ নাকচ করে দিয়েছিল চার্চিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে খাদ্যশস্য বোঝাই জাহাজকে কলকাতায় ঢুকতে দেয়নি। কানাডার সাহয্য নিতে অস্বীকার করল, ফিরে গেল গম বোঝাই জাহাজ আর ধুঁকতে থাকল বাংলার অসহায় মানুষ। নিজেদের ষড়যন্ত্র ধামাচাপা দিতে ব্রিটিশরা ছিল বদ্ধপরিকর, বাংলার মানুষের চরম দুর্দশার ইতিহাসকে সুকৌশলে মুছে ফেলতে চেয়েছিল সরকার। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ষড়যন্ত্রে ছবিটি নিষিদ্ধ করা হল। শেষ পর্যন্ত কোনো আমলাকেও এই ছবি দেখতে দেওয়া হল না, জায়গা হল ব্রিটিশ আর্কাইভে।
১৯৩৫ সালে ‘গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট’-এ সেন্সরশিপকে ‘কনকারেন্ট’ তালিকাভুক্ত করলেও ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের সরকার সেন্সরশিপকে ‘ইউনিয়ন’ তালিকাভুক্ত করল। রাজ্য সরকারকে কোনো ক্ষমতা না দিয়ে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখল। স্বাধীনতার পর নতুন সরকার আগের (১৯১৮) বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামোকে ভেঙে নতুন করে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ব্যবস্থা তৈরি করল। নতুন সংবিধানের সঙ্গেই ১৯৫২ সালে রচিত হল ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন। ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ধারায় {১৯(১)(ক)} নাগরিকের মতপ্রকাশ ও বাক্ স্বাধীনতায় হল নতুন সংযোজন। ১৯৫১ সালের জুন মাসে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে ১৯(২) ধারাতে বলা হল- যা কিছু রাষ্ট্রের পক্ষে নেতিবাচক, অবমাননাকর, নিরাপত্তা বিরোধী তা উপরিউক্ত অধিকার খাটবে না। সেন্সর বোর্ডের গিঁট বেঁধে বেঁধে পথ চলা শুরু হল নিয়মের বাঁধনে, অসংখ্য চলচ্চিত্রপ্রেমী, পরিচালক প্রযোজককে আশান্বিত করে। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সেন্সর বোর্ড চালু করল এবং ১৯৫৯ সালে শেষ সংশোধনীর পরেও তিনটি মৌলিকনীতি, সাধারণ নীতি, শেষ দুটি ধারার ব্যাখ্যা ও ও’কনরের তেতাল্লিশটি বিধির সংক্ষিপ্তরূপ ষোলোটি বিধিকে নিয়ে বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সরের নিয়মাবলি তৈরি হল। ১৯৬৮ সালে ডি জি খোসলার সভাপতিত্বে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সার্টিফিকেট নামে একটি কমিটি গঠিত হল। এই কমিটি ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের গঠন ও কর্মপদ্ধতিতে স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণাধিকার দেবার সুপারিশ করল, সেই সঙ্গে পুরাতন বিস্তারিত নির্দেশাবলির পরিবর্তে নতুন সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলির পক্ষেও সুপারিশ করল। একসময় সেন্সর বোর্ডকে ত্রুটিপূর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয় একটি প্রতিষ্ঠান বলে খাজা আহমেদ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্ত হলেন। কিন্তু পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয় ভারতের মত আর্থ-সামাজিক পরিবেশে চলচ্চিত্রের জন্য সেন্সর বোর্ডের প্রয়োজন আছে। এরপর অবশ্য ১৯৭৪ সালে এই কমিটির সুপারিশ কিছুটা মেনে নিয়ে নতুন আইন পাশ হয়। ১৯৭৫ সালে ৩০ জুন এগারো জনকে নিয়ে নতুন ‘বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সর’ গঠিত হয়। একটি বিজ্ঞপ্তিতে তা প্রকাশিতও হয়। ওই আইন অনুযায়ী এই বোর্ডকে প্রথম সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। এই বোর্ডের ক্ষমতা আদালতের সাহায্য ছাড়া সরকারও সংকোচন করতে পারত না। হয়তো সেই কারণেই পরের দিন, ১ জুলাই অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে নতুন নির্দেশাবলি বাতিল করে পুনরায় ১৯৫২ সালের নির্দেশাবলি বহাল রাখা হল। ১৯৫২ সালের আইন অনুযায়ী সরকার বোর্ডকে অগ্রাহ্য করে যে কোনো ছবিকে নিষিদ্ধ বা সাময়িক বরখাস্ত করার অধিকারী হল। অর্থাৎ সেন্সরশিপ পুরোপুরি সরকারের হাতে রইল। জরুরি অবস্থায় এই আইনের চুড়ান্ত অপব্যবহারও দেখা গেল। পরে মুরারজি দেশাই সরকার এলে আগের বোর্ড বাতিল করে নতুন বোর্ড গঠন করল ১৯৭৮ সালের ৭ জানুয়ারি। খোসলার কয়েকটি সুপারিশকে যুক্ত করা হল। এর দশটি নির্দেশাবলির আটটিতে ছিল সরাসরি রাজনৈতিক কারণ নিয়ে বিধিনিষেধ আর একটিতে ছিল অশ্লীলতা বা যৌনতা নিয়ে বিধিনিষেধ। অবশ্য নতুন নিয়মানুযায়ী ছবির অশ্লীলতা বা যৌনতার অজুহাতে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার নিয়মগুলি বাতিল করা হল। ৬ ও ৯ নম্বর ধারায় খোসলার সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় সংহতি, দেশের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলরক্ষা, পররাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সেখানে ১৯৫২ সালের চলচ্চিত্র আইনানুযায়ী সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতাটি বজায় রাখল।[১৯৮০ সালে শ্যাম বেনেগালের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হলে সেই ওয়ারকিং গ্রুপ অন ফিল্ম ‘পলিসি’র প্রতিবেদনে সিনেমা নিয়ে একটি সর্বাত্মক নীতি-নির্ধারণের কথা বলা হল। সেখানে সেন্সরবোর্ডকে উদার ও যুগোপযোগী করার প্রস্তাবও রাখা হল। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে নতুন চলচ্চিত্র আইন অনুসারে বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে হল ‘সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেট’। নতুন আইন অনুযায়ী দেশের সমস্ত চলচ্চিত্র, ভিডিয়ো, ডিভিডি, সিডি, সংগীত ভিডিয়ো, তথ্যচিত্র, কাহিনিচিত্র বাধ্যতামূলকভাবে সেন্সরবোর্ডের শংসাপত্রের আওতায় পড়ল এবং ২০০৪ সালে সে আইন আরও কঠিন হল। ১৯৫২ সাল ও ১৯৮৩ সালের ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন অনুযায়ী সমস্ত ধারার চলচ্চিত্রকে (কাহিনিচিত্র, তথ্যচিত্র, সংগীত ভিডিয়ো, ভিডিয়োচিত্র, অ্যানিমেশন) প্রদর্শনীর জন্য সেলুলয়েড কিংবা সিডি, ডিভিডি, ভিডিয়ো সংস্করণকে শংসাপত্র দান করে ‘সেনট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেট’ নামে একটি বোর্ড। এই সেন্সর বোর্ড শুধুমাত্র ছবির রিলিজ অর্ডার বা ছাড়পত্রই দেয় না, ছবির বিষয়বস্তু দেখে তার পর্যায় বা বিভাগ নির্বাচন করে দেয়। তখন থেকেই সেন্সর বোর্ড ছবির বিষয়বস্তু দেখে চার ভাগে ভাগ করে শংসাপত্র দেয়। এই শংসাপত্রেই বিভাগ উল্লেখ করা থাকে, আর এই বিভাগই বলে দেয় কোন কোন দর্শক ছবিটি দেখার যোগ্য। সেন্সর বোর্ড প্রদত্ত চারটি ভাগ হল—U, A, U/A, S। U চিহ্ন প্রদত্ত ছবিতে সকলের দেখার অনুমতি থাকে। A চিহ্ন প্রদত্ত ছবি কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের দেখার জন্য। U/A চিহ্ন প্রদত্ত ছবিগুলি মূলত সর্বজনীন হলেও অভিভাবকের অনুমতিতে বারো বছর বয়সী শিশুর দেখার জন্য। S চিহ্ন প্রদত্ত ছবি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ দর্শকের দেখার যোগ্য। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা বিজ্ঞানীদের দেখার অনুমতি দেওয়া হয়। একই ভাবে ভিডিয়ো প্রকাশের জন্য দেওয়া হয় V/U, V/A, V/UA, V/S চিহ্নগুলি।
বোর্ড ছবির দৈর্ঘ অনুযায়ী ৭৩ মিনিটের কম হলে তাকে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি এবং তার বেশি হলে তাকে পূর্ণ দৈর্ঘের ছবির আখ্যা দেওয়া হয়। বোর্ড ইচ্ছা করলে কোনো ছবিকে শংসাপত্র দিতে অস্বীকারও করতে পারে। বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা, অপরাধমূলক কাজ, শিশুদের প্রতি নির্যাতন, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের উপহাস বা অপব্যবহার, জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, অকারণ ভয়াবহতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা বিরোধ, দেশদ্রোহিতা, ধূমপান ও মাদক সেবন, যৌনতার দৃশ্য দেখানো নিষেধ থাকায় উপরিউক্ত যে কোনো একটি কারণে ছবি নিষিদ্ধ করতে পারে বা শংসাপত্র দিতে অস্বীকার করতে পারে।
সেন্সরবোর্ড ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ হওয়ার ফলে স্বশাসিত সংস্থার স্বাধীনতা ভোগ করে না, মূলত রাষ্ট্র তার ইচ্ছা মতো সংস্থাটিকে পরিচালিত করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের উপর নির্ভর করে এর গতিবিধি ও সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত থেকে বাদ পড়ে না তথ্যচিত্রও। স্বাধীন ভারতে যে উদ্দেশ্যে ফিল্মস ডিভিশন স্থাপিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যহত হয়। ফিল্মস ডিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়েছিলেন তথ্যচিত্রকে দেশের সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিতে কিন্তু সংবিধানের ১৯ এর ১/ক ধারার নতুন সংযোজনের ফাঁকে সবই আটকে গেল। আটকে গেল সত্য দর্শনের অধিকারও। গণতন্ত্রের হাত ধরে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের অপছন্দের ছবি ছাড়পত্র পায় না। আশচর্য বিষয় হল তার কোনো কৈফিয়তও দেওয়া হয় না। আবার সেই একই ছবি যা আগের শাসক দল ছাড়পত্র না দিলেও সেটিকে বিরোধীদল শাসনে এলে সবার আগে ছাড়পত্র দেয়। ছাড়পত্র নিয়ে আজও নতুন রাজনীতি, নতুন পাকচক্র তৈরি হয়েই চলেছে। চলচ্চিত্র সংস্থার মধ্যে সব থেকে আলোছায়াময় সংস্থা হল এই সেন্সর বোর্ড। নিরুপায় হয়ে পরিচালক-প্রযোজকরা আদালতের দ্বারস্ত হন। এই বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেকে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন। শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মত কোনো প্রতিষ্ঠান রাখার বিরোধিতা করেছেন অনেকেই। [২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মুকুল মুদ্গলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি সেন্সর বোর্ডের স্বাধীনতার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। আবার ২০১৬ সালে শ্যাম বেনেগালের নেতৃত্বে আর একটি কমিটি তৈরি হয়েছে পরামর্শ দিতে। সার্টিফিকেটের একটি বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করেছে কমিটি। কমিটির সুপারিশ ছিল- মূল্যায়নের বাইরে ছবি কাটাছেঁড়া করার কোনো অধিকার না রাখার জন্য, তবে অনিবার্য কারণে ছবিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে সংবিধানের ১৯(২) ধারা প্রয়োগ করে। ২০১৭ সালে অমল পালেকর সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করেন সেন্সর বোর্ডের শুধুমাত্র বিষয় ভিত্তিক শংসাপত্র দেবার অধিকার চেয়ে। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে যেহেতু সিনেমা হলের বাইরে সোস্যাল মিডিয়ায় ছবি দেখা যায় সেহেতু সেন্সর বোর্ডের আর প্রয়োজন নেই। পরিচালকের একাংশ তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা সেন্সর বোর্ড বৈষম্য সৃষ্টিকারী অসংবিধানিক একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিগত চার পাঁচ বছর ধরে এই মামলার নিষ্পত্তি না হলেও শিল্পীর স্বাধীনতা হরণকারী বোর্ডকে অনৈতিক বলে মনে করেন পরিচালকের একাংশ।
তবে বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ছবির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও পরিবেশনে দেশমাতৃকার প্রতি সকলে সমান দায়িত্বশীল হবে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে যে দেশের মানুষ এখনও প্রায় ত্রিশ শতাংশ নিরক্ষর, কোটি কোটি মানুষ এখনও শিক্ষার আলোর বাইরে সে দেশে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রচারমূলক ছবি তৈরি হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চলচ্চিত্র ব্যক্তি আক্রমণের মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারে। ভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির এই দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা বাড়িয়ে তোলার মতো বিষয়কে ছবিতে স্থান দিলে তা দেশ ও জাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। সর্বোপরি যুব সমাজরূপী বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাতে-কর্মবিমুখ করতে ঊর্বশী রূপী যৌন উত্তেজনা মূলক ছবি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ যুবসমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বরং সোস্যাল মিডিয়ার অবাধ যৌন উত্তেজনা মূলক ও হিংসাত্মক ছবি দেখানোর স্বাধীনতাকে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় রাশ টানা আবশ্যিক, যাতে কোনোভাবেই নতুন প্রজন্ম সোস্যাল মিডিয়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে। কারণ এই প্রজন্মকে সুশিক্ষিত নাগরিকে পরিনত করার সুপরিবেশ তৈরি করতে হবে আমাদেরই। শোনা যায় ১৮৯৭ সালে প্যারিসের একটি চ্যারিটি মেলায় চলচ্চিত্র দেখানোর সময় কোনো স্টলের প্রজেক্টরে আগুন লেগে ১৮০ জন প্রাণ হারায়। যেহেতু মেলার আয়োজক ছিল সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন তাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারাই। এরপর থেকে সেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনে সরকারি নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। জনগণের বিপদের কারণ হতে পারে এমন আশংকা থাকলে পুলিশ সেই চলচ্চিত্র প্রদর্শনি বন্ধ করতে পারবে এমন আইন তৈরি করা হল। পরবর্তিতে এই বিপদের সংজ্ঞা বদলে গেলো। দুরাচারী শাসক তার নিজের বিপদ বুঝলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনি বন্ধ করতে লাগল। কিন্তু বস্তুত প্রদর্শনি যদি বন্ধ করতে হয়, ছবি যদি নিষিদ্ধ করতে হয়, যদি নজরদারি করতে হয় তবে সেই সব ছবিতে নজরদারি করুক যেগুলি সাম্প্রদায়িক হিংসাকে উস্কে দেয়, যৌন উত্তেজনা বাড়িয়ে যুবসমাজকে নষ্ট করে, লিঙ্গ সাম্য ও শ্রেণিসাম্যে আঘাত হানে।
এ প্রসঙ্গে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৩০ সালের ১৯ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার চিত্রা সিনেমা হলের উদ্বোধন করতে গিয়ে চলচ্চিত্র ও সেন্সর বোর্ড সম্পর্কে বলেন- “আমরা যদি এরকম একটি বোর্ড পাইতাম যাহা আমাদের রুচি বুঝিতে সক্ষম ও আমাদের আশা- আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করার মত কল্পনা শক্তির অধিকারী, তাহা হইলে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে উহা সাহায্য করিতে পারিত”। প্রায় একশো বছর আগের দেওয়া এই বক্তব্য আজও এ দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক। দেশে এমন এক সেন্সর বোর্ডের প্রয়োজন যে বোর্ড সরকার নিয়ন্ত্রিত হবে না, হবে স্বনিয়ন্ত্রিত আর চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। সিদ্ধান্ত নেবে দেশ ও জাতির কল্যাণে এ শিল্প ব্যবহৃত হল কিনা, ছবির বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণ ও পরিবেশন শিল্পসম্মত হল কিনা তা বিচার করে।
তথ্যসূত্র-
১) শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সেন্সরশিপঃ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। চলচ্চিত্র সমীক্ষা
২) Documents of the History of the Communist party of India, vol-1, A Adhikari,
৩) বীরেন দাশশর্মা, ভারতীয় তথ্যচিত্রের রাজনৈতিকতা প্রসঙ্গে, সংবর্তক।
৪) Website of The Cinematograph Act- 1952, site of central Board of Film Certificate.
৫) The Cinematograph Act, 1952, Site of Legislative gov.in, PDF file.
৬) অরুণকুমার রায়, বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে দুই ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র ভাবনা, বাংলা চলচ্চিত্রের কথা ও কাহিনি, প্রথম পর্ব, সম্পাদনা- ঋতব্রত ভট্টাচার্য,
৭) সেনসরশিপ, চলচ্চিত্রের অভিধান, সম্পাদক – ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪,
৮) রাজদীপ মুখার্জী, তথ্যচিত্রঃ একটা লড়াই, একটা হাতিয়ার, একটা স্লোগান, সংবর্তক।
৯) দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডকুমেন্টারি চিন্তাভাবনা, এফ তথ্যচিত্র কথকতা, ঋত্বিক সিনে সোসাইটি।
১০) Directory of Indian Documentary FilmMakers, Mumbai International film festival, compiled & Edited by Sanjit Naewekar।
১১) আনন্দ পট্টবর্ধন ‘বিদ্রোহের তরঙ্গ’, (অনুবাদক শান্তনু দাশ), এফ তথ্যচিত্র কথকতা, ঋত্বিক সিনে সোসাইটি।
১২) দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডকুমেন্টারি চিন্তা ভাবনা, এফ তথ্যচিত্রের কথকতা, ঋত্বিক সিনে সোসাইটি।
১৩) গৌতম ঘোষ, ‘চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও আমি’ তথ্যচিত্রের আর্ট ও টেকনিক, সম্পাদক ধীমান দাশগুপ্ত।
১৪) পার্থ রাহা, সিনেমার ইতিবৃত্তান্ত, দে’জ পাব্লিকেশন।
***

Atyonto tatwik o suchintito lekhati .Janar khub darkar chhilo .Dhonyobad.