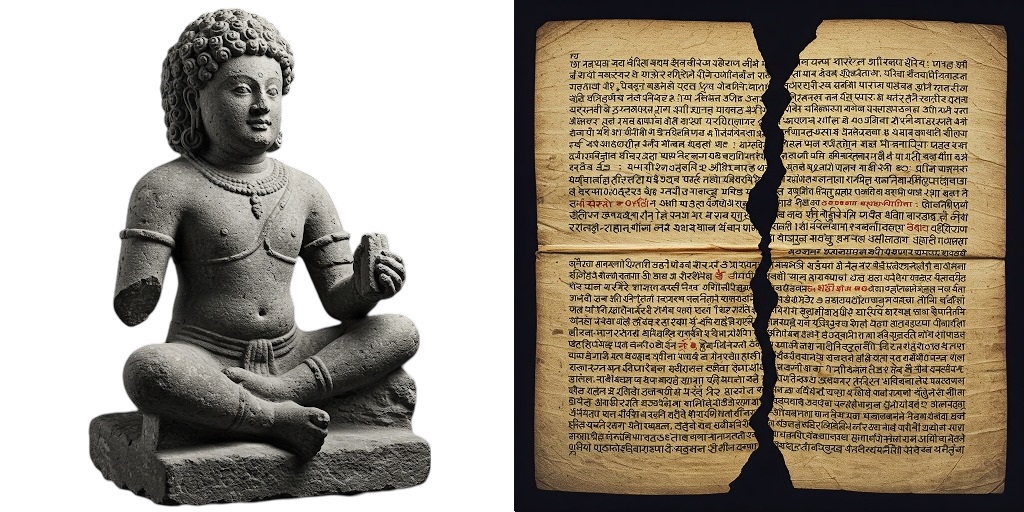
সেতুবন্ধ ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ঐতিহ্য
প্রাককথন
আজ থেকে প্রায় ষোল শ’ বছর আগে বর্তমান মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের এক শাসক প্রবরসেন রামকথার সেতু বন্ধনের ইতিবৃত্তকে প্রাকৃত ভাষায় নিজের কল্পনার রসে জারিত করে লিখেছেন – “সূর্যের রথের চাকার ঘষা খাওয়া উঁচু উঁচু শিখর যুক্ত সব পর্বত হনুমান এনে দিলেন বানর স্থপতি নলকে আর নল তাঁর বাঁ হাত দিয়ে সেই সব পর্বত তুলে সমুদ্রের মধ্যে স্থাপন করে রচনা করলেন এক সেতু।”১ এই একটি উদ্ধৃতিতে যে অনন্য সৃষ্টির ইঙ্গিত, সেই মহাকাব্যকে প্রাকৃত সাহিত্যের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অবেক্ষণ নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়।
প্রাকৃত ভাষায় রামকথা নিয়ে রচিত প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থ সম্ভবত পউমচরিয় (সংস্কৃতে পদ্মচরিত্র)। জৈন ঐতিহ্য অনুযায়ী পউম (পদ্ম), অর্থাৎ রামের জীবনকথা নিয়ে এই কাব্য রচিত। আনুমানিক তৃতীয় বা চতুর্থ শতক সাধারণাব্দে২ জৈন আচার্য বিমলসূরি রচিত ১১৮ সর্গে সমাপ্ত (প্রথম ৩৫টি সর্গ উদ্দেশ ও পরবর্তী ৮৩টি সর্গ পর্ব নামে অভিহিত) পউমচরিয় কাব্য বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনির থেকে অনেকাংশে পৃথক। পউমচরিয় কাব্যে রাম নয়, লক্ষ্মণ রাবণকে বধ করেছেন (৭৩.২৪-২৭)। বিমলসূরি তত্কালীন প্রচলিত রামায়ণ কাহিনিকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি পউমচরিয় গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী (অর্থাৎ বাল্মীকির) রামায়ণ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন, “মৃগ সিংহের নিধন করেছে, কুকুর হাতিকে ভাগিয়ে দিয়েছে, এই রকম বিপরীত আর অসম্ভব কথা দিয়ে পূর্ণ রামায়ণ কবিরা রচনা করেছেন। এই সবই মিথ্যা এবং যুক্তি ও বিশ্বাসের বিরোধী। যিনি পণ্ডিত, তিনি এই রকম বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারেন না।”৩
রাবণবহ (সংস্কৃতে রাবণবধ) বা দহমুহবহ (সংস্কৃতে দশমুখবধ) বা সেতুবন্ধ সম্ভবত বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত রামকথা অনুসরণ করে সৃষ্ট প্রথম ‘পাউঅ মহাকব্ব’ (প্রাকৃত মহাকাব্য)। পূর্ববর্তী ‘রাবণবিজয়’ মহাকাব্য সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ১৫টি আসাসঅ (সংস্কৃতে আশ্বাসক, সর্গের সমতুল্য) বিশিষ্ট এই মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাক্রম সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে (বা লঙ্কাকাণ্ড) বর্ণিত কাহিনির অনুরূপ। সেতুবন্ধ মহাকাব্যের সূচনা হনুমানের লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের বিবরণের মাধ্যমে আর সমাপ্তি রাবণের বধে। এই মহাকাব্যের কাহিনির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ পর্বতসমূহের মাধ্যমে সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধার বিবরণ কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ থেকে পৃথক। এখানে গাছ বা অন্যান্য বস্তুর ব্যবহারের কোনও উল্লেখ নেই।
সেতুবন্ধের কবি
মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত সেতুবন্ধ মহাকাব্য প্রাচীন বিদর্ভের বাকাটক বংশের নন্দীবর্ধন শাখার শাসক দ্বিতীয় প্রবরসেনের (রাজত্বকাল আনুমানিক ৪২২-৪৫৭ সাধারণাব্দ৪) রচনা বলে বুধসমাজে প্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও, সেতুবন্ধ কাব্যের অন্ত-মধ্যযুগের ব্যাখ্যাকার রামদাস, তাঁর ১৬৫২ বিক্রম সংবতে (১৫৯৫ সাধারণাব্দে) রচিত ‘রামসেতুপ্রদীপ’ গ্রন্থের প্রারম্ভে এই মহাকাব্য মহারাজ প্রবরসেনের জন্য মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞায় কালিদাসের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক বিদ্বান অনন্ত সদাশিব অল্টেকর মনে করেন, অন্ত-মধ্যযুগের এই ধারণার উত্পত্তির কারণ খুব সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য কালিদাস দ্বিতীয় প্রবরসেনের শিক্ষকতা সংক্রান্ত ঐতিহ্য।৫ সম্ভবত তিনি সেতুবন্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকার ‘সিরি পবরসেণ বিরইএ কালিদাস কএ (শ্রীপ্রবরসেন বিরচিত, কালিদাস কৃত)’ কথাগুলির ভিত্তিতে এই অনুমান করেছিলেন।
সাধারণাব্দের পঞ্চম শতকের বিদর্ভের বাকাটক শাসক দ্বিতীয় প্রবরসেনের রামকথা নিয়ে কাব্য রচনার সঙ্গে বাকাটক রাজবংশের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তনের সম্পর্ককে উপেক্ষা করা যায় না। বাকাটক রাজবংশের নন্দীবর্ধন (বর্তমানে নাগপুর জেলার নগরধাণ) শাখার প্রথম কয়েক প্রজন্ম শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্যশক্তির পুত্র প্রথম প্রবরসেনের পৌত্র প্রথম রুদ্রসেনকে ‘অত্যন্ত স্বামীমহাভৈরবভক্ত’ বলে লেখে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রুদ্রসেনের দেওটাক শিলালেখে উল্লিখিত চিক্কম্বুরির (বর্তমানে চন্দ্রপুর জেলার চিকমারা) ধর্মস্থানটি (মন্দির) সম্ভবত তাঁর ইষ্টদেবতার জন্যই নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম রুদ্রসেনের পুত্র প্রথম পৃথ্বীসেন ছিলেন ‘অত্যন্তমাহেশ্বর’। কিন্তু, পৃথ্বীসেনের পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেন অভিলেখে চক্রপাণির (বিষ্ণুর) উপাসক বলে উল্লিখিত। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের এই ধর্মীয় পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত তাঁর গুপ্তবংশীয় রাজকুমারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীগুপ্তের সঙ্গে পরিণয়। গুপ্তবংশীয় শাসকরা বৈষ্ণব ছিলেন, প্রভাবতীগুপ্তের পুণে তাম্রশাসনে তাঁর পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ‘পরমভাগবত’ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। পুণে তাম্রশাসনে প্রভাবতীগুপ্তকে ‘অত্যন্ত ভগবতভক্তা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই লেখে তাঁর ভাগবত আচার্য চনালস্বামীকে দানের কথা উল্লিখিত হয়েছে।৬ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের পঞ্চম রাজ্যবর্ষের মান্ঢল তাম্রশাসন থেকে তাঁর মোণ্ডস্বামীর (বিষ্ণু) মন্দির স্থাপনের কথাও জানা গেছে।৭ রামগিরি পর্বত (নাগপুর থেকে ৫৪ কিমি দূরে অবস্থিত বর্তমান রামটেক পাহাড়) বাকাটক রাজধানী নন্দীবর্ধনের অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত। কালিদাস তাঁর ‘মেঘদূত’ কাব্যে (পূর্বমেঘ, ১২) রামগিরিতে রঘুপতি রামের পদচিহ্ন উপাসনার কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় প্রবরসেনের ১৯তম রাজ্যবর্ষে তাঁর মা প্রভাবতীগুপ্তের রিদ্ধপুর তাম্রশাসন জারি করার স্থান রামগিরিস্বামীর পাদমূল এবং তাঁর ২৩তম রাজ্যবর্ষে জারি করা ইন্দোর তাম্রশাসনে উল্লিখিত ভগবত পাদমূল সম্ভবত এই একই স্থান –কালিদাসের মেঘদূত কাব্যেও (পূর্বমেঘ, ২) উল্লিখিত রামগিরি পর্বতের সানুদেশ। এখানে ত্রিবিক্রম, রুদ্র-নরসিংহ ও কেবল-নরসিংহ মন্দির সমেত বাকাটক শাসনকালে নির্মিত বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কয়েকটি উপাসনাগৃহের অবশেষ বিদ্যমান।৮ কেবল-নরসিংহ মন্দিরের দেয়াল থেকে সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় প্রবরসেনের রাজত্বকালের একটি সংস্কৃত লেখে উল্লিখিত ‘প্রভাবতীস্বামী’র প্রতিমা সম্ভবত এই মন্দিরে স্থাপিত নরসিংহ প্রতিমা।৯ অশ্বত্থখেটকে (বর্তমানে বেতুল জেলার পট্টন) অবস্থিত একটি মন্দিরে মহাপুরুষের (বিষ্ণুর) পদচিহ্ন উপাসিত হতো। দ্বিতীয় প্রবরসেন এখানে একটি সত্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করেছিলেন।১০ রামগিরি ও অশ্বত্থখেটকের ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) ধর্মের মন্দিরগুলির মতোই সেতুবন্ধ মহাকাব্য রচনার সঙ্গে দ্বিতীয় প্রবরসেনের মা প্রভাবতীগুপ্তের ভাগবত ধর্মের প্রতি আস্থার গভীর সংযোগ আছে বলে মনে হয়। উল্লেখ্য, সেতুবন্ধ মহাকাব্যে (৬.১৩) রাম বিষ্ণুর অবতারমাত্র নন, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বলে উল্লিখিত। দ্বিতীয় প্রবরসেন নিজে সম্ভবত শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবরসেনের দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষের জাম্ব তাম্রশাসনে ও ২৭তম রাজ্যবর্ষের পট্টন তাম্রশাসনে তাঁকে ‘অত্যন্তমাহেশ্বর’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।১১
দাক্ষিণাত্যের বাকাটক শাসকদের নন্দীবর্ধন ও বত্সগুল্ম উভয় শাখার প্রায় সব অভিলেখই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।১২ তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় প্রবরসেন কেন সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃত ভাষায় সেতুবন্ধ মহাকাব্য রচনা করলেন, তার প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যে, প্রাকৃত ভাষার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।
প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব
মধ্যযুগের ভারতে অধিকাংশ ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিদ্বানরা মনে করতেন প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। দ্বাদশ শতাব্দী সাধারণাব্দের বৈয়াকরণ হেমচন্দ্রের মতে, সংস্কৃত হচ্ছে প্রকৃতি (মূল), যা তার থেকে উত্পন্ন বা তার থেকে আগত (উদ্ভূত), তাই প্রাকৃত।১৩ তবে, একাদশ শতাব্দী সাধারণাব্দের জৈন বিদ্বান নমিসাধু ব্যতিক্রমী; তিনি রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার গ্রন্থের একটি শ্লোকের (২.১২) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, সহজ কথিত ভাষা, যাকে ব্যাকরণ ইত্যাদি দিয়ে সংস্কার করা হয়নি তাই প্রকৃতি। প্রাকৃত প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বা প্রকৃতিই প্রাকৃত। প্রাকৃত প্রাক কৃত, অর্থাৎ সব ভাষার পূর্ববর্তী, সব ভাষার উত্স। এই ভাষার সংস্কারের ফলে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি।১৪
আধুনিক বিদ্বানরা মনে করেন সাধারণাব্দের পূর্ববর্তী প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি থেকে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কথিত ভাষা থেকে পরবর্তীকালে ‘প্রাকৃত’ (মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে পাউঅ, শৌরসেনী প্রাকৃতে পাউদ) নামে অভিহিত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন রূপের প্রসার ঘটে। সম্ভবত বৈদিক ভাষা থেকে উদ্ভূত কথোপকথনের জন্য ব্যবহৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের ফলে এর উদ্ভব। প্রাকৃত ভাষার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান সম্ভবত পাওয়া যায় মহাস্থান ও সোহগৌরা শিলালেখে, সাহিত্যিক মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে এই রূপের মিল যথেষ্ট। মৌর্য সম্রাট অশোকের লেখসমূহে ‘প্রাকৃত’ ভাষার তিনটি পৃথক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় – পূর্বী, পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমা। পূর্বী রূপটির সঙ্গে অর্ধমাগধী ভাষার মিল রয়েছে। পশ্চিমা রূপটির সঙ্গে পালি ভাষার লক্ষণীয় মিল আছে। শাহবাজগড়ি ও মানসেহরা লেখে ব্যবহৃত উত্তর-পশ্চিমা রূপটি বর্তমানে ‘গান্ধারী’ নামে পরিচিত।১৫
কোনও কোনও আধুনিক বিদ্বান মনে করেন, প্রাচীন স্থবিরবাদী বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত পালি নামে পরিচিত ভাষা (প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে মাগধী বলে উল্লিখিত), সাঁচি, বিদিশা, কুষাণ আমলের মথুরা, খারবেলের লেখ সমেত বেশ কিছু প্রাচীন লেখে ব্যবহৃত অভিলেখের মিশ্র সংস্কৃত (বা সংস্কৃতায়িত প্রাকৃত) নামে অভিহিত ভাষা, অশ্বঘোষের সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা এবং প্রাচীন জৈন আগম শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত অর্ধমাগধী (বা আর্ষ প্রাকৃত) ভাষা সবই ‘প্রাচীন প্রাকৃত’ ভাষার রূপভেদ। এখানে উল্লেখ্য, সর্বাস্তিবাদী বা লোকোত্তরবাদী বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ, যেমন মহাবস্তু বা পরবর্তীকালে মহাযানী শাস্ত্রগ্রন্থ ললিতবিস্তরে ব্যবহৃত গাথা, বৌদ্ধ সংস্কৃত বা বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত নামে পরিচিত ভাষার সঙ্গে অভিলেখের মিশ্র সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট মিল আছে এবং ‘প্রাচীন প্রাকৃত’ বলে উল্লিখিত ভাষাসমূহ আদৌ একই ভাষার বিভিন্ন রূপ না কয়েকটি পৃথক সদৃশ ভাষা, তাই নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। এই ভাষা (বা ভাষাসমূহ) ‘প্রাকৃত’ বলে কবে থেকে অভিহিত হয়েছে, তাই নিয়েও আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণাব্দের পূর্ববর্তী প্রথম সহস্রাব্দের শেষদিক থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ও বহির্ভারতে ‘প্রাকৃত’ ভাষার বেশ কয়েকটি সাহিত্যিক রূপ গড়ে উঠতে শুরু করে। আধুনিক বিদ্বানরা এই ভাষাগুলিকে ‘মধ্য প্রাকৃত’ বলে উল্লেখ করেছেন।১৬
গান্ধারী প্রাকৃত
বর্তমান পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের অধিকাংশ, পাঞ্জাব প্রদেশের কিছু অংশ এবং পূর্ব আফগানিস্তানের স্বল্প অংশ প্রাচীন যুগে গান্ধার নামে পরিচিত ছিল। গান্ধার অঞ্চলে সাধারণাব্দের পূর্ববর্তী তৃতীয় শতাব্দী থেকে সাধারণাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, সরকারি দলিল, অভিলেখ ও মুদ্রায় একটি প্রাকৃত বা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। আধুনিক বিদ্বান হ্যারল্ড ওয়াল্টার বেইলি ১৯৪৬ সালে লেখা একটি নিবন্ধে এই ভাষার ‘গান্ধারী’ নামকরণ করেন১৭ এবং এই নামটিই বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্বানদের দ্বারা স্বীকৃত। সম্ভবত প্রাচীন বৈদিক ভাষা বা গান্ধারের অধিবাসী পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে (৩.২.১০৮ ও অন্যত্র) ‘ভাষা’ বলে উল্লিখিত তৎকালীন স্থানীয় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে এই ভাষার উদ্ভব। পালি ও সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষাগুলির সঙ্গে এই ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্য যথেষ্ট। অন্য সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে গান্ধারী ভাষার মৌলিক পার্থক্য হল এই ভাষাটি মূলত কথিত ভাষার সাহিত্যিক রূপ, তাই এই ভাষার কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত রূপ বা বানান ছিল না। এই ভাষার বেশ কিছু শব্দের সঙ্গে বর্তমানে এই অঞ্চলে প্রচলিত দার্দীয় ভাষাগুচ্ছের শব্দমালার যথেষ্ট মিল আছে। শুরু থেকেই এই ভাষা গান্ধার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আকিমিনীয় আমলে প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত আরামীয় লিপি থেকে উদ্ভূত খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা হয়েছে। সাধারণাব্দের তৃতীয় শতক থেকে গান্ধার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খরোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার শুরু হয়ে যায়, এর কিছু কাল আগে থেকেই গান্ধারী ভাষার সংস্কৃতায়নও শুরু হয়ে গিয়েছিল। চীনের জিনজিয়াং-উইগুর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের নিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সাধারণাব্দের তৃতীয় শতকের খরোষ্ঠী লিপিতে কাঠের পাটার উপর লেখা শান শান রাজ্যের সরকারি দস্তাবেজে গান্ধারী ভাষার যে সংস্কৃতায়িত রূপের নিদর্শন পাওয়া যায়, আধুনিক বিদ্বানরা তাকে ‘নিয়া প্রাকৃত’ বলে অভিহিত করেছেন। উনিশ শতকের শেষে এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা বৌদ্ধ ধর্মপদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ভাষাকেও আধুনিক বিদ্বানরা ‘নিয়া প্রাকৃত’ বলে চিহ্নিত করেছেন।১৮
সাহিত্যিক প্রাকৃত
আধুনিক বিদ্বানদের ধারণা ভরত মুনির রচিত বলে জ্ঞাত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি দ্বিতীয় শতাব্দী সাধারণপূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী সাধারণাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের রচনা। এই গ্রন্থে (১৭.৪৯-৫০) ৭টি সাহিত্যিক প্রাকৃত (বা মধ্য ভারতীয়-আর্য) ভাষাকে ‘ভাষা’ নামে অভিহিত করা হয়েছে – মাগধী, অবন্তিজা, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা ও দাক্ষিণাত্যা। একই সাথে ৭টি দ্রাবিড় বা অস্ট্রো-এশীয় ভাষাকে ‘বিভাষা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে – শকার (বা সচর), আভীর, চণ্ডাল, শবর, দ্রমিল ও অন্ধ্রজা (বা ওঢ্রজা) এবং বনচরদের ভাষা।১৯ ষষ্ঠ-সপ্তম শতক সাধারণাব্দ থেকে রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে মুখ্যত চারটি সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ রয়েছে – মাগধী, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী ও পৈশাচী।২০ এই সাহিত্যিক ভাষাগুলির সঙ্গে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চলের (বা জনগোষ্ঠীর) নাম যুক্ত থাকলেও বাস্তবে এই ভাষাগুলি সেখানকার কথিত ভাষার সাহিত্যিক রূপ কখনও ছিল বলে মনে হয় না।২১ পৈশাচী প্রাকৃত ভাষার কথা ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থে উল্লিখিত হলেও এই ভাষার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায়নি। সংস্কৃত নাটকে সংলাপের ভাষা হিসাবে সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ বিষয়ে প্রাচীনতম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে (১৪.৫, ১৭.১-৩)।২২ সাধারণত, সংস্কৃত নাটকে শৌরসেনী প্রাকৃত উচ্চবর্গীয় নারী ও বিদূষকদের সংলাপ এবং মাগধী প্রাকৃত নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের সংলাপের জন্য ব্যবহৃত। সংস্কৃত নাটকের অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃত কবিতা বা সঙ্গীত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। কিন্তু, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় লেখা কাব্যগ্রন্থের ভাষা ও সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে।
চীনের জিনজিয়াং-উইগুর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত সাধারণাব্দের প্রথম শতাব্দে অশ্বঘোষের রচিত শারিপুত্রপ্রকরণ নাটক ও অন্য দু’টি সংস্কৃত নাটকের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিতে প্রথম প্রাকৃত সংলাপ দেখতে পাওয়া যায়।২৩ পরবর্তীকালে ভাস, কালিদাস, শূদ্রক ও ভবভূতির নাটকেও প্রাকৃত ভাষার সংলাপের ব্যবহার দেখা গেছে। কোনও প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব না থাকায় সংস্কৃত নাটকে সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষাসমূহের যে রূপ বর্তমানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখতে পাওয়া যায়, সেই রূপটিই মূল রূপ না প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার্থে পরবর্তীকালের অনুলিপিকারদের সংশোধিত রূপ নিশ্চিতভাবে জানার কোনও উপায় নেই। সাধারণাব্দের নবম শতকের শেষে বা দশম শতকের শুরুতে রাজশেখর প্রাকৃত ভাষায় একটি সম্পূর্ণ নাটক রচনা করেন। তাঁর কর্পূরমঞ্জরী নাটকটি পরবর্তীকালের সাহিত্য বিশ্লেষকদের মতে সট্টক পর্যায়ভুক্ত। মূলত শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষায় লেখা এই নাটকের অন্তর্গত কিছু কবিতা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত।২৪
ভরত রচিত বলে জ্ঞাত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের একটি অংশে (১৭.৬-২৩) প্রাকৃত ব্যাকরণের প্রাচীনতম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই অংশের প্রথম ৪টি শ্লোক (১৭.৬-৯) প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বররুচি রচিত বলে জ্ঞাত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রাকৃতপ্রকাশ গ্রন্থের প্রথম ৯টি অধ্যায় সম্ভবত চতুর্থ বা পঞ্চম শতক সাধারণাব্দে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই ব্যাকরণ গ্রন্থের সাধারণাব্দের সপ্তম শতক বা তারও পরে সংযোজিত শেষ ৩টি অধ্যায়ে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকে আদর্শ বলে মেনে নিয়ে অন্য শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী প্রাকৃত ভাষার পার্থক্যগুলিকে নিয়মবদ্ধ করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত দ্বাদশ শতক সাধারণাব্দে গুজরাতের জৈন বিদ্বান হেমচন্দ্র সূরি (আনুমানিক ১০৮৮-১১৭২ সাধারণাব্দ) তাঁর সিদ্ধহেমচন্দ্র বা সিদ্ধহেম-শব্দানুশাসন গ্রন্থের প্রথম ৭টি অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোচনা করার পর অষ্টম অধ্যায়ে ষড়ভাষার (৬টি ভাষার) ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন – প্রাকৃত, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী, চুলিকাপৈশাচী ও অপভ্রংশ। হেমচন্দ্র প্রাকৃত অর্থে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকেই উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে (৮.১.৩) অর্ধমাগধী নামে অধিকতর পরিচিত জৈন আগমশাস্ত্রের ভাষাকে আর্ষ প্রাকৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বাদশ শতক সাধারণাব্দে ক্রমদীশ্বরও তাঁর সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রথম ৭টি অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোচনা করার পর অষ্টম অধ্যায়ে প্রাকৃত ব্যাকরণের আলোচনা করেছেন। একাদশ বা দ্বাদশ শতক সাধারণাব্দে পূর্ব ভারতের বিদ্বান পুরুষোত্তম তাঁর প্রাকৃতানুশাসন নামের ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী সাধারণাব্দে জৈন বিদ্বান ত্রিবিক্রম প্রাকৃত-শব্দানুশাসন নামে যে ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন, সেখানে ১০৩৬টি সূত্র এবং তার স্বকৃত বৃত্তি, অর্থাৎ ব্যাখ্যা রয়েছে।চণ্ড রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রাকৃতলক্ষণ কবেকার রচনা তাই নিয়ে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে। সম্ভবত ঐতিহ্যগত রীতিতে শেষ প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ ঋষিকেশ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী রচিত প্রাকৃতব্যাকরণ। এই সংস্কৃত গ্রন্থটি ইংরেজি অনুবাদ সমেত ১৮৮৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।২৫
সাধারণাব্দের প্রথম সহস্রাব্দের পর থেকে সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষার চর্চা খুবই কমে আসে। ১৯০৩ সালে ধার শহরে আবিষ্কৃত দুটি পাথরের উপর উত্কীর্ণ আর্যা ছন্দে ১০৯ শ্লোকবিশিষ্ট মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় লেখা কাব্যদ্বয় পরমার বংশীয় শাসক ভোজের (রাজত্বকাল আনু. ১০১১-১০৫৫ সাধারণাব্দ) রচিত বলে উল্লিখিত। অবন্তীকূর্মশতক নামে উল্লিখিত সাধারণাব্দের একাদশ শতকে লেখা এই দুটি প্রাকৃত কাব্যে সাহিত্যগুণের লেশমাত্র নেই।২৬ আধুনিক বিদ্বানদের ধারণা, সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষাসমূহে ‘দেশ্য’ বা ‘দেশি’ নামে অভিহিত স্থানীয় কথিত ভাষাগুলির শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ থেকে ক্রমাগত গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সাধারণাব্দের প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সাহিত্যিক অপভ্রংশ ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। মধ্যযুগে রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণের গ্রন্থসমূহে অনেকগুলি সাহিত্যিক অপভ্রংশ ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে নাগর অপভ্রংশ ভাষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।২৭ তবে, সাহিত্যিক অপভ্রংশ ভাষাসমূহ আদৌ পতঞ্জলির ‘মহাভাষ্য’ গ্রন্থে উল্লিখিত ‘অপভ্রংশ’ ভাষা নয়, পতঞ্জলির উল্লিখিত ‘অপভ্রংশ’ কথাটির অর্থ কথ্য ভাষা, অশুদ্ধ ব্যাকরণযুক্ত বা অমার্জিত ভাষা।২৮
সাহিত্যিক অপভ্রংশ ভাষাগুলির ক্রমশ জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পরিণামে সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষাসমূহের চর্চা কার্যত পরিত্যক্ত হয়। এরপর বিদ্বানদের মধ্যে চর্চা শুরু হয় অবহটঠ ভাষার। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক সাধারণাব্দের মিথিলার কবি বিদ্যাপতি, তাঁর কীর্তিলতা কাব্যের শুরুতে তাঁর অবহটঠ ভাষায় লেখার কারণ হিসাবে বলেছেন, “সংস্কৃত ভাষা বুধজনদের ভালো লাগে, প্রাকৃত ভাষার রসের মর্ম তো আর কেউ বুঝতেই পারে না। দেশি ভাষা সবার কাছে মিষ্টি লাগছে, তাই সেই দেশি ভাষার সমতুল্য অবহটঠ ভাষায় আমার এই রচনা।”২৯ বিদ্যাপতির সমকালীন উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিদ্বৎ সমাজে সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষার সম্পর্কে ধারণা এই মন্তব্যে পরিস্ফুট।
১৬৭৬ সাধারণাব্দ নাগাদ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তাঁর পুত্র আজম খানের পৃষ্ঠপোষকতায় মির্জা খান ফার্সি ভাষায় তুহফাত-উল-হিন্দ (ভারতের উপহার) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রজভাষার ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার, কাব্য, অলঙ্কার, সঙ্গীত এবং জ্যোতিষ গ্রন্থ সম্পর্কে তুহফাত-উল-হিন্দ বিশ্বকোষপ্রতিম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মির্জা খান তিনটি ভাষার উল্লেখ করেছেন – সহঁসকির্ত (সংস্কৃত), পরাকির্ত (প্রাকৃত) ও ভাখা (ব্রজভাষা)। তিনি এই গ্রন্থে প্রাকৃত ভাষাকে পাতাল-বাণী ও নাগ-বাণী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধারণা প্রাকৃত ভাষা সবচেয়ে নিম্নস্তরের মানুষদের এবং জমির নীচে বসবাসকারী সরীসৃপদের ভাষা; রাজা ও মন্ত্রীদের প্রশংসার জন্য পাতালবাসীদের ব্যবহৃত ভাষা। এই ভাষা সংস্কৃত ও ব্রজভাষা মিশিয়ে তৈরি।৩০ স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, সপ্তদশ শতক সাধারণাব্দে উত্তর ভারতের অধিকাংশ বিদ্বানের প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না।
পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে অন্ত-মধ্যযুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের বিদ্বানদের মধ্যে প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা যে অব্যাহত ছিল, তার কয়েকটি নিদর্শন বিদ্যমান। পূর্ব ভারতে সপ্তদশ শতক সাধারণাব্দ পর্যন্ত প্রাকৃত ব্যাকরণ চর্চার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ষোড়শ শতক সাধারণাব্দে ওড়িশার বিদ্বান মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র প্রাকৃতসর্বস্ব ও সপ্তদশ শতক সাধারণাব্দে বাংলার বিদ্বান রামশর্মা তর্কবাগীশ প্রাকৃতকল্পতরু নামের প্রাকৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। দক্ষিণ ভারতে যে প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের চর্চা অষ্টাদশ শতক সাধারণাব্দ পর্যন্ত চলেছিল তার নিদর্শনও বিদ্যমান। ত্রয়োদশ শতক সাধারণাব্দে বিল্বমঙ্গল বা কৃষ্ণলীলাশুক গোবিন্দাভিষেক বা শ্রীচিহ্নকাব্য নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেন। দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত এই মহাকাব্যের শেষ ৪টি সর্গ বিল্বমঙ্গলের শিষ্য দুর্গাপ্রসাদয়তি রচনা করেন। এরপর, শ্রীকণ্ঠ সৌরিচরিত নামের একটি যমককাব্য ও সপ্তদশ শতক সাধারণাব্দে রুদ্রদাস চন্দ্রলেখা নামের সট্টক পর্যায়ভুক্ত একটি নাটক রচনা করেন। অষ্টাদশ শতক সাধারণাব্দের মাঝামাঝি কেরালার রাম পাণিবাদ (নাম্বিয়ার) প্রাকৃত ভাষায় কংসবহো ও উসাণিরুদ্ধ মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন। তিনি প্রাকৃতবৃত্তি নামে বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থও রচনা করেন।৩১
অভিলেখের প্রাকৃত
মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যে, অধিকাংশ শাসকদের লেখমালায় প্রাকৃত ভাষার একটি বিশেষ রূপের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। এই রূপটি অশোকের লেখমালার ভাষার পশ্চিমা রূপের, বিশেষত গিরনার শিলালেখের ভাষার খুবই নিকটবর্তী, সাহিত্যিক প্রাকৃত শৌরসেনীর সঙ্গেও এর যথেষ্ট মিল। এই আমলের বৌদ্ধ স্তূপ ও গুহা মন্দিরে উত্কীর্ণ অভিলেখেও এই একই ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি বানান বা কিছু ব্যাকরণগত পার্থক্য ছাড়া অভিলেখসমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই প্রাকৃত ভাষার রূপের স্থান ও কালভেদে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যায়নি। এই ভাষাকে আধুনিক প্রত্নলিপিশাস্ত্রবিদরা অভিলেখের প্রাকৃত বা সৌধের প্রাকৃত (‘মনুমেন্টাল প্রাকৃত’) অভিধায় চিহ্নিত করেছেন।৩২ এই ভাষাকে ‘স্তূপ প্রাকৃত’ নামেও অভিহিত করা হয়েছে।
উত্তর ও মধ্য ভারতে সাধারণাব্দের পূর্ববর্তী প্রথম শতক থেকে এবং পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্যে সাধারণাব্দের প্রথম শতক থেকে অভিলেখের ভাষা হিসাবে প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। উত্তর ভারতে মথুরার কুষাণ শাসকদের লেখে শেষ সংস্কৃত প্রভাবিত প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার দেখা গেছে। সাধারণাব্দের তৃতীয় শতকের পর থেকে ভারতের প্রায় সর্বত্র শাসকদের লেখমালা (এবং মুদ্রায় উত্কীর্ণ লেখ) থেকে প্রাকৃত ভাষা প্রত্যাহৃত হয় এবং সাধারণাব্দের পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা চলতে থাকে। দাক্ষিণাত্যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর সাতবাহন বংশের উত্থান ঘটে। সাতবাহন শাসকদের আমলের লেখমালা ও মুদ্রায় প্রাকৃত ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ থেকে অনুমান করা যায় সাতবাহন রাজসভার ভাষা ছিল প্রাকৃত। তবে, সাতবাহনদের লেখমালা বা মুদ্রায় ব্যবহৃত ভাষা অভিলেখের প্রাকৃত ভাষা। সাতবাহন শাসনের অবসানের পর তৃতীয় শতাব্দী সাধারণাব্দের গোড়ার দিকে পূর্ব দাক্ষিণাত্যে ইক্ষ্বাকু বংশীয় শাসকরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এই শাসকদের লেখমালায় ব্যবহৃত ভাষা অভিলেখের প্রাকৃত। চতুর্থ শতাব্দী সাধারণাব্দের গোড়ার দিকে ইক্ষ্বাকু বংশের শাসনের অবসানের পর এই অঞ্চল পল্লব শাসকদের অধীনে চলে যায়। সাধারণাব্দের চতুর্থ শতক পর্যন্ত পল্লব শাসকদের লেখেও অভিলেখের প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার দেখা গেছে। চতুর্থ শতক সাধারণাব্দের গোড়ার দিকে বর্তমান উত্তর-পশ্চিম কর্নাটকে কদম্ব বংশীয় শাসকদের উত্থান ঘটে। প্রথম দিকের কদম্ব বংশীয় শাসকদের লেখেও অভিলেখের প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।৩৩ বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক রাজ্যে ষষ্ঠ শতক সাধারণাব্দ পর্যন্ত প্রাকৃত লেখের সন্ধান পাওয়া গেছে।৩৪
সাহিত্যিক মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত ভারতের একমাত্র লেখের নিদর্শন দেখা যায় ছত্তিসগড়ে সাধারণাব্দের পূর্ববর্তী তৃতীয় শতকের জোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত লেখে।৩৫ বর্তমান শ্রীলঙ্কায় সাধারণাব্দের পূর্ববর্তী তৃতীয় শতক থেকে সাধারণাব্দের তৃতীয় বা চতুর্থ শতক পর্যন্ত অভিলেখে ব্যবহৃত সিংহলি প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে প্রাচীন অভিলেখের প্রাকৃত ভাষার বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও, এই ভাষায় উপর মাগধী প্রাকৃত ভাষার প্রভাব দেখা গেছে।৩৬
মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
অধিকাংশ আধুনিক বিদ্বানদের অনুমান, সাধারণাব্দের পূর্ববর্তী কয়েক শতকে বর্তমান মহারাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী কর্ণাটক, গুজরাত, রাজস্থান ও মালব অর্থাৎ পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীদের কথিত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যিক রূপ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। আবার, কারও অনুমান সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে এই প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব উত্তর ভারতে।৩৭ দাক্ষিণাত্যে, বিশেষত বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকায় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত বহু প্রাচীন। সাধারণাব্দের প্রথম শতক বা সম্ভবত তারও আগে রচিত সাত শতাধিক মুক্তক বা ছোটো ছোটো কবিতার সংগ্রহ গাহাসত্তসঈ বা গাহাকোস মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা কাব্যের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। অবশ্য এই কোষগ্রন্থের একাধিক রূপের পরিচয় বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, এই রূপগুলিতে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যাও পৃথক। ২৬০ জন বা তারও বেশি সংখ্যক কবির রচিত এই কবিতা সংগ্রহে প্রাচীন যুগের দাক্ষিণাত্যের সাধারণ মানুষের ভাবনা এবং সম্ভবত তাঁদের ভাষাও প্রতিফলিত। প্রতিষ্ঠানের (বর্তমানে মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগর জেলার পৈঠন শহর) সাতবাহন শাসক হাল এই কাব্যগ্রন্থের সংকলক বলে স্বীকৃত, এই সংকলনে তাঁর লেখা ৪৪টি কবিতাও রয়েছে।
চতুর্থ শতাব্দী সাধারণাব্দে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত হরিবিজয় মহাকাব্য বর্তমানে লুপ্ত। এই কাব্য বাকাটক রাজবংশের প্রথম প্রবরসেনের পুত্র বত্সগুল্ম (বর্তমানে বাশিম জেলার সদর শহর বাশিম) শাখার প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সর্বসেনের (রাজত্বকাল আনু. ৩২৫-৩৫৫ সাধারণাব্দ) রচনা। সর্বসেনের পর মানপুরের (বর্তমানে সাতারা জেলার মান শহর) প্রাচীন রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা মানাঙ্ক (রাজত্বকাল আনু. ৩৭৫-৪০০ সাধারণাব্দ) এবং তাঁর পুত্র দেবরাজও (রাজত্বকাল আনু. ৪০০-৪২৫ সাধারণাব্দ) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে সাহিত্য রচনা করেছেন বলে জ্ঞাত। পঞ্চম শতাব্দী সাধারণাব্দের বাকাটক শাসক দ্বিতীয় প্রবরসেন (রাজত্বকাল আনু. ৪২২-৪৫৭ সাধারণাব্দ) সেতুবন্ধ মহাকাব্য ছাড়া গাহা সত্তসঈ-এর কয়েকটি কবিতারও রচয়িতা বলে জ্ঞাত।
মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় পরবর্তীকালের উল্লেখনীয় মহাকাব্য অষ্টম শতক সাধারণাব্দের শুরুতে বাকপতিরাজের আর্যা ছন্দে লেখা গউড়বহ এবং নবম শতক সাধারণাব্দের গোড়ায় কঊহল (সংস্কৃতে কুতূহল) লীলাবঈ (বা লীলাবঈকহা)। নবম শতক সাধারণাব্দে আনন্দবর্ধনের লেখা বিষমবাণলীলা বর্তমানে লুপ্ত এবং এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। তবে, সেতুবন্ধ মহাকাব্যের মতো প্রসিদ্ধি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত আর কোনও কাব্য অর্জন করতে পারেনি।
জৈন মহারাষ্ট্রী ও জৈন শৌরসেনী
ঐতিহ্য অনুযায়ী পালিত্ত সাধারণাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে তরঙ্গবঈ (সংস্কৃতে তরঙ্গবতী) নামে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে একটি গদ্য কাহিনি রচনা করেছিলেন। তরঙ্গবঈ নামের এক সাধ্বীর বৈচিত্র্যময় জীবনকথা এই কাব্যের বিষয়। পঞ্চম শতক সাধারণাব্দ বা তার পূর্বে রচিত শ্বেতাম্বর জৈন আগমগ্রন্থ অণুওগদ্দারসুত্তে (সংস্কৃতে অনুযোগদ্বারসূত্র) তরঙ্গবঈ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গেছে। মধ্যযুগের জৈন ঐতিহ্য অনুযায়ী, আচার্য পালিত্ত (বা পাদলিপ্তসূরি) প্রতিষ্ঠানের সাতবাহন সভায় অবস্থানকালে তরঙ্গবঈ রচনা করেছিলেন। মূল তরঙ্গবঈ গ্রন্থের কোনও সন্ধান পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালে, আনুমানিক সাধারণাব্দের দশম শতাব্দে এই গ্রন্থের তরঙ্গলোলা (বা সংখিত্ত তরঙ্গবঈ কহা) নামে একটি সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়। এই সংক্ষিপ্তসারের লেখক জস (সংস্কৃতে যশ) মূল গ্রন্থের অনেক ‘দেশি’ (অর্থাৎ কথিত ভাষার) শব্দ বর্জন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।৩৮ তরঙ্গবঈ গ্রন্থের ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত বলে অনুমিত। অনেক আধুনিক বিদ্বান মনে করেন, এই ভাষার উপর প্রাচীন জৈন আগম সাহিত্যের ভাষা অর্ধমাগধীর (আধুনিক বিদ্বানদের মতে অর্ধমাগধী নামকরণের কারণও মাগধীর সঙ্গে মহারাষ্ট্রী ভাষার মিশ্রণ) প্রবল প্রভাবের ফলে সাহিত্যিক মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সঙ্গে এই ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। হেরমান জাকোবি তাঁর ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত দ্য কল্পসূত্র অফ ভদ্রবাহু গ্রন্থের ভূমিকায় প্রাচীন জৈন আগম সাহিত্যের ভাষাকে জৈন প্রাকৃত ও এই ভাষাটিকে জৈন মহারাষ্ট্রী বলে চিহ্নিত করেছেন।৩৯ একই কারণে, অন্য আধুনিক বিদ্বানরা অর্ধমাগধী প্রভাবিত শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষাকে জৈন শৌরসেনী বলে অভিহিত করেছেন। জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় মূলত শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকরা সাহিত্য রচনা করেছেন এবং জৈন শৌরসেনী প্রধানত দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকদের রচিত সাহিত্যের ভাষা। অবশ্য উনিশ ও বিশ শতকের আধুনিক বিদ্বানদের কোনও প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে ধর্মের নাম যুক্ত করে চিহ্নিতকরণ যথাযথ কিনা তাই নিয়ে একুশ শতকে প্রশ্নও তোলা হয়েছে।৪০
জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় প্রাচীনতম রামকথা পউমচরিয় প্রধানত গাথা (বা আর্যা) ছন্দে লেখা। এই ভাষায় রচিত পরবর্তী উল্লেখনীয় গ্রন্থ বসুদেবহিণ্ডী। কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের হিণ্ডী অর্থাৎ ভ্রমণকাহিনি নিয়ে লেখা এই বিশাল গ্রন্থের ২৯টি লম্ভ (সংস্কৃতে লম্বক) বিশিষ্ট প্রথম অংশ সংঘদাসগণি ও ৭১টি লম্ভ বিশিষ্ট শেষ অংশ ধর্মসেনগণি রচনা করেন। সংঘদাসগণি সম্ভবত সাধারণাব্দের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে বসুদেবহিণ্ডী রচনা করেছিলেন। বসুদেবহিণ্ডী মূলত গদ্য রচনা, তবে কিছু কাব্য অংশও রয়েছে। গুণাঢ্যের বর্তমানে লুপ্ত বড্ডকহা (সংস্কৃতে বৃহৎকথা) সাধারণাব্দের প্রথম শতকে পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত বলে মনে করা হয়। এই গ্রন্থের কাহিনি বসুদেবহিণ্ডী গ্রন্থের সংঘদাসগণি রচিত অংশে অনুসৃত হয়েছে। জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত আর একটি উল্লেখনীয় গ্রন্থ সাধারণাব্দের অষ্টম শতকে রাজস্থানের জৈন বিদ্বান হরিভদ্রসূরি রচিত সমরাইচ্চকহা (সংস্কৃতে সমরাদিত্যকথা)। মূলত গদ্যে রচিত সমরাইচ্চকহা গ্রন্থের ভাষা বহুল পরিমাণে সংস্কৃত প্রভাবিত। ৭৭৯ সাধারণাব্দে রাজস্থানের আর এক জৈন বিদ্বান উদ্যোতন সূরি কুবলয়মালা নামের একটি চম্পূকাব্য রচনা করেন। মূলত জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় লেখা হলেও এই কাব্যগ্রন্থে সংস্কৃত, পেসায়া (পৈশাচী প্রাকৃত) এবং অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ১০৩২ সাধারণাব্দে আচার্য দুর্গদেব জৈন শৌরসেনী ভাষায় রিষ্টসমুচ্চয় নামের একটি জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ১০৩৮ সাধারণাব্দে ধনেশ্বর জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় সুরসুন্দরীচরিয় নামের একটি কাব্য রচনা করেন। সাধারণাব্দের চতুর্দশ শতকে শ্বেতাম্বর জৈন জয়বল্লভ বজ্জালগ্গ (সংস্কৃতে ব্রজ্যালগ্ন) গ্রন্থে জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত বহুসংখ্যক মুক্তক অনেকগুলি বজ্জায় (সংস্কৃত ব্রজ্যা অর্থাৎ গুচ্ছ) বিভক্ত করে সংকলন করেন।
সাধারণাব্দের প্রথম সহস্রাব্দের শেষ কয়েক শতকে জৈন মহারাষ্ট্রী ও জৈন শৌরসেনী উভয় ভাষার চর্চাই কমে আসে, জৈন অপভ্রংশ ভাষায় ধর্মাশ্রয়ী রচনার প্রচলন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আনুমানিক অষ্টম শতক সাধারণাব্দে রামকথা নিয়ে স্বয়ম্ভু রচিত পউমচরিউ জৈন অপভ্রংশ ভাষায় উল্লেখনীয় কৃতি।
সেতুবন্ধ ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ঐতিহ্য
আদি-মধ্যযুগের সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থে সেতুবন্ধ কাব্যের পূর্ববর্তী দু’টি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় লেখা মহাকাব্যের উল্লেখ রয়েছে – রাবণবিজয় ও হরিবিজয়। এর মধ্যে, রাবণবিজয় মহাকাব্যের ভোজ রচিত শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি শ্লোক ছাড়া কিছুই জানা যায়নি। সাধারণাব্দের সপ্তম শতকে রচিত দণ্ডীর অবন্তীসুন্দরী কাব্যের শুরুতে হরিবিজয় মহাকাব্যের উল্লেখ রয়েছে। আনন্দবর্ধন রচিত ধ্বন্যালোক, অভিনবগুপ্ত রচিত ধ্বন্যালোকের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ লোচন, কুন্তকের বক্রোক্তিজীবিত, ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশ ও হেমচন্দ্র রচিত কাব্যানুশাসন গ্রন্থে সর্বসেনের হরিবিজয় সম্পর্কে উল্লেখ এবং ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশ ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থদ্বয়ে হরিবিজয় গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত কাব্যাংশ থেকে এই মহাকাব্যটির বিষয়বস্তু ও রচনারীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। হরি অর্থাৎ কৃষ্ণের তাঁর পত্নী সত্যভামার জন্য ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে আসার কাহিনি এই মহাকাব্যের উপজীব্য।৪১
সেতুবন্ধ, রাবণবহ বা দহমুহবহ মহাকাব্য মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত কাব্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে মূলত স্কন্ধক ছন্দে রচিত। তবে ১৩৬২টি শ্লোকের মধ্যে ৪০টি শ্লোক গলিতক ছন্দে লেখা, আর লম্বিতা, কুমুদিনী, ললিতা, উগ্রগলিতক, মালাগলিতক ও সুন্দরা ছন্দও ব্যবহার করা হয়েছে। ভোজ তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থে সেতুবন্ধ ও তার পূর্ববর্তী দুটি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত মহাকাব্য রাবণবিজয় ও হরিবিজয় শুধুমাত্র একটি ছন্দেই রচিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিদ্বৎজন এই মহাকাব্যগুলিতে গলিতক ছন্দে রচিত অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।৪২ আধুনিক বিদ্বানরা সেতুবন্ধের রচনারীতি পূর্ববর্তী হরিবিজয় মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন। বিদর্ভের দুই বাকাটক শাসক, বত্সগুল্ম শাখার সর্বসেন ও নন্দীবর্ধন শাখার প্রবরসেনের রচনারীতিই সম্ভবত সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যের বৈদর্ভী বা বত্সগুল্মী রীতির নামকরণের উত্স।৪৩
প্রাকৃত সাহিত্যে প্রবরসেনের সেতুবন্ধ মহাকাব্যের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণাব্দের সপ্তম শতকের সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিদ দণ্ডীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে (১.৩৪) বলেছেন, “মহারাষ্ট্রে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা সবচেয়ে উত্কৃষ্ট বলে বিদিত। কারণ, রত্নের আকর সাগরের মতো, সেতুবন্ধ ও অন্যান্য সুলিখিত কাব্যের আকর এই ভাষা।”৪৪ দণ্ডীর মতে, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত আদর্শ সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষা এবং সেতুবন্ধ এই ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।
সাধারণাব্দের প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবরসেনের সেতুবন্ধ মহাকাব্য যে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সেই সময়কার বিদ্বানদের মন্তব্য তার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। সপ্তম শতকে বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিত গ্রন্থে প্রবরসেনের সেতুবন্ধ মহাকাব্যের প্রশংসা করে বলেছেন, “বানর সেনার নির্মিত সেতু যেমন একদিন সাগরের পরপারে পৌঁছে দিয়েছিল, তেমনই প্রবরসেনের কুমুদের মতো (সেতুবন্ধ রূপ) শুভ্র উজ্জ্বল কীর্তি (তাঁর খ্যাতিকে বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে)।”৪৫ আদি-মধ্যযুগে সেতুবন্ধের খ্যাতি বাস্তবেই সমুদ্র পার হয়ে কম্বোডিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। নবম শতকের শেষ দিকের কম্বোডিয়ার খমের সম্রাট প্রথম যশোবর্মনের (রাজত্বকাল ৮৮৯-৯০০ সাধারণাব্দ) একটি সংস্কৃত অভিলেখে ও তাঁর সেতুবন্ধ মহাকাব্যের উল্লেখ পাওয়া গেছে।৪৬
অন্ত-মধ্যযুগে সেতুবন্ধ কাব্যের রচয়িতা প্রবরসেনের ঐতিহাসিক পরিচিতি বিদ্বৎসমাজে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। পঞ্চদশ শতক সাধারণাব্দের কেরালার কৃষ্ণকবি তাঁর ভরতচরিত নামের কাব্যগ্রন্থে (১.৪) প্রবরসেনকে কুন্তলেশ অর্থাৎ কুন্তলের শাসক বলে উল্লেখ করেছেন। কুন্তল বলতে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের যে অঞ্চল ইতিহাসে পরিচিত, বিদর্ভ তার থেকে অনেক দূরবর্তী। সেতুবন্ধ কাব্যের কয়েকটি অন্ত-মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় পবরসেণকে (সংস্কৃতে প্রবরসেন) চাহুআন (অর্থাৎ চৌহান) বংশীয় শাসক বলা হয়েছে। অন্ত-মধ্যযুগের সেতুবন্ধ মহাকাব্যের দক্ষিণ ভারতের টীকাকার কৃষ্ণবিপ্র তাঁকে প্রাকৃতদের মহারাজা বলে উল্লেখ করেছেন। অন্ত-মধ্যযুগে কবির পরিচিতি লুপ্ত হলেও প্রাকৃত সাহিত্যের বিদ্বানদের কাছে সেতুবন্ধ কাব্যের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি।
আদি-মধ্যযুগে সেতুবন্ধ কাব্যের প্রথম জ্ঞাত ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচনা করেন সাহসাঙ্ক, আধুনিক বিদ্বানদের মতে ইনি দশম শতাব্দী সাধারণাব্দের পরমার বংশীয় শাসক সিন্ধুরাজ। এর পরবর্তী ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের রচয়িতা একাদশ শতাব্দী সাধারণাব্দের প্রথমার্ধের কামরূপের শাসক হর্ষপাল। সাম্প্রতিক কালে নেপালে এই গ্রন্থের তালপত্রের উপর লেখা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। হর্ষপাল তাঁর গ্রন্থ রচনার জন্য সাহসাঙ্কের গ্রন্থের ও প্রাকৃতকোবিদদের সহায়তা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।৪৭ অন্ত-মধ্যযুগে সেতুবন্ধ মহাকাব্যের বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীনিবাস রচিত সেতুদর্পণ সম্ভবত এর মধ্যে প্রাচীনতম রচনা, এই গ্রন্থের ১৪৪০ সাধারণাব্দে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত মোগল সম্রাট আকবরের দরবারের রাজস্থানের বিদ্বান রামদাস রচিত রামসেতুপ্রদীপ, দক্ষিণ ভারতের বিদ্বান কৃষ্ণবিপ্র রচিত সেতুবিবরণ (বা সেতুব্যাখ্যান) ও বিশ্বনাথ রচিত সেতুতত্ত্বচন্দ্রিকা সর্বাধিক পরিচিত। সেতুতত্ত্বচন্দ্রিকা গ্রন্থে পূর্ববর্তী লেখক লোকনাথ, সাহসাঙ্ক ও হর্ষপালের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেখা যায়। বাংলার বিদ্বান কুলনাথের দশমুখবধবিবরণ, কেরালার বিদ্বান মাধবযজ্বার সেতুতাত্পর্যটীকা এবং মল্লভট্ট (বা মুদমল্লভট্ট) রচিত সেতুচন্দ্রিকা প্রমুখ ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থও বিদ্যমান। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে অম্বষ্ঠ শিবনারায়ণদাস ‘সেতুসরণি’ নামে এই গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় একটি কাব্যানুবাদ করেন।
উনিশ শতকে ভারত থেকে সেতুবন্ধ মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি ইউরোপে পৌঁছানোর পর জার্মানির সংস্কৃত বিদ্বানদের মধ্যে চর্চা শুরু হয়। ১৮৮০ সালে সেতুবন্ধ মহাকাব্যের প্রথম সমীক্ষাত্মক সংস্করণ স্ট্রাসবার্গ থেকে সিগফ্রিড গোল্ডস্মিড্ট-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এরপর, ১৮৮৪ সালে স্ট্রাসবার্গ থেকেই এই গ্রন্থের সিগফ্রিড গোল্ডস্মিড্ট কৃত জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালে প্রাকৃত টেক্সট সোসাইটি আহমেদাবাদ থেকে এই মহাকাব্যের কৃষ্ণ কান্ত হাণ্ডিকি কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে। সেতুবন্ধ গ্রন্থের রঘুবংশ কৃত প্রথম হিন্দি অনুবাদ রাজকমল প্রকাশন এলাহাবাদ থেকে প্রকাশ করে। এরপর, ২০০২ সালে চৌখম্ভা ভারতী অকাদমী বারাণসী থেকে ‘সেতুবন্ধ’ মহাকাব্যের আশা কুমারী কৃত একটি হিন্দি ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে।
শেষকথন
ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছে বহু সংখ্যক সাহিত্যকর্ম এবং এই রচনাসম্ভারের এক বৃহৎ অংশ জৈন ধর্মাশ্রিত। আজ থেকে দুই সহস্রাব্দ পূর্বে প্রাকৃত ভাষার সাংস্কৃতিক বিস্তার উপমহাদেশের বাইরে আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্য উচ্চবর্গীয় বিদগ্ধজন এবং প্রাকৃত সাহিত্য নিম্নবর্গীয় প্রাকৃতজনের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত, এই রকম একটি দ্বিমাত্রিক ধারণা বহু কাল ধরে প্রচলিত থাকলেও, এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশগুলি উচ্চবর্গের বিদ্বানদের সাহিত্যিক প্রাকৃত চর্চার নিদর্শন। সাধারণাব্দের প্রথম সহস্রাব্দ জুড়ে সৃষ্ট প্রাকৃত কাব্য, বিশেষত, গাহাসত্তসঈ, তরঙ্গবঈ, হরিবিজয়, পউমচরিয়, সেতুবন্ধ বা সমরাইচ্চকহার মতো নান্দনিক গুণসম্পন্ন রচনা উচ্চবর্গের মধ্যে প্রাকৃত সাহিত্য চর্চার গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে।
প্রাকৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে সেতুবন্ধ মহাকাব্যের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য সংস্কৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে পৃথকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন রূপের (বা ভাষাগুচ্ছের) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাসের চর্চা আবশ্যক। একই সাথে প্রাকৃত সাহিত্য সম্পর্কে ঐতিহ্যগত নান্দনিক ভাবনাকে আধুনিক চিন্তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন আছে।
টীকা
১. “জং জং আণেই গিরিং রহিরহচক্কপরিমট্টসিহরং হণুমা।/ তং তং লীলাই ণলো বামকরুত্থম্বিঅং রএই সমুদ্দে॥” – প্রবরসেন, সেতুবন্ধ ৮.৪৩; দেখুন: Śivadatta and Kāśīnāth Pāṇḍurang Parab edited, ‘The Setubandha of Pravarasena with the Commentary of Rāmadāsa Bhūpati’; Bombay: Nirṇaya Sāgar Press, second edition,1935, p. 267।
২. K.R. Chandra, ‘A Critical Study of Paumacariyaṁ’; Vaishali (Muzaffarpur): Research Institute of Prakrit, Jainology & Ahimsa, 1970, p. 16.
৩. “সীহো মএণ নিহও সাণেণ য কুঞ্জরো জহা ভগ্গো।/ তহ বিবরীয়পয়ত্থং কঈহি রামায়ণং রইয়ং॥/ অলিয়ং পি সব্বমেয়ং উববত্তিবিরুদ্ধপচ্চয়গুণেহিং।/ ন য সদ্দহন্তি পুরিসা হবন্তি তে জে পণ্ডিয়া লোএ॥” – বিমলসূরি, পউমচরিয় ২.১১৬-১১৭; দেখুন: H. Jacobi edited and Shantilal M. Vora translated, ‘Ācārya Vimalasūri’s Paumacariyaṃ with Hindi Translation Part I’; Ahmedabad: Prakrit Text Society, 2005, p. 17।
৪. Hans T. Bakker, ‘The Vākāṭakas: An Essay in Hindu Iconology’; Groningen: Egbert Forsten, 1997, p. 170.
৫. Ramesh Chandra Majumdar and Anant Sadashiv Altekar edited, ‘The Vākāṭaka-Gupta Age (Circa 200-550 A.D.)’; Banaras: Motilal Banarsi Dass, 1946, pp. 372-373.
৬. Vasudev Vishnu Mirashi, ‘Inscriptions of the Vākāṭakas, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 5’; Ootacamund: Government Epigraphist of India, 1963, pp. xl-xli, 5-9.
৭. Hans T. Bakker, ‘The Vākāṭakas: An Essay in Hindu Iconology’, pp. 18-19.
৮. Hans Bakker, “The Antiquities of Ramtek Hill, Maharashtra” in ‘South Asian Studies, Volume 5, Issue 1’; Routledge, 1989, pp. 79-102; আরও দেখুন: A.P. Jamkhedkar, “Anicient Structures” in ‘Marg, Vol. XXXVII, No. 1’; Bombay: Marg Publications, 1985, pp. 25-36.
৯. Hans T. Bakker and Harunaga Isaacson, “The Ramtek Inscriptions II: The Vākāṭaka Inscription in the Kevala-Narasiṃha Temple” in ‘Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 56, No. 1’; Cambridge University Press, 1993, pp. 46-74.
১০. Vasudev Vishnu Mirashi, ‘Inscriptions of the Vākāṭakas, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 5’, p. xli.
১১. Ibid, pp. 12, 60.
১২. Ibid, p. liii.
১৩. অতীন্দ্র মজুমদার, ‘মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য’; কলিকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৬০ পৃ. ৮৩; হেমচন্দ্র তাঁর ‘সিদ্ধহেমচন্দ্র’ গ্রন্থে (৮.১.১) লিখেছেন, “প্রকৃতি সংস্কৃতম্। তত্র ভবং তত্র আগত বা প্রাকৃতম্।“ দেখুন: P.L. Vaidya edited, ‘Prakrit Grammar of Hemaçandra, Being the Eighth Chapter of his Siddhahemacandra’; Poona: Motilal Ladhaji, 1928, p.1; মধ্যযুগের অন্য ভারতীয় বিদ্বানদের মত সম্পর্কে দেখুন: R. Pischel (translated from German by Subhadra Jha), ‘Comparative Grammar of the Prakrit Languages’; Varanasi: Motilal Banarsidass, 1957, p.1।
১৪. “সকলজগজ্জন্তূনাং ব্যাকরণাদিভিরনাহিতসংস্কারঃ সহজো বচনব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ। তত্র ভবং সৈব বা প্রাকৃতম্। ‘আরিসবয়ণে সিদ্ধং দেবাণং অদ্ধমাগহা বাণী’ ইত্যাদি বচনাদ্যা প্রাক্পূর্বং বালমহিলাদিসুবোধং সকলভাষানিবন্ধনভূতং বচনমুচ্যতে। মেঘনির্মুক্তজলভিবৈকস্বরূপং তদেব চ দেশবিশেষাৎসংস্কারকরণাঞ্চ সমাসাদিতবিশেষং সৎসংস্কৃতাদ্যুত্তরবিভেদানাপ্নোতি। অত এব শাস্ত্রকৃতা প্রাকৃতমাদৌ নির্দিষ্টং সংস্কৃতাদীনি। পাণিন্যাদি ব্যাকরণোদিতশব্দলক্ষণেন সঙ্করণাৎসংস্কৃতমুচ্যতে।” – দেখুন: কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সম্পাদিত, ‘শ্রীরুদ্রটপ্রণীতঃ কাব্যালঙ্কারঃ নমিসাধু কৃতয়া টিপণ্যা সমেতঃ’; মুম্বই: নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয়, ১৮৮৬, পৃ. ১৩।
১৫. Richard Salomon, ‘Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and the Other Indo-Aryan Languages’; New York: Oxford University Press, 1998, pp. 73-76.
১৬. Alfred C. Woolner, ‘Introduction to Prakrit’; Lahore: University of Panjab, 2nd edition, 1928, pp. 2-3.
১৭. H.W. Bailey, “Gāndhārī” in ‘Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 11, No. 4’; London: Cambridge University Press, 1946, pp. 764-797.
১৮. T. Burrow, “The Dialectical Position of the Niya Prakrit” in ‘Bulletin of the School of Oriental Studies (University of London), Vol. 8, No. 2/3, Indian and Iranian Studies: Presented to George Abraham Grierson on His Eighty-Fifth Birthday, 7th January, 1936’; London: Cambridge University Press, 1936, pp. 419-435.
১৯. M. Ramakrishna Kavi edited, ‘Nāṭyaśāstra with the commentary of Abhinavagupta, Vol. II’; Baroda: Oriental Institute, 1934, p. 376; আরও দেখুন: Natalia Lidova, “The Nāṭyaśāstra: the Origin of the Ancient Indian Poetics” in ‘Cracow Indological Studies, Issue 14’; Księgarnia Akademicka, 2012, pp. 61-85।
২০. বররুচি, ‘প্রাকৃতপ্রকাশ’ ১০.১, ১১.১, ১২.১ ও ১২.৩২; দেখুন: Rāmachandra Jhā edited, ‘The Prākṛta-Prakāśa of Vararuchi with the Manoramā Commentary of Bhāmaha’; Banaras: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, third edition, 1949, pp. 99, 102, 106, 111।
২১. সুকুমার সেন, ‘ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস’; কলকাতা: ভারবি, ১৯৯২, পৃ. ২৫৯।
২২. M. Ramakrishna Kavi edited, ‘Nāṭyaśāstra with the commentary of Abhinavagupta, Vol. II’, pp. 225, 365-366.
২৩. জগদীশচন্দ্র জৈন, ‘প্রাকৃত সাহিত্য কা ইতিহাস’; বারাণসী: চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬১, পৃ. ৬১৪।
২৪. Richard Salomon, “The Original Language of the Karpūra-mañjarī” in ‘Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Vol. 132, No. 1’; Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1982, pp. 119-141.
২৫. Hartmut Scharfe, ‘Grammatical Literature, A History of Indian Literature, Vol. V, Fasc. 2’; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1977, pp. 191-194; আরও দেখুন: D.C. Sircar, ‘Grammar of the Prakrit Language, Based Mainly on Vararuchi, Hemachandra and Purushottama’; Delhi: Motilal Banarsidass, second enlarged edition, 1970, pp. 1-8.
২৬. Richard Pischel, “Two Prakrit Poems at Dhar” in ‘Epigraphia Indica, Vol. VIII, 1905-06’; Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1906, pp. 241-260.
২৭. George Abraham Grierson, ‘Linguistic Survey of India, Vol. 1, Part 1’; Calcutta: Government of India Central Publication Branch, 1927, pp. 123-124.
২৮. Suniti Kumar Chatterji, ‘The Origin and Development of the Bengali Language, Part I: Introduction, Phonology’; Calcutta: Calcutta University Press, 1926, p. 89.
২৯. “সক্কঅ বাণী বুহঅন ভাবই।/ পাউঅ-রস কোই মম্ম ন পাবই॥/ দেসিল বঅনা সবজন মিটঠা।/ তেঁ তৈসন জম্পও অবহটঠা॥” – বিদ্যাপতি, ‘কীর্তিলতা’ ১.১৪; দেখুন: বাবুরাম সকসেনা সম্পাদিত ও অনূদিত, ‘মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠক্কুর কৃত কীর্তিলতা’; কাশী: নাগরীপ্রচারিণী সভা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃ. ৬।
৩০. M. Ziauddin edited and translated, ‘A Grammar of the Braj Bhakha by Mīrzā Ḵhān (1676 A.D.)’; Calcutta: Visva-Bharati Book Shop, 1936, p. 34.
৩১. A.N. Upadhye edited and translated, ‘Rāma Pānivāda’s Kaṁsavaho’; Bombay: Hindi Grantha Ratnākara Kāryālaya, 1940, pp. xv-xxiii.
৩২. E. Senart, (G.A. Grierson translated and author revised), “Monumental and Literary Prakrit” in ‘The Indian Antiquary, A Journal of Oriental Research, Vol. XXI’; Bombay: Education Society’s Press, 1892, p. 258.
৩৩. Sheldon Pollock, ‘The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India’; Berkeley: University of California Press, 2006, pp. 115-119.
৩৪. K. Rajan, “Situating the Beginning of Early Historic Times in Tamil Nadu: Some Issues and Reflections” in ‘Social Scientist, Vol. 36, No. 1-2, January – February 2008’; New Delhi, 2008, pp. 40-78.
৩৫. K.P. Jayaswal, “The Jogīmārā Cave Inscription” in ‘The Indian Antiquary, A Journal of Oriental Research, Vol. XLVIII, 1919’; Delhi: Swati Publications, 1985, p. 131; বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন: T. Bloch, “Caves and Inscriptions in Rāmgarh Hill” in ‘Archaeological Survey of India, Annual Report, 1903-04’; Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1906, pp. 123-131 ।
৩৬. Richard Salomon, ‘Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and the Other Indo-Aryan Languages’, pp. 79-80.
৩৭. Manomohan Ghosh, “Mahārāṣṭrī, A Later Phase of Śauraseni” in ‘Journal of the Department of Letters, University of Calcutta, Vol. XXIII’; Calcutta: University of Calcutta, 1933, pp. 1-24.
৩৮. Andrew Ollett, “The Taraṅgavatī and History of Prakrit Literature” in Nalini Balbir and Peter Flügel edited, ‘Jaina Studies: Selected Papers Presented in the ‘Jaina Studies’ Section at the 16th World Sanskrit Conference, Bangkok, Thailand and the 14th World Sanskrit Conference, Kyoto, Japan’; New Delhi: DK Publishers, 2018, pp. 129-164.
৩৯. Hermann Jacobi edited, ‘The Kalpasûtra of Bhadrabâhu’; Leipzig: In Commission bei F.A. Brockhaus, 1879, p. 17.
৪০. Andrew Ollett, ‘Language of the Snakes: Prakrit, Sanskrit, and the Language Order’; Oakland, California: University of California Press, 2017, p. 54.
৪১. V. Raghavan, ‘Bhoja’s Śṛṅgāra Prakaśa’; Madras: Punarvasu, 1978, pp. 810-811; এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: A.K. Warder, ‘Indian Kāvya Literature, Vol. 3, Early Medieval Period (Śūdraka to Viśākhadatta)’; Delhi: Motilal Banarsidass, 1977, pp. 59-63; হরিবিজয় মহাকাব্য সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন: V.M. Kulkarni, “The Hari-Vijaya of Sarvasena” in R.N. Dandekar edited, ‘Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. 58/59, Diamond Jubilee Volume (1977-1978)’; Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1978, pp. 691-710 ।
৪২. “ননু চাশ্বাসকবন্ধেষু তৎসমাপ্তাবপি ন চ্ছন্দোভেদ উপলভ্যতে। তথা হি রাবণবিজয় হরিবিজয় সেতুবন্ধেষু আদিতস্সমাপ্তিপর্যন্তমেকমেব চ্ছন্দো ভবতি। গলিতকানি তু ব্যাসকষ্টবৎ কৈরপি বিদগ্ধমানিভিঃ উপক্ষিপ্তানীতি তদ্বিদো ভাষন্তে” – ভোজ, শৃঙ্গারপ্রকাশ ১১.৩৭২; দেখুন: Rewāprasāda Dwivedī and Sadāśivakumāra Dwivedī edited, ‘Śṛṅgāraprakāśa (Sāhityaprakāśa) by Bhojarāja, Vol. I (1-14 Prakāśa)’; New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts and Varanasi: Kālidāsa Samsthāna, 2007, p. 679।
৪৩. রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নাটকে (১.১) বচ্ছোমী (সংস্কৃতে বত্সগুল্মী) কথাটি বৈদর্ভীর সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে; দেখুন: V.V. Mirashi, “The Home of the Vākāṭakas” in ‘Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. XXXII, Parts I-IV’; Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1951, pp. 1, 1n1।
৪৪. “মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।/ সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্॥” – দণ্ডী, কাব্যাদর্শ ১.৩৪; দেখুন: S.K. Belvalkar, ‘Kāvyādarṣa of Daṇḍin: Sanskrit Text and English Translation’; Poona: The Oriental Book Supplying Agency, 1924, p. 3।
৪৫. “কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।/ সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥” – বাণভট্ট, ‘হর্ষচরিত’, ভূমিকা, ১৪; দেখুন: P.V. Kane edited, ‘The Harshacharita of Bāṇabhatta (Uchchāsas I-VIII)’; Bombay: Published by author, 1918, p. 2।
৪৬. “যেন প্রবরসেনেন ধর্মসেতুং বিবৃণ্বতা।/ পরঃ প্রবরসেনোঽপি জিতঃ প্রাকৃতসেতুকৃত॥” – R.C. Majumdar, ‘Inscriptions of Kambuja’; Calcutta: The Asiatic Society, 1953, p. 99; আরও দেখুন, M.A. Barth, ‘Inscriptions Sanscrites du Cambodge’; Paris: Imprimerie Nationale, 1885, p. 254 [434]।
৪৭. Diwakar Acharya, “A Brief Note on Harṣapāla’s Commentary on the Prakrit Kāvya Setubandha” in ‘Newsletter of the Nepalese–German Manuscript Cataloguing Project, Number 2, October 2006’; pp. 2-4.
আকর গ্রন্থপঞ্জি
সেতুবন্ধ: মূল ও অনুবাদ
১. Siegfried Goldschmidt, ‘Rāvaṇavaha oder Setubandha, Prākṛt und Deutsch Herausgegeben, 1. Text, Index’; Strassburg: Verlag von Karl Trübner, 1880.
২. Siegfried Goldschmidt, ‘Rāvaṇavaha oder Setubandha, Prākṛt und Deutsch Herausgegeben, 2. Übersetzung’; Strassburg: Verlag von Karl Trübner, 1884.
৩. Śivadatta and Kāśīnāth Pāṇḍurang Parab edited, ‘The Setubandha of Pravarasena with the Commentary of Rāmadāsa Bhūpati’; Bombay: Nirṇaya Sāgar Press, second edition,1935.
৪. Radhagovinda Basak edited, ‘Pravarasena’s Rāvanavaha-Mahākāvyam with the Commentary of Setu-Tattva-Candrikā’; Calcutta: Sanskrit College, 1959.
৫. Krishna Kanta Handiqui translated, ‘Pravasena’s Setubandha’; Ahmedabad: Prakrit Text Society, 1976.
প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য
১. Alfred C. Woolner, ‘Introduction to Prakrit’; Lahore: University of Panjab, 2nd edition, 1928.
২. Andrew Ollett, ‘Language of the Snakes: Prakrit, Sanskrit, and the Language Order’; Oakland, California: University of California Press, 2017.
৩. D.C. Sircar, ‘Grammar of the Prakrit Language, Based Mainly on Vararuchi, Hemachandra and Purushottama’; Delhi: Motilal Banarsidass, second enlarged edition, 1970.
৪. George Abraham Grierson, ‘Linguistic Survey of India, Vol. 1, Part 1’; Calcutta: Government of India Central Publication Branch, 1927, pp. 121-133.
৫. পরেশচন্দ্র মজুমদার, ‘সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ’; কলিকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৬১।
৬. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস’ কলিকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৬০।
৭. R. Pischel (translated from German by Subhadra Jha), ‘Comparative Grammar of the Prakrit Languages’; Varanasi: Motilal Banarsidass, 1957.
