
অথ অশ্ব কথা
॥শুরুর কথা॥
শের শাহ প্রথম ঘোড়ার ডাক প্রচলন করেন। স্কুলের ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। তার আগে ঘোড়া ডাকতো না? রসিকতা তো বটেই। কিন্তু এটা সত্যি ঘোড়ার জাতি-বংশ রঙ স্বাস্থ্য সব এখন মানুষের নিয়ন্ত্রণে।
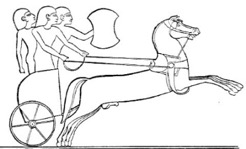
মিশরের দেওয়ালচিত্রে হিট্টাইটদের রথ
মানব সভ্যতার উপরে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছে একটি প্রাণী, ঘোড়া। ঘোড়া না থাকলে মানব ইতিহাসটাই আমূল পাল্টে যেত। কৃষিকাজে ঘোড়ার ব্যবহার হয়ত অনেকটাই সীমিত, কিন্তু যাতায়াতে, বিশেষ করে দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার জন্য ঘোড়া অতুলনীয়। অবশ্যই সপরিবারে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবহারই হয়ত প্রাচীনতম এবং জনপ্রিয়তমও ছিল। বিশেষ করে যখন স্পোক লাগানো হাল্কা চাকার আবিষ্কার হয়নি, তখন সেই ভার বহনের জন্য গরু মোষ ছিল অপরিহার্য। কিন্তু একক ব্যক্তির দ্রুতগতির জন্য ঘোড়া ছিল একমাত্র সম্বল। ঘোড়ার ব্যবহারের আগে একক ব্যক্তি বা ছোট দলের ভ্রমণের পরিধি থাকত সীমাবদ্ধ। কারণ হয় পায়ে হাঁটা অথবা গরু মোষে চড়ে যাওয়া, দুটো গতিই ছিল প্রায় সমতুল শ্লথ। ফলে ঘোড়ার দ্রুতগতিকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্যই হয়ত মানুষকে হাল্কা চাকা বানাতে হয়েছিল।
একটি কাল্পনিক দৃশ্য ভাবা যাক। আমরা জানি আফ্রিকা থেকে বের হয়ে আসা হোমো-স্যাপিয়েন্সরা ভারত অবধি আসতে সময় লেগেছিল আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর। কিন্তু যদি তারা ঘোড়সওয়ার হত তবে তারা ভারতে পৌঁছে যেত পাঁচ বৎসরেই। সেক্ষেত্র অবশ্য একটা বিশাল সমস্যা থাকত তা হল তাদের সপরিবারে আসা প্রায় অসম্ভব ছিল। এই দ্রুতগতির ঘোড়সওয়াররা পরবর্তীকালে গোটা পৃথিবীতে মানব পরিযানে শুধু গতিই আনেনি তারা আরেকটি চরিত্রগত পার্থক্য গড়ে ফেলেছিল। ঘোড়সওয়ার মানব পরিযান ঘটতে থাকে কেবল পুরুষ বা পুরুষ সমৃদ্ধ ছোট ছোট দলে। ফলে এই ছোট ছোট দলগুলো তাদের উৎস ভূমি থেকে দূর দূরান্তে দ্রুত পৌঁছে গেছে যেমন, তেমনি বাধ্য হয়েছে স্থানীয় নারীদের গ্রহণের মাধ্যমে পুরো জাতি পরিচয় বদলে ফেলতে।
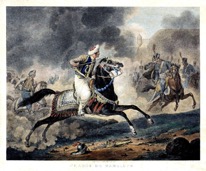
মামলুক আক্রমণ
আর এই দ্রুত গতি ঘোড়সওয়াররা অভিবাসন প্রক্রিয়াও আমূল পাল্টে দিয়েছিল। তারা আগেকার শ্লথগতিতে চলা জনগোষ্ঠীর মত পরিবেশ ও স্থানীয় মানুষদের সাথে ধীরে ধীরে মিশে যাওয়ার বদলে দ্রুততার সাথে দখল অভিযান চালাতে সমর্থ হয়।

স্পেনীয়দের মুর সেনাদের আক্রমণ
ফলে রাজনৈতিক চালচিত্রও পাল্টাতে থাকে দ্রুততার সাথে। নিরুপদ্রব রাজাদের রাজত্বগুলো আক্রমণের মুখে পড়ে দ্রুতগতি দখলদার সেনার মুখে। এই দ্রুতগতির সামনে একের পর এক প্রাচীন রাজত্বগুলোর পতন হতে থাকে। গড়ে ওঠে সাম্রাজ্য। দ্রুত দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠাও কঠিন ছিল।

স্তেপে এলাকার গৃহপালিত ঘোড়া
ঘোড়ার ব্যবহার কৃষিকাজে, যোগাযোগে, পরিবহনে, যুদ্ধে তো আছেই, কিছু মাংস আর বেশি দুধের যোগানদার হিসাবে খাদ্যের প্রয়োজনেও আছে, আছে বিনোদনেও (ঘোড়দৌড়, পোলো)। মানব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই প্রাণী। একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের জগতেও রয়েছে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে শক্তির একক হিসাবে অশ্ব-শক্তি শব্দের ব্যবহারে। একটা আনুমানিক হিসাবে এই মোটর গাড়ি মোটর বাইকের যুগেও ঘোড়া সংখ্যা প্রায় ৬কোটি আর ঘোড়া কেনা বেচা হয় বছরে ৩০০ বিলিয়ন। (ভারতের রাজনৈতিক ঘোড়ার কেনা বেচা এই হিসেবের বাইরে থাকবে স্বাভাবিক ভাবেই)।

উৎসবের সজ্জায় আরবি ঘোড়া
দ্রুতগতি সম্পন্ন কষ্টসহিষ্ণু এই প্রাণীটি মানুষের পরম আপনজন। অনেক মানুষের সাথে এই প্রাণীটির নিবিড় আবেগের সম্পর্কের অনেক কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। অনেক বীর তেমন বীর হতো না যদি না তা তার ঘোড়াটি আর দশটা সাধারণের অনেক উপরে অবস্থান না করতো। গোটা পৃথিবীতে মানব পরিযান আর যুদ্ধের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই প্রাণীটির। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘোড়া না থাকলে রথ থাকতো না। ফলে পায়ে হেঁটে কত আর কাটাকাটি হতো। হতে পারে কল্পনার সেই ঘোড়াহীন জগতে যুদ্ধটাই অনেক অনেক কম হত।
॥ঘোড়ার আদিপর্ব॥
সব জীবিত প্রাণীর মত ঘোড়ারও ফসিল নিয়ে আর জিন নিয়েও গবেষণা হয়েছে। সেই গবেষণায় আছে মাইটোকন্ড্রিয়া আর ওয়াই ক্রমোজমের বিশ্লেষণও। এখন অতি প্রাচীন দেহাবশেষের থেকে ডি.এন.এ. নিষ্কাশন করে তার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। আর তারই দৌলতে নানা তথ্য পাচ্ছি যা পাবার কথা আগে ভাবাও সম্ভব ছিল না। প্রথম ঘোড়ার বা ঐ জাতীয় প্রাণীর জিনের বিশ্লেষণের শুরু হয় একটি বিলুপ্ত প্রজাতির জেব্রার (১৮৮৩ সাল থেকে মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ছিল) টিস্যু দিয়ে। তারপরে প্রায় কাছাকাছি প্রজাতির আরেকটি জেব্রার ডি.এন.এ. পাঠ থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয় এই প্রাণীর জিন কেমন হবার কথা বা কেমন করে বিবর্তিত হতে পারে। এরপরে ডি.এন.এ. বিশ্লেষণে যোগ হল ঘোড়া, গাধা, খচ্চর। বোঝা গেল এগুলোর বিভিন্নতার মাপকাঠি। সময় লেগে গেল ১৩ বৎসর। আর প্রায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করা জনা আট বিজ্ঞানীর প্রয়াস।
অবশেষে এখন পর্যন্ত প্রাচীনতম ঘোড়ার ডি.এন.এ সংগ্রহ আর বিশ্লেষণ সম্ভব হল. যা পাওয়া গেছে কানাডার ইয়ুকন-এ বরফের তলায় চাপা পড়ে থাকা দেহাবশেষ থেকে।(ওর্লান্ডোঃ২০১৩)বয়স নির্ধারণ হয়েছে ৭.৮ লক্ষ থেকে ৫.৬ লক্ষ বৎসর।
প্রাচীনত্বের দৌড়ে এরপরে আছে ৪৩ হাজার বৎসর, ১৬ হাজার বৎসর, ৫,২০০ বৎসর, এই রকম, নানা জায়গায়। শৈত্যযুগের শেষে বা ১১,৭০০ বৎসর আগে থেকে গোটা পৃথিবী জুড়ে ঘোড়ার বিচরণের উপযুক্ত ঘাসে ভরা বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর কমতে থাকে। ফলে ঘোড়ার বিচরণ ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হতে থাকে। প্রধানত ইয়োরোপের আইবেরিয়া আর স্তেপে পন্টিয়াক-কাস্পিয়ান এলাকার বিস্তৃত প্রান্তরেই ঘোড়ার আবাসস্থল গড়ে উঠতে থাকে। ফলে এই এলাকাতেই এখনো ঘোড়ার জেনেটিক বৈচিত্র্য সর্বাধিক।
ভারতে ঘোড়ার অস্তিত্ব নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়। কারণ এর সাথে জড়িয়ে গেছে আর্য জনগোষ্ঠীর ভারতে আগমন। ফলে ভারতে এটি সাধারণ প্রাণী অনুসন্ধানের স্তর পেরিয়ে রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছে গেছে। তবে ভারতে এ পর্যন্ত সরাসরি ঘোড়ার উৎপত্তি সূচক কোন প্রত্ন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ভারতে যা পাওয়া গেছে তা হল জেব্রা জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম। যাদের সর্বশেষ অস্তিত্ব ছিল আজ থেকে ১০ হাজার বৎসর আগে। তারা হল-
১. ইকুস নামাডিকাস: জেব্রা জাতীয় ঘোড়া। জীবাশ্মের দেখা মিলেছিল ভারতের নর্মদা নদীর পাড়ে।
২. ইকুস সিভালেনসিস: এর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে ১৮৩০ সালে, শিবালিক পাহাড় এলাকায়। ছিল ২৬ লক্ষ বৎসর থেকে ১০ হাজার বৎসর আগে পর্যন্ত।
বিজ্ঞানী ফ্যালকনার ও কটলি তিন রকমের ঘোড়ার ফসিল পান ভারতে। শিবালিক এলাকার ফসিলের নাম দেন ইকুস সিভালেনসিস আর নর্মদা এলাকার দুই রকমের ফসিলের নাম দেন ইকুস নামাডিকাস ও ইকুস প্যালিওনাস। পরে বিজ্ঞানী আজ্জারোলি পরীক্ষা করে বলেন ইকুস সিভালেনসিসের ঘোড়ার বদলে জেব্রার সাথেই বেশি মিল। তারপরে আবার বিজ্ঞানী সাহনি ও খান (১৯৬১), বাদাম ও তেওয়ারী (১৯৬৬) আজ্জারোলি (১৯৭৪) বলেন বাকি দুটোও (ইকুস নামাডিকাস ও ইকুস প্যালিওনাস) নিঃসন্দেহে জেব্রা গোত্রেরই। এছাড়া হিপ্পোথেরিয়াম অ্যান্টিলোপামকে যে তিন খুর বিশিষ্ট ঘোড়ার পূর্বপুরুষ বলা হয়, জীবাশ্মবিদ অদ্বৈত জুকারের মতে সেটা একদম বাজে কথা। ওটা আসলে বেশ কয়েকটি বিভিন্ন প্রাণীর ফসিলের যোগফল মাত্র।
এখন পর্যন্ত জানা মতে ঘোড়ার পূর্বপুরুষের প্রথম বাসস্থান উত্তর আমেরিকা, তারপরে দক্ষিণ আমেরিকা। সেখানে ঘোড়ার পূর্বপুরুষেরা (ইকুইড) নানা প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়। এখন অবশ্য ইকুইড নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না। এখন ইকুইস বলে যে গণ ধরা হয় তার মধ্যেই পড়ে জেব্রা, ঘোড়া, গাধা খচ্চর। সাধারণ মতে উত্তর আমেরিকাতে ঘোড়ার বিলুপ্তি ঘটে ১১,৭০০ বৎসর আগে। একটি বিশাল উল্কার পতন হয় ১২,৯০০ বৎসর আগে। তার ফলে যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন হতে থাকে তাতে আমেরিকা থেকে অনেক বড় আকারের প্রাণীই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সম্ভবত সেই ঘটনার সাথেই ঘোড়াও বিলুপ্ত হয় আমেরিকা থেকে।তবে ১০,৫০০ বৎসর আগের আলাস্কার পাললিক স্তরে সংরক্ষিত দেহাবশেষ থেকে ডি.এন.এ. সংগ্রহ করে জানা গেছে তখন সেখানে মানুষ আর ঘোড়া দুইই বাস করত (হেইলে ও সাথীরাঃ ২০০৯)। সেই ঘোড়ার আর মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে পাললিক স্তরে। ফলে ১২,৯০০ সালের উল্কা পতনে যে আসলেই সব বিলুপ্ত হয়নি আর তারা, ঘোড়ারা ১০,৫০০ বৎসর আগেও ছিল সেটা বোঝা গেল। এরপরে ৩,৭০০ বৎসর আগেও তাদের অস্তিত্ব ঐ এলাকায় ছিল এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। তাছাড়া মাত্র ২৩০০ বৎসর আগে মানুষের সাথে তাদের সহবিচরণেরও প্রমাণ বের হয়ে আসছে। সবসহ উল্কার পতনেই তাদের বিলুপ্তি নিয়ে একটা প্রশ্ন এসে গেল। সেই উল্কা পতনে বিলুপ্তির মতবাদের বদলে এল অত্যধিক বা নির্বিচার শিকার আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে জনিত উপযুক্ত খাদ্যের অপ্রতুলতার কথা।
।।ঘোড়ার জেনেটিক দিক॥
ঘোড়ার উৎপত্তি নিয়ে কিছু আলগা সুতো রয়ে গেল। তা থাকুক। প্রাচীন জিন গবেষণা তো সবে শুরু হয়েছে। জানা গেছে ঘোড়ার জিনে আছে ২৭০কোটি বেস পেয়ার। কুকুরের চেয়ে বেশি কিন্তু গবাদি পশু বা মানুষের চেয়ে কমই। প্রথমবারে ২০০৬ সালে ঘোড়ার জেনেটিক তথ্য বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। আর সম্পূর্ণ জেনোম ম্যাপিং করা হয় ২০০৯ সালে। কাজ অনেকটা হয়েছে ঠিকই কিন্তু অনেক তথ্য এখনো জোগাড় করাও বাকি।
তবে আধুনিক গৃহপালিত ঘোড়ার খবর কিন্তু অনেকটাই হাল আমলের। ইউরেশিয়ান স্তেপের বোটাই (বর্তমানের কাজাকিস্তানের) (আউট্রাম: ২০০৩) প্রত্নক্ষেত্রে গৃহপালিত ঘোড়ার প্রাচীনতম দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, যার বয়স ৫.৫ হাজার বৎসর। এই আধুনিক গৃহপালিত ঘোড়ার উৎপত্তি আর বিস্তারের বিশদ তথ্য জানতে গিয়ে এক অদ্ভুত সমস্যার দেখা পাওয়া গেল। দেখা গেল আধুনিক সব ঘোড়ার পিতৃধারা (ওয়াই-ক্রমোজম) হাতেগোনা সামান্য কয়েকটি পুরুষ ঘোড়ার। যাদের অস্তিত্বের শুরু মাত্র ২০০ বৎসর আগে।
ব্যাতিক্রমী পিতৃধারা হিসাবে পাওয়া গেছে ২৮০০ বৎসর আগের সিথিয়ানদের আমলের দেহাবশেষে আর বর্তমানের ইয়াকুটিয়ান(রাশিয়ার শক রিপাবলিক) ঘোড়ার মধ্যে। ইয়াকুটিন ঘোড়ার এই টিকে থাকা আর ভিন্নতার কারণ হিসাবে অনুমান করা হয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়া থেকে শকদের দেশে আসা জনগোষ্ঠীর সাথে এই ব্যতিক্রমী পিতৃধারা আসে। আর যেহেতু এই এলাকা মোটামুটি ভাবে বাকি দুনিয়ার থেকে খানিক বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল তাই সেই ব্যতিক্রম টিকে যায়। পিতৃধারার বৈচিত্র ছোট হলেও মাতৃধারার (মাইটকন্ড্রিয়া)বৈচিত্র্য কিন্তু বিশাল। আধুনিক ঘোড়ার মাতৃধারার আরম্ভ ৯৩ হাজার থেকে ১৬০ হাজার বৎসর আগে। এখন অবধি জানা গেছে কম করেও ১৭-৪৬টি ভিন্ন মাতৃধারা ছড়িয়ে আছে গোটা দুনিয়ায়। মাতৃধারার বিশাল বৈচিত্র্যের সাথে পিতৃধারার অতি সীমাবদ্ধতা খুবই অবাক করার মত। যদিও পুরুষ ঘোড়া অতিমাত্রায় বহুগামী তবু প্রকৃতিতে এতটা বৈপরীত্য হবার কথা নয়। তবু এই ঘটনা দেখা গেল ঘোড়ার বেলা। দেখা গেল কারণ এই সমস্যার জন্মদাতা ছিল মানুষ।
গোটা পৃথিবীতে এখন ঘোড়া মানেই গৃহপালিত ঘোড়া। কিন্তু গোড়াতে সব পশুর মতো ঘোড়াও তো বন্য ছিল। সেই বন্য ঘোড়ারা কোথায় গেল? ঘটনা হল অতি নিয়ন্ত্রিত ঘোড়া প্রজননের ফলে তারা বিলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত। মোট জানা ৯০৫টি ঘোড়ার প্রজাতির মধ্যে ৮৭টি ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
ক্রমাগত সুনিয়ন্ত্রিত প্রজননের ফলে একসময় ঘোড়ার জিন বৈচিত্র্য কমতে থাকে। যা সম্ভাব্য বিপদের সূচক। বন্য ঘোড়াদের মধ্যে তথ্য জানা আছে এমন প্রথম ঘোড়া বিলুপ্ত হয় পূর্ব ইউরেপের তার্পান ঘোড়া ১৯০৯-এ। তখন থেকে সতর্কতা শুরু হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ৮৭ রকমের ঘোড়ার প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আগে যেটুকু জিন বৈচিত্র্য ছিল সেটাও অতিদ্রুত লোপ পাচ্ছে। বিশেষ করে ২০০ বৎসর আগে থেকে এটা ঘটছে অতি দ্রুত হারে। ফলাফল কি হবে তা নিয়ে গবেষণা চলছে। বড় সমস্যা থাকছে জেনেটিক বৈচিত্র্যের অভাবে বংশানুক্রমিক রোগ বাড়তে থাকার।

স্বেলাস্কিস ঘোড়া।
স্তেপের এশিয় অংশে ছিল স্বেলাস্কিস হর্স। এটি মঙ্গোলিয়া এলাকার বন্য ঘোড়া। যখন একে আলাদা করে চিনে নিয়ে খোঁজ খবর শুরু হল তখন বেঁচে ছিল মাত্র ১২ থেকে ১৬টি। রাশিয়ান সেনাবাহিনীর কর্নেল স্বেলাস্কি (জাতিতে পোল্যান্ডের লোক) প্রথম এর খোঁজ পেয়ে এর সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন। তাঁর নামেই এই জাতের ঘোড়ার নামাকরণ হয়। ক্রমে চীন আর মঙ্গোলিয়ার মিলিত প্রয়াসে এখন বিলুপ্ত প্রায় সংজ্ঞা থেকে স্বেলাস্কিস হর্সের পদোন্নতি হয়েছে বিপন্ন প্রজাতিতে। সংখ্যা বেড়ে এখন দুই হাজারের বেশি। ১২ থেকে দুই হাজার, ভালো বলতেই হবে।
মঙ্গোলিয়ার বন্যঘোড়া স্বেলাস্কিস হর্সকে এনে বর্তমানের গৃহপালিত ঘোড়ার জেনেটিক বৈচিত্র্য বাড়ানোর চেষ্টা প্রেক্ষিতে এই জাতের ঘোড়ার ইতিহাস দেখা যেতে পারে। মঙ্গোলিয়ার বন্য ঘোড়া স্বেলাস্কিস হর্স আর গৃহপালিত ঘোড়ার মধ্যে ক্রোমোজমের ফারাক আছে। গৃহপালিত ঘোড়ার ক্রমোজমের চেয়ে স্বেলাস্কিস ঘোড়ার দুজোড়া বাড়তি ক্রমোজম রয়েছে। এই দুটো বাড়তি ক্রমোজম জোড়ের জন্য এদের চেনা সহজ। দেখা গেছে স্বেলাস্কিস ঘোড়া তাদের মুল সাধারণ উৎস থেকে আলাদা হবার পরে আবার মিলিত হয় ৪৫ হাজার বৎসর আগে। তারপরেও মাঝখানে সময়ের ফাঁক রেখে কয়েকবারে এরা মিলিত হয়েছে। সেই রকম শেষতম মিলনের প্রমাণ পাওয়া গেছে যার বয়স ৫২০০ বৎসর আগের। প্রায় সেই সময়ের যখন ঘোড়াকে পোষ মানানো শুরু হয়।
এই থেকেই অনুমান করা হয় যে এখনকার মতই আদিম কালেও, মানুষ ঘোড়া পোষার শুরু থেকেই, মেয়ে ঘোড়া বেশি পুষতো। কারণ দুধ আর বাচ্চা পাওয়া যাবে। (মাংস খেত তবে তুলনায় কম, গৃহপালিত পশুর মাংস খাওয়া একটু সীমিতই হয় সহজাত মানবিক আচরণের প্রেক্ষিতে)। তার সাথে নিজেদের পশুর সংখ্যা বাড়াবার জন্য বুনো মেয়ে-ঘোড়াও ধরে আনত প্রায়ই। ফলে মাইটোকন্ড্রিয়ার বৈচিত্র্য বাড়তে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু ওয়াই-ক্রমোজমের বেলা তেমনটা ঘটেনি। প্রজননের জন্য তারা ধরে আনত বা পুষে রাখত গোনাগুনতি পছন্দের দুই একটি পুরুষ ঘোড়াকে। এই করেই গোটা ব্যাপারটা একপেশে হয়ে যায়।
ঘোড়ার মাইটোকন্ড্রিয়া জেনোম থেকে কি আমরা জানতে পারি ঘোড়ার বিভিন্ন জাতি আর পরিযানের কথা? যেমন করে জানতে পারি মানব পরিযানের কথা। তাহলে ভারতের ঘোড়ার মাথা তর্কের অবসান হয়ে যেত।
ঘোড়ার মাইটোকন্ড্রিয়া ধরে তার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে এখন পর্যন্ত তা ব্যর্থই বলা যায়। শৈত্যযুগের শেষ থেকে তাম্রযুগ অবধি ঘোড়ার বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সুবিশাল এলাকা জুড়ে। তাদের দ্রুত গতির জন্যই হয়ত তাদের বিশেষ ভূমিখণ্ডের সীমানার মধ্যে আলাদা আলাদা হয়ে আটকে থাকতে বাধ্য হতে হয় নি। ফলে ঘোড়ার মধ্যে ভুখণ্ডিয় মাতৃধারার বৈশিষ্ট্য খুব একটা সুনিশ্চিত অবস্থায় থাকেনি, যেটুকু পাওয়া গেছে তা ছিল অতি ক্ষীণ। তার থেকে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ততে আসা যায় না। তবু যেটুকু থাকার সম্ভাবনা ছিল তা ব্রোঞ্জ যুগের থেকে মানুষের ঘোড়া পালনের আগ্রাসী ভূমিকা সেটুকুকেও ক্ষীণতর করে দিয়েছে। ফলে এখন আর তাকে আলাদা করে চেনার খুব একটা সুযোগ নেই হয়ত।
তারই মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া নিউক্লিয়ার তথ্যে যা দেখা গেছে, ৩২২ টি গৃহপালিত নয় এমন ঘোড়ার থেকে নেওয়া তথ্যে, তা হল মূলত আইবেরিয়া আর পশ্চিম-ইয়োরোপীয় স্তেপে এলাকাতেই বৈচিত্র্য সর্বাধিক। ফলে ঐ দুটি এলাকাকেই আধুনিক ঘোড়ার উৎস বলে ধরে ভাবা শুরু করা যেতে পারে, আপাতত। এর মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া ডি১ পাওয়া গেছে আইবেরিয়াতে আর উত্তর আফ্রিকার বার্ব ঘোড়ার মধ্যে। মুশকিল দাঁড়ালো যে আইবেরিয়াতেই আরো ২২টি ভিন্ন ঘোড়ার মাইটোকন্ড্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা গেছে এদের মাইটোকন্ড্রিয়া ডি১ নিয়ে আইবেরিয়াতে আগমন মধ্যযুগের পরে। কাজেই আইবেরিয়াকে ডি১ এর উৎসভূমি বলতে ঢোঁক গিলতেই হয়। তা বাদেও ইয়োরেশিান স্তেপের ঘোড়াদের রঙের বাহারও আবার আইবেরীয় ঘোড়ার নেই। বোঝা গেল রঙের বৈচিত্র্যে পূর্ব-ইউরেশিয়ার স্তেপে এলাকার ঘোড়া আইবেরিয়ার চেয়ে প্রাচীন।
এদিকে আবার পর্তুগালের ঘোড়ার মাইটোকন্ড্রিয়া-সি সংখ্যায় বেশ কম তারা কিন্তু আছে একেবারে ব্রোঞ্জযুগেরও আগে থেকে। ফলে সব মিলিয়ে আইবেরীয়ার ছবি ঝাপসা।
তাহলে উত্তর আফ্রিকার বার্ব ঘোড়া প্রাচীনতম? না সেখানকার ছবিও ঝাপসা। বার্ব ঘোড়ার আদত উৎস এখনো কিছুটা অজানা, অনুমান করা হয় এগুলো সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে আরব থেকে আনা ঘোড়ার বংশধর।
॥ঘোড়ার ও গৃহপালিত ঘোড়ার নিয়ন্ত্রিত প্রজনন।॥

আরবীয় ঘোড়া
ঘোড়া ঠিক কবে থেকে গৃহপালিত হল সেটা কিন্তু সঠিক বলা কঠিন। চার হাজার বৎসর আগে থেকেই ঘোড়াকে রথ টানার কাজে লাগানো হয়েছিল সেটা জানা গেছে। জানা গেছে মোটামুটি ভাবে সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর আগে ঘোড়াকে বাড়ীতে পোষা হত। ইয়োরেশিয়ান স্তেপের প্রাচীন প্রত্নক্ষেত্র বোটাই সংস্কৃতি (আকমোলা প্রদেশ, কাজাখস্তান)তে ঘোড়া পালনের সরাসরি প্রমাণ পাওয়াতে সেটাই এখনো জানা মতে ঘোড়ার গৃহপালিত পশু হবার প্রাচীনতম সময় বলে মানা হয়।
যখন থেকে মানুষ ঘোড়া পুষেছে, বিশেষ করে পুষে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে,তখন থেকেই ঘোড়ার ক্রেতারা চেয়েছে বিশেষ প্রয়োজনের আর পছন্দের ঘোড়া পালকরাও ক্রেতার পছন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছে, বা দিতে বাধ্য হয়েছে। আর সেই চাহিদানুযায়ী প্রজনন ঘটিয়েছে।। তার কারণ ছিল এই প্রাণীটির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকা বংশগতি ভিত্তিক বিভিন্নতা। কোন একটি ঘোড়ার মধ্যে চাহিদা মত সব বৈশিষ্ট্য না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন বংশগতির ঘোড়ার ব্যবহার ও ব্যবহারগত চাহিদার বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। ফলে পছন্দসই ঘোড়ার জন্ম দিতে দিতে বিবর্তনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কয়েকটি বিশেষ ধরনের ঘোড়ারই জন্ম হয়ে এসেছে এতকাল। তবে বিবর্তনকে শেষ পর্যন্ত কতটা বুড়ো আঙ্গুল দেখানো সম্ভব বা উচিত সেটা সন্দেহের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আধুনিককালের ঘোড়া নিয়ে গবেষণায় অগ্রণী পাবলো লিব্রাডো গবেষণা করেছেন আধুনিক ঘোড়াদের মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হারে প্রোটিনের মিউটেশন নিয়ে। কিন্তু সে আলোচনা ঘোড়ার ভবিষ্যতের আলোচনা, এখানে দরকার হবে না।
পশুপালকরা তাদের গ্রাহকের চাহিদা মত ঘোড়া জোগান দেবার জন্য নিয়ন্ত্রিত প্রজননের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দরকার তাদের বিশেষ অজ্ঞতা। ঘোড়ার কোন কোন বংশগত বৈশিষ্ট্য তার জন্মদাতার উপর নির্ভর করবে সেটা পশুপালকরা অভিজ্ঞতার জোরেই জেনে গেছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঘোড়ার চলন, রঙ, কষ্ট সহিষ্ণুতা, চারিত্রিক স্থিরতা-দৃঢ়তা। এবার গ্রাহকের চাহিদা আর ঘোড়া পালনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ন্ত্রিত জন্মের কাজে নেমে পড়ল আস্তাবলের মালিকরা।
ঘোড়ার নানা বৈশিষ্ট্য প্রজনন নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও একই পশুপালকের পক্ষে অত বিভিন্নতার খেই রাখা খুব কঠিন, বা সব সময়ে উপযুক্ত গুণাবলীর পুরুষ ও মেয়ে ঘোড়াও হয়ত তার কাছে থাকে না। তাই এই পশুপালন ক্রমে কিছুটা হলেও ভৌগোলিক বিশেষত অর্জন করে। আসলে সেই অর্থে ঘোড়ার ভৌগোলিকত্ব এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হবে ঘোড়ার প্রজনন কেন্দ্রের ভৌগোলিক অবস্থান। বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকার পশুপালকরা ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ধরনের ঘোড়ার জন্ম দিতে বিশারদ হয়ে ওঠে, স্থানীয় চাহিদার অনুসারে।
আসিরীয় যোদ্ধাদের অপ্রতিহত রণদক্ষতার মুলে ছিল একটি বিশেষ ব্যবস্থা। আসিরীয় সম্রাটরা আলাদা অশ্ব প্রজননকারী, সরবরাহকারী ঠিক করে রেখেছিল।তাদের দায়িত্ব ছিল প্রতি তিনমাস অন্তর তাদের সরবরাহ করা যুদ্ধের ঘোড়া পাল্টাতে হবে। সেনাবাহিনী যেখানেই থাকুক। ফলে ঐ এলাকায় যুদ্ধের উপযুক্ত ঘোড়ার প্রজনন অগ্রাধিকার পেতে থাকে।
এই ঘোড়া পালনের স্থানীয় সংস্কৃতি ভিত্তিক বিভিন্নতা যা মানুষের আসলে প্রয়োজন ভিত্তিক সৃষ্টি, যা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। ফলে ঘোড়ার জাতি বা উৎস নির্ধারণের পক্ষে এটা এক বড় বাধা,বা এমন একটা গোলকধাঁধা তৈরি করেছে যে অনেক বিজ্ঞানীরই মত যে, আমরা কোনদিনই পুরো তথ্য সাজাতে পাবো না। সম্ভবই না।
॥ঘোড়ার চলন ও চাহিদা॥

তুর্কমেনিস্তানের আকেল-টেকে ঘোড়া
গৃহপালিত ঘোড়ার প্রজনন নিয়ন্ত্রণে ঘোড়ার দুটো ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যই আসলে প্রজননকেও নিয়ন্ত্রণে করছে। এই দুটো বৈশিষ্ট্যই ঘোড়া বাছাই করার কাজে মানুষের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে বরাবর। তার মধ্যে একটি হল তার গতিবেগ অপরটি তার সৌন্দর্য। এদের মধ্যে অবশ্যই ঘোড়ার গতিবেগ শুধু নয়, তার গোটা চলনটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বৈশিষ্ট্য ভেদে যে ঘোড়া জোরে দৌড়ায় সে ঘোড়া দীর্ঘকাল ভারী ওজন বইতে পারে না ভালোভাবে। আবার দৌড়ের মধ্যেও ফারাক আছে। কিছু ঘোড়া দুলকি চালে বেশি কর্মক্ষম। কিছিু ঘোড়া আবার প্রথম থেকেই তীব্রবেগে ছুটতে পারে। আবার কিছু ঘোড়া প্রথমেই জোরে শুরু করলেও খানিক পরে তীব্র গতিবেগে ছুটতে পারে।এই বৈশিষ্ট্যগুলো ঘোড়ার বংশগত বৈশিষ্ট্য। অনেক ঘোড়া দৌড় শুরু করেই দুলকি চালের চেয়ে বেশি দ্রুত ছুটতে পারে, অথচ পূর্ণ গতিতে যায় না। এই গুন কাজে লাগে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের মাঝপথে মাঝারি গতি থেকে অন্তে এসে অতিদ্রুত বেগে ছোটার কাজে। ঘোড়ার চলনের এই গুনটি আসে একটি বিশেষ জেনেটিক মিউটেশন থেকে।আর এই জন্যই ঘোড়ার বংশগতি দেখে তার মেজাজ মর্জি আর দৌড়ের গতিবেগ বুঝে বাজী ধরার জন্য ঘোড় দৌড়ের মাঠে ঘোড়ার কুলজি পাঠ। সেই কুলজী পাঠের কথা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। যার থেকে এসেছে প্রবাদ বাক্য ঘোড়ার মুখের খবর।
ঘোড়ার গতিবেগ বাড়ায় মায়োস্ট্যাটিনজিন। তবে এর মধ্যেটি-অ্যালেলেকাজ করে ঘোড়ার সমান বেগে বেশিদূর দৌড়োবার ক্ষমতার জন্য আর সি-অ্যালেলে সাহায্য করে ঘোড়ার অল্প সময়ের জন্য অসম্ভব দ্রুত দৌড়ের ক্ষমতা পেতে। লক্ষণীয় আরবি অ্যালেলে ঘোড়াটি বেশি কর্মক্ষম।
স্বাভাবিক কারণেই চাষের কাজে বা মাল পরিবহনের ঘোড়ার তীব্র গতিবেগ দরকার নেই। চাষের জন্য সাধারণ হাঁটাই যথেষ্ট। মাল ও যাত্রী পরিবহনের জন্যও তীব্রগতি দরকার নেই, দরকার দুলকি চাল। যুদ্ধে, যোগাযোগে, কখনো সখনো তীব্র গতিবেগ দরকার হলেও সাধারণ ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাদের ততটা তীব্র গতিবেগ দরকার হয় না। এই প্রয়োজনভিত্তিক গতিবেগের বিভিন্ন তাই, বিভিন্ন ধরনের ঘোড়ার চাহিদার বিভিন্নতা তৈরি করে দিয়েছে। আর সেই চাহিদার বিভিন্নতা অনুপাতেই পশুপালকরা প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারই ফলে অতি সামান্য কয়েকটি পুরুষ ঘোড়ার বংশের ব্যবহার হয়ে এসেছে শুরু থেকেই।
ঘোড়ার পা লম্বা হলে ঘোড়া জোরে ছুটতে পারবে, এমন সরল অঙ্ক কাজে লাগবে না। দেখা গেছে পা লম্বা হলে ঘোড়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় একটা গর্জনের মত আওয়াজ বের হয়। এর কারণ সেই সময় তার হৃদপিণ্ড অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য ক্ষমতার চেয়ে বেশি বাতাস টানার চেষ্টা থেকে। সাময়িক ভাবে কাজে লাগলেও দীর্ঘকালীন হিসাবে এটা ঘোড়ার পক্ষে ক্ষতিকর।
॥ঘোড়ার রঙ ও চাহিদা॥
ঘোড়ার প্রজনন নিয়ন্ত্রণ কেবল তার গতিবেগের তারতম্যের ভিত্তিতে চাহিদার বিভিন্নতা কাজ করে না। আরেকটি জিনিষও অনেকটাই চাহিদার বিভিন্নতার সৃষ্টি করে। আর তা হল গোড়ার গায়ের রঙ। এখানে বিচিত্র তথ্য হল মানুষের মতই গোড়াতে সব ঘোড়ারও গায়ের রঙ একরকম ছিল, হাল্কা বাদামী। এই হালকা বাদামী রঙ পরে বদলাতে শুরু করে। আসে কালো রঙ। আর দেখা দেয় রঙের ছিটে বা ছোপ সারা গায়ে। আরো মজার কথা হল মানুষের মত ঘোড়ারও একটি জিনই এই কাজের কাজি। মেলানোকর্টিন রিসেপ্টর ওয়ান-এ একটু মিউটেশন, ব্যস মানুষ বা ঘোড়া গায়ের রঙ বদলে যাবে। এই মিউটেশন কালো পিগমেন্টের পথ বন্ধ করে দেয় ফলে গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যাকে আমরা ফর্সা বলি। আর মানুষের মাথার চুলকে লাল করে দেয় অনেক সময়েই, কারণ কালো আটকে লাল রঙকে প্রাধান্য দেয় মিউটেশন। এই লাল রঙের দরুনই ঘোড়ার হাল্কা বাদামী রঙ লালচে বাদামী দেখায়। পরে নিয়ন্ত্রিত প্রজননে এই বিশেষ রঙের ঘোড়ার বেশি জন্ম নেওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়, কারণ ক্রেতা চাহিদা। ঘোড়ার বেলা ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী, মানুষের বেলা সমাজের চাহিদা অনুযায়ী রঙ বদলের খেলা।মানুষের ত্বকের রঙ আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে পরিবর্তিত হয় বটে তবে তারপরে পছন্দসই প্রজনন সেটাকে প্রাধান্য দেয়। যেমন ভারতীয়রা সবাই ফর্সা জনকে বিয়ে করতে চায়, না হলে ছেলে মেয়ে কালো হবে যে। এটাও আসলে নিয়ন্ত্রিত প্রজনন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।
তবে বিজ্ঞানীদের মতে এই কালো বন্ধ করে লাল রঙের প্রাধান্য মানুষের বেলা ব্যথার অনুভূতি বেশি তীব্র করবে, বা ব্যথায় তারা বেশি কাতর হবে। অর্থাৎ ফর্সা লোকের ব্যথার অনুভূতি বেশি হবার সম্ভাবনা বেশি। আর ঘোড়ার বেলা লালচে বাদামি (চেস্টনাট) ঘোড়া আবহাওয়া পরিবর্তনে বেশি মেজাজ পরিবর্তন করবে। ঘোড়ার রঙে আরেকটি ব্যাপার আছে যা মানুষের নেই, তা হল শরীরের এক এক জায়গায় এক এক রঙ। ঘোড়ার এটা হয়। এর জন্য দায়ী আগৌতি সিগনালিং প্রোটিন মিউটেশন। এই জিনের মিউটেশনের ফলে প্রধানত ঘোড়ার গায়ে কালো রঙ দেখা দেবে। তবে সেটা একটা বিশেষ অঙ্গে বা অংশে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটিও প্রজনন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং হয়ও।
ঘোড়ার গায়ে হাল্কা রঙ কিন্তু ঘাড়ের কেশর গাঢ় রঙ পায়ের খুরের কাছে গাড় রঙ আর পিঠ থেকে পেছনে টানা গাড় রঙের ছোপ এমন ঘোড়ার প্রথম অস্তিত্ব ছিল ৪৩ হাজার বৎসর আগে মধ্য সাইবেরিয়াতে।
মহাভারতের মাধবী ও গালবের কাহিনীতে বিশ্বামিত্রের চাহিদা ছিল একটি কান কালো এমন এক হাজার ঘোড়া। অনেক চেষ্টাতেও চার চারজন তখনকার সবচেয়ে প্রতাপশালী রাজা মিলেও এই এক হাজার এক কান কালো ঘোড়া জোগাড় হয়নি। এবং বলেই দেওয়া হল, দেশে কোথাও নেই। মহাভারতের এই কাহিনীতে অন্তত একটি কথা পরিষ্কার যে ঐ বিশেষ রঙের বৈশিষ্ট্য থাকা ঘোড়া বড়ই দুর্মূল্য আর দুর্লভও ছিল। তার সাথে জানা হয়ে গেল যে এই কাহিনীটি ঘোড়ার সুনিয়ন্ত্রিত অতি দক্ষ প্রজনন প্রথা চালু হবার পরের ঘটনা।
ঘোড়ার গায়ের রঙের বৈচিত্র্য নব্য প্রস্তর যুগের আর প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা চিত্রেও (নানা গুহা চিত্র সহ) বোঝা যায়। চিরন্তন হালকা বাদামী বাদে লালচে বাদামী বা চিতার মত ফোঁটা ফোঁটা রঙের ঘোড়া বন্য অবস্থাতেই আলাদা আলাদা করে সংখ্যায় বাড়ছিল। যদিও চিতা ছোপের ঘোড়ার একটা সমস্যা ছিল যে এর এই ছোপের জন্য দায়ী এল.পি অ্যালেলে আবার ঘোড়ার রাতকানা রোগেরও কারণ ছিল। তবু কিন্তু চিতা ছাপ ঘোড়ারাও সংখ্যায় বাড়ছিল।
এই এল. পি. অ্যালেলে তুরস্কের কিরক্লারেলি-কানলিগ্লেসিট প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া দশটি ঘোড়ার কঙ্কালের মধ্যে ছটিরই ছিল (৪২০০-৪৭০০ বৎসর আগে)। কিন্তু লৌহযুগে ক্রমে এটা কমে এসেছিল। এই রোগ আবার দেখা গেছে পশ্চিম সাইবেরিয়ার চিচা-প্রত্নক্ষেত্রে (৩৩০০-৩৪০০ বৎসর আগে)। এতে বোঝা যায় কোন না কোন কারণে ব্রোঞ্জ যুগের শুরুতে এই রোগ থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘোড়াই লোকদের পছন্দের ছিল। কিন্তু ব্রোঞ্জযুগের অন্তে এই পছন্দ বদলে যাওয়াতে এই রোগে রুগী ঘোড়াও কমতে থাকে।
এই ঘটনার উল্লেখ খুব দরকার। কারণ এখানেই দেখতে পাই কি করে মানুষ প্রাকৃতিক বিবর্তনকে নির্বাচিত নিয়ন্ত্রণে বদলে দিতে পারে।
॥কিছু বিশেষ ঘোড়ার কথা॥
॥আরবের ঘোড়া॥

আরবের ঘোড়া তার নানা গুনাবলীর জন্য বিশ্বখ্যাত। এই ঘোড়ার চাহিদা গোটা বিশ্বে সর্বোচ্চ।আরবে এর প্রাচীনতম অস্তিত্ব জানা গেছে ৪২০০ বৎসর আগের। অনেকে ধারনা করেন এই ঘোড়া আরবে আসে আনাতোলিয়ার দিক থেকে। তবে এর সপক্ষে জোরালো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাব আছে। এই ঘোড়া আরবেই উদ্ভূত না অন্য জায়গা থেকে এসেছে সেটা একেবারে সঠিক বলা কঠিন। আকারে অনেক বড়, উচ্চতায়ও বড় এই ঘোড়ার গুণপনার মুল বাহাদুরি কিন্তু এই ঘোড়ার পালকদের। পালকদের নিয়ন্ত্রিত প্রজননের সময়ে তাদের ঘোড়ার বংশাবলী ধরে ধরে, গুণপনার নিখুঁত খবর রেখে, নতুন ঘোড়ার জন্মের জন্য জুটি বানানোই আদত কৌশল। এই কৌশলই দিয়েছে আরবী ঘোড়ার বিশ্বজোড়া নামডাক। বর্তমানে আমেরিকা, আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া সব জায়গায় মূলত এই আরবি ঘোড়ার বংশধরেরাই রাজত্ব করছে।
॥ইরানের ঘোড়া॥

উত্তর-ইরানের ঘোড়া আরবের ঘোড়ার চেয়ে প্রাচীন। যে দেহাবশেষ পাওয়া গেছে তার বয়স ৫৪০০ বৎসর। সাইবেরিয়ার বোটাই সংস্কৃতির গৃহপালিত ঘোড়ার সমসাময়িক হলেও ইরানে কিন্তু তখনো এই ঘোড়া বুনো ঘোড়া। আকারে খানিকটা ছোট এই ঘোড়াকে ক্যাসপিয়ান ঘোড়া বা খাযার ঘোড়াও বলা হয়। ঘোড়ার পূর্ব পুরুষ বলে যে চারটি জাতের ঘোড়ার পরিচিতি আছে (উত্তর-ইয়োরোপীয়, উত্তর-স্তেপীয়, দক্ষিণ স্তেপীয়, আর আইবেরীয় তার মধ্যে ইরানের এই ঘোড়াকে ধরা হয় না। এই ক্যাসপিয়ান ঘোড়া মোটামুটি ভাবে মঙ্গোলিয়ার স্বেলাস্কিস আর তুর্কমেনিস্তানের আখাল টেকে ঘোড়ার সমগোত্রের দুর্লভ জাতের ঘোড়া।
উত্তর ইরানের ঘোড়া তার গতিবেগের জন্যই বেশি বিখ্যাত। উত্তর-ইরানের পার্বত্য এলাকায় জন্ম হওয়া এই ঘোড়া খুব কষ্ট সহিষ্ণু আর শক্তিশালী।উত্তর ইরানের মাজান্দারানের গোহার টেপে এলাকায়, ২০১১ সালে ৫২০০ বৎসর আগের একটি কবরে এই ঘোড়ার দেহাবশেষ পাওয়া যায়। সেখানে কয়েকটি আঁকা ছবিও পাওয়া যায়। যে ছবিগুলোতে দেখা যাবে ঘোড়া রথ টানছে। এই ঘোড়া ব্যবহার করেই পারসিক সম্রাটরা তাদের সাম্রাজ্যে দ্রুততম ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা চালু করেছিল। শীত গ্রীষ্ম ঝড় তুফান রোদ অন্ধকার যাই হোক না কেন এই ডাক ব্যবস্থা সময়ের ব্যাপারে থাকতো নিখুঁত থাকতো এই ক্যাসপিয়ান ঘোড়ার দৌলতেই। অথচ পারসিক সাম্রাজ্যের পতনের পরে থেকে এই ছোট আকারের দ্রুতগতির ঘোড়ার অস্তিত্ব প্রায় মুছে যেতে থাকে। আবার নজরে আসে ৭০০ সাধারণাব্দে। অর্থাৎ মাঝে প্রায় হাজার বৎসর এই ঘোড়ার কথা সবাই ভুলেই গিয়েছিল।কিন্তু তারপরেও উন্নততর আরবি ঘোড়ার দাপটে এই ঘোড়া হারিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছিলেন এই ক্যাপসিয়ান ঘোড়া বিলুপ্ত। কিন্তু ১৯৬৫ সালে আরেকবার দেখা মেলে নতুন করে।
॥তুর্কমেনিস্তানের আকেল-টেকে ঘোড়া॥

এই ঘোড়ার নামডাক তার সহনশীলতা আর গতির জন্য। তবে বেশি বিখ্যাত তার গায়ের উজ্জ্বল রঙের জন্য। তার মসৃণ উজ্জ্বল বাদামী রঙের জন্য তার নামই হয়ে যায় সোনালী ঘোড়া।
এই ঘোড়ার পূর্বপুরুষের সঠিক কোন খোঁজ নেই। যদিও এই ঘোড়া আজ থেকে তিন হাজার বৎসর আগেও ছিল, তবু গত দেড় হাজার বৎসর আগে থেকে মাত্র ঘোড়ার পালকরা ঘোড়াগুলোর পূর্বপুরুষের নাম উল্লেখের প্রথা চালু করেছে।
এই আকেল-টেকে বা সোনালী ঘোড়ার লালন পালনের একটা অদ্ভুত রীতি আছে। বাচ্চার জন্মের আগে হবু মা-ঘোড়াকে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘোড়ার বাচ্চা বনে জন্মানোর পরেও বাচ্চা বড় হতে থাকে বন্য পরিবেশেই। পালকদের ধারনা এতে বাচ্চা ঘোড়ারা অনেক বেশি চতুর, বলশালী আর তরতাজা হয়। এমনটা ভাবার কারণ, এই গুনগুলো না থাকলে তারা বন্য পরিবেশে বাঁচতেই পারতো না। বাচ্চা খানিক বড় হলে আবার বন থেকে ধরে আনা হয়। তারপরে মাত্র আটমাস বয়সেই লাগাম পরানো হয়। সম্ভবত এই প্রথার দরুনই এদের বংশগতি যথাযথ রাখা সম্ভব ছিল না। বন থেকে ধরে আনার পরে প্রথমে পিঠে সওয়ার হয় হাল্কা ওজনের কিশোর। তারপরে শেখানো হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। ঘোড় দৌড়ে জেতার জন্য শরীরের পেশী শক্তি দ্রুত বৃদ্ধির জন্য এদের খাবারও খানিক আলাদা হয়। এদের খেতে দেওয়া হয় বার্লি, খেজুর, কিসমিস, আলফা আলফা, মুরগীর মাংস আর পাঁঠার চর্বি।
ঘোড়ার মাংস খাবার তথ্য আমার কাছে খুবই অবাক লেগেছে। আমার ব্যক্তিগত ধারনা এই ঘোড়াগুলোকে ঘোড়দৌড়ে লাগানোর হবে বলেই তাদের পেশী শক্তি বাড়ানোর জন্য হাই-প্রোটিন ডায়েট হিসাবে মুরগীর মাংসের ডাস্ট অন্য খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হত। কারণ কোন তৃণভোজী ঘোড়া মাংস খেতে পারবে না বলেই আমার ধারনা।
॥তারপান ঘোড়া। (বিলুপ্ত)॥

তারপান বা তারপানি শব্দটি তুর্কী শব্দ যার অর্থ হল বুনো ঘোড়া। এই ঘোড়া আসলেই বুনো ঘোড়া অথবা স্বেলাস্কিস ঘোড়ার সাথে গৃহপালিত ঘোড়ার মিলনে এদের উদ্ভব হয়েছিল তা নিয়ে মত বিরোধ আছে। কারণ প্লেইস্টোসিন যুগের কোন তারপান ঘোড়ার ফসিল পাওয়া যায় নি।
রাশিয়ান সাইবেরিয়া অঞ্চলের এই ঘোড়া রাশিয়ান সম্রাটদের কাছে ছিল। শেষ ঘোড়াটি মারা যায় ১৯০৯ সালে। এরপরে১৯৩০ থেকে তারপান ঘোড়ার মত দেখতে কিছু ঘোড়ার প্রজনন করে তাকেই তারপান ঘোড়া বলে বিক্রি করা হচ্ছে। তারপান ঘোড়ার যে টুকু তথ্য পাওয়া গেছে তাতে বলা হয় এই ঘোড়ার উচ্চতা ১৪০০ থেকে ১৪৫০ মিলিমিটার উচ্চতা। ঘাড়ে খাড়া ঘন কেশ। গায়ের রঙ ইঁদুরের মত, একটু নীলের আভাস সহ। পায়ের রঙ গাঢ়, কালোর কাছাকাছি, মেরুদণ্ড বরাবর টানা গাড় রঙের দাগ, সেই দাগ কখনো কখনো কাঁধের কাছেও থাকে।
॥মারোয়াড়ি ঘোড়া॥

রাজস্থানের মারওয়ার (যোধপুর) এলাকার ঘোড়া। এ ঘোড়ার অতীত উৎস জানা নেই। অতীত উৎস বলতে স্থানীয় ঘোড়া ব্যবসায়ীরা বলেন সেই যখন ঘোড়ার ডানা ছিল তখন থেকেই এই ঘোড়া আছে। এই ঘোড়ার সাথে গুজরাতের কাথিওয়ার এলাকার ঘোড়ার কিছু জেনেটিক নৈকট্য আছে। এই ঘোড়ার ক্রমোজম স্বেলাস্কিস ঘোড়ার মতই দুটি বাড়তি।জানা গেছে মাঝে এই ঘোড়ার জেনেটিক বটলনেক এসেছিল। অর্থাৎ জিন বৈচিত্র্য একেবারেই কমে গিয়েছিল। এমনটা সাধারণত ঘটে যদি সংখ্যায় খুব কমে যায় আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে অন্য ঘোড়ার সাথে। এই ঘোড়ার রঙের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সম্ভাব্য সব রকম রঙেরই পাওয়া যায়। তবে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় তা হল এদের গায়ের উজ্জ্বল রঙ। যার সাথে মিল আছে তুর্কমেনিস্তানের আকেল-টেকে ঘোড়ার। এই ঘোড়ার গতিবেগ মাঝারি। দুলকি চালের চেয়ে খানিক জোরে ছুটলেও তীব্র গতিতে ছুটতে পারে না। ১২০০ শতকে রাঠোর রাজারা এই গোড়ার প্রজনন শুরু করেন। কিন্তু বংশগতি বা কুলজী রক্ষা করতেন না। তবে ব্রিটিশ আমলে সেটা অবহেলিত হতে থাকে। কারণ ব্রিটিশরা এই ঘোড়া পছন্দ করতো না। সম্ভবত সেই সময়েই জেনেটিক বটলনেক দেখা দেয়। বর্তমানে নতুন করে যথাযথ ভাবে বংশ কুলুজী রক্ষা করে প্রজনন বৃদ্ধির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়েছে তিন হাজার মারোয়াড়ী ঘোড়া। ভারতে এক একটি মারোয়াড়ী ঘোড়ার দাম পাঁচ থেকে আট লক্ষ টাকা।
॥ইয়াকুটিয়ান ঘোড়া॥

শক রিপাবলিকের ইয়াকুটিয়ান ঘোড়া, শীত কালে।
শক রিপাবলিকের ঘোড়া। সাইবেরিয়ার +৩৮ ডিগ্রী থেকে -৭০ ডিগ্রীতে এরা দিব্বি থাকে। তবে শীতকালে তাদের গায়ের লোম প্রায় ৮০ মিলিমিটার লম্বা হয়ে যায়। একটু বেঁটে কিন্তু শক্তপোক্ত চেহারার এদের গায়ের রঙ হালকা বাদামী, ধুসর, আর ডান রঙ হয়। (ডান রঙে গায়ের রঙ হাল্কা তবে কেশর গাড় পায়ের খুরের কাছে গাড় আর পিঠে লম্বা গাড় রঙের ছোপ)। অনেকের বেলা পায়ে জেব্রার মত ছাপ ও আছে। ইয়াকুটিয়ানদের মধ্যে কয়েটি ভাগ আছে। তারমধ্যে উত্তরাংশের ভেরখোনিয়াস্ক ঘোড়া প্রাচীনতর।
॥জেজু ঘোড়া॥

দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপের ঘোড়া। মাঝারি আকারের এই ঘোড়া প্রবল শীত অনায়াসে সহ্য করে খোলা জায়গাতেই থাকতে পারে। গায়ের রঙের বৈচিত্র্য বিশাল। প্রায় সব রঙেরই পাওয়া যায়। রঙ অনুযায়ী আবার নামও পাল্টে যায়। এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রত্ন প্রমাণে ঘোড়া এই দ্বীপেই ছিল প্রস্তরযুগের শেষ দিক থেকেই।
১০৭৩ থেকেই এখানে ঘোড়ার পালন প্রজনন বেশ নিয়ম মেনে শুরু হয়। এই কাজে তারা মঙ্গোলিয়া থেকেও ঘোড়া আনতো। অধুনাকালের রেকর্ড বলছে জেজু দ্বীপ থেকে ২০হাজার ঘোড়া রপ্তানি হয়েছে।
॥আইসল্যান্ডের ঘোড়া।॥

আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে,বা ভাইকিংদের আমল থেকে, এখানে ঘোড়ার পালন প্রজনন শুরু হয়। মাঝারি গতিবেগে লম্বা দৌড়ের উপযুক্ত এখানকার ঘোড়ার সাথে মঙ্গোলিয়ার ঘোড়ার জেনেটিক সম্পর্ক পাওয়া গেছে। তবে এখন আইন করে মিশ্র-প্রজননের জন্য বাইরে থেকে ঘোড়া আনা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের জন্য ভেড়া পালকদের ঘোরাঘুরি জন্য লাগে। তাছাড়া এখান থেকে ঘোড়া মাংস জাপানে রপ্তানি করা হয়।
॥মঙ্গোলিয়ান ঘোড়া॥

শক্ত সমর্থ গড়নের মাঝারি আকারের ঘোড়া। এরা এতটাই শক্তি রাখে যে ২শ কেজি অবধি ওজন নিয়ে দিনে ৫০-৬০ কিলোমিটার যাতায়াত এদের নিত্যকর্ম। মঙ্গোলিয়ায় আসলে নানা জাতের ঘোড়াই পাওয়া যায়। আর তাদের গতিবেগও আলাদা আলাদা। পাহাড়ি অঞ্চলের ঘোড়ার পা ছোট হয়, আর খুব একটা জোরে ছুটতে পারে না। আবার খোলা ঘাসের জমির (স্তেপে এলাকার) ঘোড়াগুলো দৌড়তে পারে তীব্র গতিতে। মঙ্গোলিয়ার ঘোড়া পোষার পদ্ধতি অন্যদের চেয়ে আলাদা। ঘোড়া তাদের সারা জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী। এখানে সব ঘোড়া ছাড়া থাকে। ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতে খেতে দুরে চলে গেলে একদিন দুইদিন তাদের দেখাই পাওয়া যাবে না। তবে পালকরাও তো তেমনিই। তারাও অনেকেই প্রায় যাযাবর। এখানকার নিয়মে যে কোন লোকের ঘোড়া যে কোন লোকের জমির ঘাস খেতেই পারে।
মঙ্গোলিয়ার ঘোড়ার ঘাড়ের আর লেজের লোম বেশ লম্বা হয়। এতটাই লম্বা হয় যে ঘাড়ের লোম দিয়ে বিনুনিও বাঁধা যায়। এই ঘোড়ার লোম দিয়ে বেহালার ছড়িও বানানো হয়।
তথ্যসূচীঃ-
1. Pablo Librado, Antoine Fages, Charleen Gaunitz, Michela Leonardi, Stefanie Wagner, Naveed Khan, Kristian Hanghøj, Saleh A. Alquraishi, Ahmed H. Alfarhan, Khaled A. Al-Rasheid, Clio Der Sarkissian, Mikkel Schubert and Ludovic Orlando: The Evolutionary Origin and Genetic Makeup of Domestic Horses: Publication: . Genetics .org
GENETICS October 1, 2016 vol. 204 no. 2 423-434; https://doi.org/10.1534/genetics.116.194860
2. Katie Pieper: The Genetic History of Horses: Published by: Gene to Genome Blog Society of America.
3. Nancy S. Loving: It’s all in the Genes: Horse Traits and Heritability: Published in : Published in Horse.com on June 12, 2018
4. S.C. Gupta, Neelam Gupta, Jyotsna Behl, Rahul Behl, R.K Vijh, Gurmej Singh, S.P.S. Ahlwat: The Genetic Resources of India Marwari An Elegant Horse Breed. Published by: National Bureau of Animal Genetic Resources, Indian Council of Agricultural, Research, Karnal Haryana

আপনার লেখা সবসময় জানা তথ্যকেও নতুন দৃষ্টি দেয়| এটিও তার ব্যতিক্রম নয়| অনেক তথ্য জানলাম, আর কিছু কিছু নতুন ভাবে দেখলাম| 🙏
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। মানুষ আর ঘোড়ার সম্পর্ক মানব সভ্যতাকে একটা ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে বলা যায় মানব সভ্যতার উন্নতির পেছনে এই চারপেটে প্রাণীর অবদান প্রায় সীমাহীণ। আমাদের দেশে ঘোড়া রাজনীতির অঙ্গ হয়ে গেছে , তাই এই প্রাণীটি নিয়ে আলোচনা খুব কম হয়। আমি সামান্য চেষ্টা করলাম।
দারুন। আমরা যে ইতিহাস গবেষণার এক ‘নতুন সময়ে’ বাস করছি এই রচনা তার বড় প্রমাণ।
ধন্যবাদ