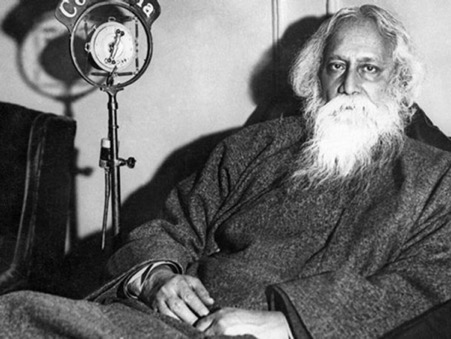
হিন্দুমেলা, শিবাজী উৎসব ও সেকুলারিজমের পথে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা (প্রথম পর্ব)
(এক)
প্রথম যুগের বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন, “নবগোপাল মিত্র এবং তাঁহার বন্ধু ও গুরুস্থানীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, ইঁহারাই বাংলার ‘স্বদেশী’র প্রথম পুরোহিত।”১ বস্তুত, ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে স্বাদেশিকতার ভাব জাগরণ ও জাতীয় চেতনার প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ‘ন্যাশনাল পেপার’এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র চৈত্রমেলা নামে একটি জাতীয় মেলার সূচনা করেন। ঘটনাটির সময়কাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা স্থাপিত হওয়ার প্রায় বছর দশেক আগে। পরবর্তীকালে এরই নামকরণ হয় হিন্দুমেলা। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার “কার্যবিবরণ হইতে ‘প্রসপেকটাস অফ এ সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অফ ন্যাশনাল ফীলিং এমং দি এডুকেটেড নেটিভস অফ বেঙ্গল’ রচিত হয়। … ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভার পান।”২ মেলাটি বিভিন্ন সময়ে জাতীয় মেলা বা স্বদেশী মেলা নামেও পরিচিতি লাভ করে। হিন্দুমেলার উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রায় একই কথা বলেছেন — “রাজনারায়ণ বসুকে এই নুতন স্বদেশিকতার গুরু বলিলে বোধহয় শব্দের অপপ্রয়োগ হইবে না। ১৮৬১ অব্দে তিনি মেদিনীপুর হইতে ‘শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা স্থাপনের এক প্রস্তাব’ শীর্ষক ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পরে (১৮৬৫) কলকাতায় আসিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়া ‘স্বাদেশিকদের সভা’ স্থাপন করেন। প্রধানত ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলা স্থাপিত হয়।”৩
হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হল রাজা নরসিংহ রায় বাহাদুরের চিৎপুরের বাগানবাড়িতে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক হলেন মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। শিশিরকুমার ঘোষ এবং মনমোহন বসুও এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। একমাসেরও কম সময়ের প্রস্তুতিতে আয়োজিত এই মেলা প্রথম বছর খুব ছোট আকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মনমোহন বসুর ভাষায়, “জন্মদিনে কেবল অনুষ্ঠাতা ও কতিপয় বান্ধব মাত্র উৎসাহী ছিলেন। সে যেন নিজ বাটী ও পাড়াটী বলিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা।”৪ পরবর্তীকালে এই মেলার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা কমলকৃষ্ণ দেব, রমানাথ ঠাকুর, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পরের বছর বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের মতে, “দ্বারকানাথ ঠাকুরের ‘জমিদার সভা’, দেবেন্দ্রনাথ-প্রমুখের ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ বা পরবর্তীকালে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থাপিত ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ রাজনীতিকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেছিল, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু ‘হিন্দুমেলা’ বা ‘জাতীয় মেলা’ গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবর্তিত হয়েছিল। এর ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল ‘স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বদেশের উন্নতি করা’।”৫ একই কথা লিখেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও — “সংক্ষেপে বলিতে গেলে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল।”৬ বস্তুত এই মেলার বৈশিষ্ট্যই ছিল – দেশীয় শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ দান, দেশীয় প্রতীক, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, সঙ্গীতের চর্চা, কুস্তি-ব্যায়াম প্রভৃতির প্রতি উৎসাহ দান। একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় — “এই হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে না-ও হয়, সর্ব্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition এর) পত্তন করিল।”৭
হিন্দুমেলার নামকরণের মধ্যে দিয়ে সেই যুগের বুদ্ধিজীবীদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে মনোভাবটি প্রকাশ পায়, তা যথার্থভাবে তুলে ধরেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, প্রবাসী মাসিক পত্রিকার পৌষ ১৩২৯ সংখ্যায় ‘হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র’ প্রবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন, “সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খ্রিষ্টীয়ান প্রভৃতির এদেশের উপর কোনও বিশেষ দাওয়াদাবী আছে, ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। এই সংকীর্ণ স্বদেশিকতার প্রেরণাতেই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়। সেই সংকীর্ণ স্বদেশিকতার প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-বিবাহবিধির প্রতিবাদ করেন। আর সেই স্বদেশিকতার আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন নামে সেইরূপ ভাবে ও কার্য্যেও ইহা হিন্দুমেলাই হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ সকলে হিন্দু ছিলেন। এই মেলাতে যে সকল বক্তৃতাদি প্রদত্ত হয়, তাহা সকলই হিন্দু-ভাবের দ্বারা প্রণোদিত ও হিন্দুর গুণ-গরিমায় পরিপুষ্ট ছিল।”৮ উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের উপায় ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। যোগেশচন্দ্র বাগলের গ্রন্থ থেকে, এর মধ্যেকার প্রথম দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে — “১) এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা হিন্দুজাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্যসকল সংসাধন জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করতঃ এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। ২) প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদুর উন্নতি হইল, এই বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্র-সংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।”৯ বিপিনচন্দ্র আরও জানিয়েছেন, “যতদুর মনে পড়ে বোধহয় এই হিন্দু মেলা ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রথমে তাঁহার ‘হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব’ শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলেন।”১০ যদিও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে ১৮৭১ সালে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ভবনে জাতীয় সভার অধিবেশনে রাজনারায়ণ ওই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে বিপিনচন্দ্রের মন্তব্য খানিকটা অনুকরণ করে বলা যায়, স্বদেশিকতাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমার্থক করে তোলবার ব্যাপারে সত্যিই রাজনারায়ণ বসু আর নবগোপাল মিত্র ছিলেন পুরোহিত।
(দুই)
১৮৬৭ সালে যখন হিন্দু মেলা শুরু হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছয় বছরের বালকমাত্র হলেও ক্রমেই অনুষ্ঠানটির উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। কারণটা আর কিছুই নয়, আমরা দেখেছি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ সহ ঠাকুরবাড়ির একাধিক সদস্য এই মেলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। কয়েক বছর পরেই মেলার নবম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ‘জীবনস্মৃতি’-তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, “আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা’ বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়ছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত ‘মিলে সবে ভারতসন্তান’ রচনা করিয়ছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুশীলোক পুরস্কৃত হইত। লর্ড কার্জনের সময় দিল্লি দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্ৰবন্ধ লিখিয়াছি – লর্ড লিটনের সময় লিখিয়ছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্ৰকাশ করেন নাই। টাইমস পত্রেও কোনো পত্ৰলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়ছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।”১১
এইখানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি সম্ভবত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। “হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া” যে কবিতা পাঠের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত দ্বিতীয় কবিতা, ১৮৭৭ সালে। তার দুই বছর আগেই ১৮৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে তিনি যে স্বরচিত কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, তার উল্লেখ জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ করতে ভুলেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, কবিতাটি সেই বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি ‘অমৃত বাজার’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সংযুক্ত হয়ে ‘হিন্দুমেলায় উপহার’ নামে প্রকাশিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ‘দ্য ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ’ পত্রিকা এই সম্বন্ধে লিখেছিল, “The Hindoo Mela. The Ninth Anniversary of the Hindoo Mela was opened at 4 p.m. on Thursday, the 11th instant, at the well-known Parseebagan … by Rajah Komul Krishna Bahadoor … Baboo Robindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendro Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory ; the suavity of his tone, much pleased his audience.”১২ যদিও পনেরো নয় ; কবির প্রকৃতপক্ষে বয়স তখন ছিল তেরো বছর নয় মাস। কিশোরবেলার উচ্ছ্বাসে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিতে পুরাণের রাম, যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে ইতিহাসের পৃথ্বীরাজ, দুর্গাবতী প্রমুখ যাবতীয় হিন্দুবীরকে স্মরণ করেছিলেন। কবিতার কিছুটা অংশ বরং উদ্ধৃত করা যাক —
“… চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্মভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।
দেখেছি সে-দিন যবে পৃথ্বীরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত-কোলে।
দেখেছি সে-দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীরবালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।
তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময় ;
যদিও তাদের চিতাভস্মরাশি,
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে !
আবার সে-দিন(ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ-ভারতভূমি
কী সুখের দিন ! কী সুখের দিন !
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে?
রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে)
স্বাধীন নৃপতি আর্য-সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সেসব কেবল রয়েছে গাঁথা !
শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ-ভারতভূমি,
আর কি সে-দিন আসিবে ফিরে !
ভারত-কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন ;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া,
আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি।
তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবি রে পুনঃ,
সে-দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদজলে? …”১৩
আমরা সেই সময়কার পুরানো পত্রপত্রিকা হাতড়ালে দেখতে পাই, ১১ ফাল্গুন ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানটির কথা ছাপা হয়েছিল – “গত পূর্ব্ব শুক্রবার সারকিউলার রোড পারসীবাগানে মহা সমারোহে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০০ হিন্দু ভদ্রলোক মেলার স্থলে উপস্থিত হন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া উহা মুখস্থ পাঠ করিয়া সকলের চিত্ত রঞ্জন করে এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন।”১৪
অনুষ্ঠানটি নিয়ে কোনো মতভেদ না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের পঠিত কবিতাখানি নিয়ে কিন্তু কিছুটা বিতর্কের অবকাশ আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সকলেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত কবিতা প্রসঙ্গে ‘হিন্দুমেলায় উপহার’ শীর্ষক কবিতাখানির কথা বললেও, ‘রবিজীবনী’ গ্রন্থে প্রশান্তকুমার পাল ২৯শে মে ১৯৭৬ এর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী লিখিত ‘রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা’ শীর্ষক প্রবন্ধের সূত্র তুলে দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ লিখিত ‘হোক ভারতের জয়’ নামের একটি কবিতা “ঢাকা থেকে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত ‘বান্ধব’ মাসিক পত্রিকাটির মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। “কবিতাটির শেষে ‘(র)’ অক্ষরটি লেখা আছে এবং পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে : ‘হিন্দুমেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল।’ শ্রীঘটক চৌধুরী মনে করেছেন হিন্দুমেলার উদ্বোধন দিবসে এই কবিটাটিই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ‘পঠিত’ হয়েছিল ; ‘হিন্দুমেলার উপহার’ নয়। … এই কবিতাটিই যে হিন্দুমেলার উদ্বোধনী দিবসে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেছিলেন তার প্রমাণ Indian Daily News ও Bengalee-র প্রতিবেদনেই আছে – যেখানে কবিতাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে ‘a Bengali poem on Bharut (India)’, যা এই শিরোনামটিকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল।”১৫ ‘হোক ভারতের জয়’ কবিতাটির প্রাসঙ্গিক অংশ পড়লে বোধহয় বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে।
“এসো এসো ভ্রাতৃগণ ! সরল অন্তরে
সরল প্রীতির ভরে
সবে মিলি পরস্পরে
আলিঙ্গন করি আজ বহুদিন পরে।
এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ,
ভারত সমাজে তবে
হৃদয় খুলিয়া সবে
এসো এসো এসো করি প্রিয়সম্ভাষণ।
দূর করো আত্মভেদ বিপদ-অঙ্কুর,
দূর করো মলিনতা
বিলাসিতা অলসতা,
হীনতা ক্ষীণতা দোষ করো সবে দূর।
ভীরুতা বঙ্গীয়জন-কলঙ্ক-প্রধান —
সে-কলঙ্ক দূর করো,
সাহসিক তেজ ধরো,
স্বকার্যকুশল হও হয়ে একতান।
হল না কিছুই করা যা করিতে এলে —
এই দেখো হিন্দুমেলা,
তবে কেন কর হেলা?
কী হবে কী হবে আর তুচ্ছ খেলা খেলে?
সাগরের স্রোতসম যাইছে সময়।
তুচ্ছ কাজে কেন রও,
স্বদেশহিতৈষী হও —
স্বদেশের জনগণে দাও রে অভয়।
নাহি আর জননীর পূর্বসুতগণ —
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীর,
অনন্তজলধিতলে হয়েছে মগন। ….”১৬
যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেই ‘জীবনস্মৃতি’তে ঘটনাটির উল্লেখ করতে ভুলেছেন, তাই আজ আর কিছুতে জানা বোধহয় সম্ভব নয় যে, ১৮৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন কবিতাখানি আবৃত্তি করে উপস্থিত শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছিলেন।
(তিন)
১৮৭৭ সালের মার্চ মাসে হিন্দুমেলার একাদশতম অধিবেশনে আবার আমরা পেলাম কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে। এবার অধিবেশন বসেছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানে। এবার রবীন্দ্রনাথ মেলা প্রাঙ্গণে সদ্য সমাপ্ত দিল্লি দরবার নিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। ৪ঠা মার্চ ‘সাধারণী’ পত্রিকার প্রতিবেদক জানিয়েছেন, “আমরা নিরাশ মনে নবগোপাল বাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্র বাবু ‘দিল্লীর দরবার’ সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছায়ায় দুর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা ও গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতের বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আদ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁর সুকুমার কন্ঠের আবৃত্তির মাধুর্য্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তার কোমল হৃদয় পর্য্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। … একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমুল্য রত্ন লাভ হইবে।”১৬ রবীন্দ্রনাথের কন্ঠে যে কবিতাটি শুনে তৎকালীন বিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন আপ্লুত হয়েছিলেন, সেই কবিতাটি একবার পড়া যেতে পারে।
“দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে !
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির-রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্য-কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ন নয়নে দেখিতেছ তুমি – কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি —
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই-সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি, তখনো একত্রে ভারত মেলে নি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে —
বন্ধনশৃঙ্খলে করিতে পূজা !
ব্রিটিশ-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ-চরণে লোটাতে শির —
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !
হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কন্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ-রাজের বিজয়রবে?
ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক’জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।১৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরে রবি জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন, লর্ড লিটন প্রবর্তিত ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট বা দেশীয় সংবাদপত্র আইনের কঠোর বিধিব্যবস্থার জন্য কবিতাটি সমকালীন কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরে, ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৯, সজনীকান্ত দাসের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “প্রথম লর্ড লিটনের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে কবিতা লিখেছিলুম হিতৈষীদের সতর্কতা মান্য করে সেটা লোপ করে দেওয়া হয়েছিল। মনে আছে, কেউ কেউ সেটা হাতে লিখে প্রচার করে বেড়াতেন।”১৮
এইখানে আর একটা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনার আছে, তা হল — রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত তিনটি কবিতাতেই আমরা দেখছি, অতীতের গৌরবময় স্মৃতি রোমন্থন করে বর্তমানকে গভীর জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত করবার প্রয়াস। ‘নেশন কি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন — “অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন। … অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ — একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা — এইগুলিই আসল জিনিস, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্যসত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়; একত্রে মাসুলখানা-স্থাপন বা সীমান্তনির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। … অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন।”১৯ মুশকিলটা হল, প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে পুরাণ ও ইতিহাস মিলেমিশে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ কখন নিজের অগোচরেই হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেল — তা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ টেরও পাননি।
এই কথা অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই যে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের ‘দিল্লি দরবার’ কবিতাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিলেতে রক্ষণশীল দলের নেতা বেঞ্জামিন ডিজরেলী প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৮৭৬ সালে ‘রয়্যাল টাইটেল এ্যাক্ট’ পাস করিয়ে রানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভুষিত করালেন। ১৮৭৭ সালে বড়লাট লর্ড লিটন বিপুল সমারোহ ও আড়ম্বরের সঙ্গে মুঘল সম্রাটদের মতো দিল্লিতে দরবার আহ্বান করে মহারানীকে ওই উপাধি প্রদানের কথা ঘোষণা করলেন। ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজারা ওই দরবারে উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এই মহাসমারোহ আয়োজন করা হল কখন? যখন দক্ষিণ ভারতে প্রবল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্নের জন্য হাহাকার করছে। নেপাল মজুমদার জানিয়েছেন, “বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় বাহান্ন লক্ষ লোক মারা যায়।”২০ এই পরিস্থিতিতে দেশীয় রাজন্যবর্গের ব্রিটিশ পদলেহন সম্ভবত কিশোর রবীন্দ্রনাথের স্বজাত্যবোধকে তীব্র আহত করেছিল এবং তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিল — ‘ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক আমরা গাব না / আমরা গাব না হরষ গান, / এসো গো আমরা যে ক’জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।’
হিন্দুমেলা নিয়ে মানুষের উৎসাহ ক্রমেই কমে আসছিল। ততদিনে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন বা ভাত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় মনে হয় এই জাতীয় মেলার সতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখবার প্রয়োজন ক্রমেই কমে এসেছিল কারণ এর উদ্দেশ্য ভারত সভার মধ্যেই অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। আরও কয়েকটি বছর টিমটিম করে চলবার পর হিন্দুমেলার অধিবেশন অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। আমরা দেখেছি, হিন্দুমেলা যখন আরম্ভ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন নিতান্তই বালক এবং তাঁর কৈশোর অতিক্রম করবার আগেই এর অবলুপ্তি ঘটেছিল। তাই যৌবনের সমস্ত উদ্দীপনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মেলার পাশে উপস্থিত থাকতে পারেন নি, হিন্দুমেলা সংক্ষিপ্ত সময়ে স্বনির্ভরতা ও স্বদেশচেতনার যে সাধনা করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, এমনকি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাতেও এই স্বনির্ভরতার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই বৃহত্তর অবদান সত্ত্বেও বঙ্গীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা করে হিন্দুমেলা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল, পরবর্তীকালে তা-ই ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে মহিরুহর আকার নেয়।
(চার)
আগের কয়েকটি পর্বে আমরা দেখলাম, কিশোর রবীন্দ্রনাথ রীতিমতো হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের মতোই প্রাচীন ঐতিহ্যের মহিমাকীর্তনে রত; ১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সরোজিনী’ নাটকে তিনি রাজপুত বিধবা নারীদের জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করে সতী হওয়ার ঘটনাগুলোকে মহিমান্বিত করে সতীত্বের গুণগান করছেন —
“জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন ! — শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র’লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনলশিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন —
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই !
জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন ! দেখ্ রে তোরা !
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি ;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥
আয় আয় বোন ! আয় সখি আয় !
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ !
দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্ রে চন্দ্রমা দেখ্ রে গগন !
স্বর্গ হতে সব দেখ্ দেবগণ,
জলদ-অক্ষরে রাখ্ গো লিখে।
স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরান অনল-শিখে॥”২১
‘রাজনীতির রুদ্ধ দ্বার ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে সন্দীপন সেন লিখেছেন, “শুধু ‘সতী’-র গুণকীর্তন বা মুসলমানদের ‘যবন’ বলে সম্বোধনই নয়, এ গানে যবনদের ‘প্রতিফল’ ভুগতে হবে বলে এক ধরণের সাবধানবাণীও দেওয়া হয়েছে, অনুমান করা যায় যা হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের খুব পছন্দ হয়েছিল।”২২ চোদ্দো বছর বয়সি কিশোর রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি তখনও তৈরি হয়নি, বলে এইসব কবিতা অগ্রাহ্য করা যেতেই পারে কিন্তু সমস্যা হল আরও চব্বিশ বছর পর ১৮৯৯ সালেও রবীন্দ্রনাথকে দেখি সহমরণের মহিমাকীর্তন করতে ; ‘কথা’ কাব্যগ্রন্থের ‘বিবাহ’ কবিতায়, যার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করলাম —
“… নিশীথ-রাতে আকাশ আলো করি
কে এল রে মেত্রিপুরদ্বারে !
‘থামাও বাঁশি’ কহে, ‘থামাও বাঁশি —
চতুর্দোলা নামাও রে দাসদাসী।
মিলেছি আজ মেত্রিপুরবাসী
মেত্রিপতির চিতা রচিবারে।
মেত্রিরাজা যুদ্ধে হত আজি,
দুঃসময়ে কারা এলে দ্বারে?’
‘বাজাও বাঁশি, ওরে, বাজাও বাঁশি’
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে,
‘এবার লগ্ন আর হবে না পার,
আঁচলে গাঁঠ খুলবে না তো আর —
শেষের মন্ত্র উচ্চারো এইবার
শ্মশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে।’
‘বাজাও বাঁশি, ওরে, বাজাও বাঁশি’
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে।
বরের বেশে মোতির মালা গলে
মেত্রিপতি চিতার’পরে শুয়ে।
দোলা হতে নামল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র-‘পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের ‘পরে থুয়ে।
নিশীথ-রাতে মিলনসজ্জা-পরা
মেত্রিপতি চিতার’পরে শুয়ে।
ঘন ঘন জাগল হুলুধ্বনি,
দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা।
কয় পুরোহিত ‘ধন্য সুচরিতা’,
গাহিছে ভাট ‘ধন্য মৃত্যুজিতা’,
ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল চিতা —
কন্যা বসে আছেন যোগাসনা।
জয়ধ্বনি উঠে শ্মশান-মাঝে,
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।”২৩
কেবলমাত্র ‘বিবাহ’ কবিতাটিই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো রবীন্দ্রনাথের ‘কথা’ কাব্যগ্রন্থেরও অনেক কবিতাই ছিল মুসলিম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে রাজপুত ও শিখ জাতির বীরত্বের গাথা — ‘বন্দী বীর’, ‘মানী’, ‘প্রার্থনাতীত দান’, ‘হোরিখেলা’ — উদাহরণ অসংখ্য। তবে ইতিহাসের বিকৃতি করবার অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ওঠেনি, যা উঠেছে ওই সময়ের আরেকজন দিকপাল সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।
অত্যন্ত একটি বিতর্কিত বিষয়ে প্রবেশ করে ফেলেছি তাই মনে করি যে, বিষয়টা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। মোটামুটিভাবে ১৮৭০ সালের পরবর্তী বছরগুলিকে শিবনাথ শাস্ত্রী আখ্যা দিয়েছিলেন ‘হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা’ বলে। ১৮৭০ সালের পরবর্তী ত্রিশ বছরের সময়কালটাকে ভালো করে লক্ষ্য করুন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে গৌরবময় বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রাথমিক উৎসাহ উদ্দীপনা তখন ক্রমেই থিতিয়ে এসেছে। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দিন শেষের পথে ; দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ক্রমশই জাঁকিয়ে বসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে কেশবচন্দ্র সেন ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব এক প্রকার পরিত্যাগ করে “যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতির সাধনার্থ কলিকাতার সন্নিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া, কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ একান্তবাসী হইলেন ; স্বপাকে আহার করিতে লাগিলেন; গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন ; এবং বৈরাগ্য প্রচারে রত হইলেন।”২৪ এই সময়েই ব্রিটিশ সরকারের আনা ‘সহবাস সম্মতি আইন’ (Age of consent bill) নিয়ে গোঁড়া হিন্দুরা নির্লজ্জভাবে নারীবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। রক্ষণশীল নেতা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি ইত্যাদিরা এই আইনটির বিপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে প্রধান ভুমিকা নিলেন। হিন্দু নেতা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন লেখেন, “কতিপয় হিন্দুকুলকুঠার একত্র হইয়া সনাতন ধর্মানুশাসিত হিন্দুসমাজকে কলুষিত ও নির্যাতিত করিবার জন্য বরবর্ণিনী কুলকামিনীগণের কুলমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ‘স্ত্রী-সমাগম-সম্মতি-কাল’ (Age of consent) নিরুপণার্থ রাজদ্বারে আইন প্রার্থী হইয়া সভাসমিতি ও সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন করিয়া তুলিয়াছে। … আইনটিপ্রচলিত হইলে ধর্মাধিকারের মূলোচ্ছেদ হইবে।”২৫ শশধর তর্কচুড়ামণি লিখলেন, হিন্দুর গর্ভাধান কার্য ‘অতি গুরুতর ও পরমাদরণীয় ধর্মানুষ্ঠান’। বাবো বছরের আইন করলে হিন্দুদের ‘মস্তকে বজ্রপাত করা হইবে, হিন্দুর হৃদয়ে শূলবিদ্ধ হইবে’। রক্ষণশীল পত্রিকা ‘বঙ্গবাসী’ আইনটির বিরোধিতা করতে গিয়ে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হল। ১৮৯১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বিলটির বিরোধিতায় আয়োজিত একটি সভায় লাখখানেক লোকের ভিড় হল, সে যুগে যা প্রায় অকল্পনীয়।
এমনকি প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সনাতন ধর্মবিরোধী কট্টর বিজ্ঞানবাদী মিল-এর বস্তুবাদী দর্শন, কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদী দর্শন এবং রুশোর সাম্যবাদী দর্শনে প্রভাবিত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্ববিরোধিতা কাটিয়ে উঠে ‘মেলাবেন তিনি মেলাবেন’ পথের অনুসারী হয়ে ক্রমেই পরিণত হলেন রক্ষণশীল, পশ্চাৎমুখী, হিন্দু জাতীয়তাবাদী। (আধুনিক রাজনৈতিক অর্থে নয়) যে বঙ্কিম ‘জৈবনিক’ প্রবন্ধে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, “যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁর কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব।”২৬ সেই বঙ্কিমই ‘ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে’ প্রবন্ধে অনায়াসে বলে ফেললেন, “ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতি অবলম্বিত খ্রীষ্টধর্মাপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত ও নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু খ্রীষ্টিয় সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরেকথিত মিল-কৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে। হিন্দুদিগের মত কর্ম্মফল মানিলে বা হিন্দুদিগের মায়াবাদে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হয়।”২৭ নবরূপে বঙ্কিম হিন্দু ধর্মকেই জগতে সম্পুর্ণ ধর্ম বলে মনে করতেন। যদিও তাঁর ধর্মতত্ত্ব ছিল শশধর তর্কচুড়ামণি জাতীয় প্রচলিত হিন্দু গোঁড়ামির থেকে আলাদা।
স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তরা গর্ব করে বলেন যে ভারতে চরমপন্থী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের অধিকাংই ছিলেন বিবেকানন্দের ভক্ত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের এই বিপুল সমাদরের কারণ অবশ্যই জাতীয় গৌরববোধ, যা বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুসৃত ধর্মটিকে তাদের শাসকগোষ্ঠীর দরবারে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯০০ সালের ২৭ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা শেক্সপিয়ার ক্লাবে প্রদত্ত ‘আমার জীবন ও ব্রত’ শীর্ষক বক্তৃতায় বিবেকানন্দ নিজেও বলেছিলেন, “আপনারা কি কখনও এমন দেশ দেখিয়াছেন? সেখানে যদি আপনি দস্যুদল গঠন করিতে চান, তবে দলের নেতাকে কোনরূপ ধর্ম প্রচার করিতে হইবে, তারপর কতকগুলি অসার দার্শনিকতত্ত্ব সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, ‘এই দস্যুবৃত্তিই ভগবান্-লাভের সবচেয়ে সুগম ও সহজ পন্থা’। তবেই নেতা তাহার দল গঠন করিতে পারিবে। অন্যথা নয়। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এ-জাতির লক্ষ্য ও প্রাণশক্তি — ধর্ম। এই ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হয় নাই বলিয়াই জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে। … ইংলণ্ড বা আমেরিকায় যদি ধর্মপ্রচার করিতে যান, তাহা হইলে রাজনৈতিক পন্থা অনুসারে আপনাকে কাজ করিতে হইবে। সেখানে পাশ্চাত্য রীতি-অনুযায়ী ভোট-ব্যালট, প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন প্রভৃতি দ্বারা সংস্থা ও সমিতি গঠন করিতে হইবে, কারণ উহাই পাশ্চাত্যজাতির ভাষা ও রীতি। পক্ষান্তরে আপনি যদি ভারতবর্ষে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চান, তাহা হইলে আপনাকে ধর্মের ভাষায় কথা বলিতে হইবে।”২৮ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবন্ধেও স্বামী বিবেকানন্দ দাবী করেন, “… এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম ; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, …”২৯ স্বামী বিবেকানন্দ রচিত ‘বর্তমান ভারত’এর শেষাংশে লিখিত যে ‘স্বদেশমন্ত্র’, যা কিনা অসংখ্য দেশপ্রেমিক তরুণকে জাতীয় সংগ্রামে তথা বিপ্লবী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে তা হল — “হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা —এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না — তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্ৰী, দময়ন্তী ; ভুলিও না — তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না — তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের — নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না — তুমি জন্ম হইতেই ‘মায়ের’ জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভূলিও না — তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না — নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই ! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদৰ্পে বল — আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই । বল — মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্ৰ-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদৰ্পে ডাকিয়া বল — ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই — ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বৰ্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিন-রাত, ‘হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর’।”৩০ — এই স্বদেশমন্ত্রে কোথাও কি অহিন্দুর স্থান আছে? গৌরীনাথ অথবা জগদম্বের কাছে কোনো অহিন্দুর পক্ষে নিজেকে মানুষ করবার প্রার্থনা জানানো সম্ভব নয়; সম্ভব নয় উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্করের উপাসনা করাও। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন, বিবেকানন্দের “এইসব আলঙ্কারিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কিন্তু মিশে ছিল পুরোপুরি অস্বচ্ছতা — নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি, গণ-সংযোগের পদ্ধতি, বা এমনকি রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধেও। তবু এই পাঁচমিশেলি ভাবের মধ্যে নিহিত ছিল তাঁর আবেদন শক্তি আর পৌরুষের অর্চনা, অস্পষ্ট জনমুখিতা ও হিন্দু-গৌরবের ভাব-উদ্রেকের সঙ্গে দেশপ্রেমের এই মিশ্রণ আসন্ন স্বদেশী পর্বে তরুণদের পক্ষে বাস্তবিকই তীব্র মাদক বলে প্রমাণ হয়।”৩১
শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করা নয়, এইসমস্ত বক্তব্যের মাধ্যমেই বোধহয় ভারতবর্ষে রাজনীতির সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গলাগলির পথিকৃৎ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর দেখানো পথ ধরেই চরমপন্থীরা পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের ধারণাকে আপন করে নিতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র পথ বলে মনে করলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন এই পদ্ধতির পথিকৃৎ। “যেমন, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে গণসংযোগের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার (সহবাস সম্মতি বিষয়ে তিনি জোট বাঁধেন সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে, আর তারপরেই ১৮৯৪ থেকে সংগঠিত করেন গণপতি উৎসব), জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে একই সঙ্গে স্বদেশিক-তথা-ঐতিহাসিক ভজনা গড়ে তোলা (শিবাজী উৎসব, এটি তিনি সংগঠিত করেন ১৮৯৬ থেকে)।”৩২ ১৯০৬ সালের ৩রা জানুয়ারি বেনারসে ‘ভারত ধর্ম মহামন্ডল’-এ ভাষণ দিতে গিয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, “Hindu religion as a whole is made up of different parts co-related to each other as so many sons and daughters of one great religion. If this idea is kept in view and if we try to unite the various sections it will be consolidated in a mighty force. So long as you are divided amongst yourselves, so long as one section does not recognise its affinity with another, you cannot hope to rise as Hindus. Religion is an element in nationality. … If we lay stress on it forgetting all the minor differences that exist between different sects, then by the grace of Providence we shall ere long be able to consolidate all the different sects into a mighty Hindu nation. This ought to be the ambition of every Hindu.”৩৩ বঙ্গদেশে প্রথম যুগের রাজনীতিবিদ বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, “সেকালে আমরা স্বদেশাভিমানের অনুশীলন করিতে যাইয়া এককালে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর যে বিরোধ ছিল তাহার স্মৃতিকেই আশ্রয় করিয়াছিলাম। মুসলমানকে খাটো দেখিলে আমাদের স্বাজাত্যাভিমান পরিতৃপ্ত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে এইভাবেই আমাদের স্বাজাত্যাভিমানকে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের আশ্রয়েই ‘দুর্গেশনন্দিনী’র আখ্যায়িকা গড়িয়া ওঠে। কতলু খাঁর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে যাইয়া অসহায়া হিন্দু বিধবা বিমলা তাঁহার বুকে ছুরি মারিয়া সহস্র প্রহরীবেষ্টিত মুসলমান শিবির হইতে নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িলেন — এই দৃশ্যে বাঙালী হিন্দু স্বজাতি গৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছিল। … তারপর জগৎসিংহ এবং ওসমান। উভয়েই বীরপুরুষ, উভয়ের মধ্যেই অনেক সদগুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জগৎসিংহকেই বড় করিয়া ধরিয়াছেন। সর্ব্বশেষে আয়েষা এবং তিলোত্তমা — দু্ইই অপূর্ব্ব সৃষ্টি। … তিলোত্তমাতে হিন্দু নারীত্বের ছবি অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আয়েষাতেও রমণী চরিত্রের মাধুর্য্য এবং শক্তি অল্প ফুটে নাই। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমাকেই আয়েষা অপেক্ষা বড় করিয়া তুলুন আর নাই তুলুন বেশী মিষ্টি করিয়া আঁকিয়াছেন। ইহাতে আমাদের নবজাগ্রত স্বাজাত্যাভিমানে নুতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। যেমন দুর্গেশনন্দিনীতে সেইরূপ কপালকুণ্ডলাতে এবং মৃণালিনীতেও বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু এবং মুসলমানকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়াছেন, এবং সর্ব্বত্রই হিন্দুর তুলনায় মুসলমানকে খাটো করিয়া আঁকিয়াছেন।”৩৪
নিজের ‘প্রথম আলো’ উপন্যাসে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসটিকে তথ্য পরিবর্তনের (তথ্যবিকৃতিও নয় কি?) দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সন্ন্যাস বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে লিখিত আনন্দমঠ উপন্যাস এবং বন্দেমাতরম গান যতোই জাতীয়তাবাদীদের উদ্বুদ্ধ করুক না কেন, মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে আনন্দমঠের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বারবার এর পাঠ বদল করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে এটি আদৌ ইংরেজবিরোধী উপন্যাস নয়। বঙ্গদর্শনের সপ্তম বছরে অর্থাৎ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা (বঙ্গদর্শনের ৮৪ তম সংখ্যা) থেকে ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত আনন্দমঠ উপন্যাস প্রথমবার প্রকাশিত হয়। সেই ধারাবাহিক উপন্যাস সিরিজ আর পরবর্তীকালে প্রকাশিত আনন্দমঠ উপন্যাসের পুর্ণাঙ্গ সংস্করণ পড়লে দেখা যায় কিভাবে ‘ইংরেজসেনা’ ‘যবনসেনা’-তে এবং ‘ইংরেজ’ কখনও ‘যবন’-এ কখনও ‘নেড়ে’-তে পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে সত্যানন্দ ও চিকিৎসকের মধ্যেকার একটি কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে —
“সত্য। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই — এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল। … চিকিৎসক বলিলেন, … আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। … ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে – নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। … ইংরেজ এক্ষণে বণিক — অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে ; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।”৩৫ অথচ তৎকালীন ইতিহাস বলছে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলাদেশ ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রায় ৩৭ বছর ব্যাপী অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হওয়া এই বিদ্রোহকে ইতিহাসবেত্তারা ‘সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ’ নামে অভিহিত করেন।
বঙ্কিমচন্দ্রের এই খোলাখুলি ইংরেজ-প্রীতি এবং হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবাহন সত্ত্বেও তৎকালীন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিপিনচন্দ্র পাল জানিয়েছেন, “মুসলমানকে খাটো করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। যাঁহারা বঙ্কিম সাহিত্যের আশ্রয়ে স্বদেশপ্রীতির অনুশীলন করিতেন তাঁহাদের অন্তরেও মুসলমানের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। লেখক এবং পাঠক — উভয়পক্ষই মুসলমান শাসনের বিরোধের স্মৃতি জাগাইয়া বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন। সত্য বলিতে কি, ভিতরে ভিতরে এই সকল চিত্রে মুসলমান বলিতে আমরা মুসলমানকে বুঝি নাই, যে স্বাধীনতার পরিপন্থী তাহাকেই বুঝিতাম। মুসলমান এই সকল সাহিত্যে একটি ভাবের প্রতীকমাত্র হইয়াছিলেন।”৩৬ স্পষ্টতই, বিপিনচন্দ্রের এই জাস্টিফিকেশন কুযুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, পড়বার পর একটি প্রাচীব বাংলা প্রবাদ মনে পড়ে যায় – ঝি কে মেরে বউ কে শেখানো!
ঠিক এই বক্তব্যটাই তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক সুমিত সরকার। তাঁর মতে, বঙ্কিম বারংবার বলেছেন – “বাঙলা তার স্বাধীনতা হারায় পলাশীতে নয়, বক্তিয়ার খিলজী আসার সঙ্গে সঙ্গে। আঞ্চলিক জীবনে মুঘল কেন্দ্রীকরণের ক্ষতিকর প্রভাবের উপর তিনি জোর দিয়েছেন, আর তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে (বিশেষ করে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম-এ) মুসলমানদের নিন্দা করেছেন যথেচ্ছ। … বিপান চন্দ্র যাকে যথার্থই ‘আনুকল্পিক (ভাইকারিয়স) জাতীয়তাবাদ’ বলেছেন, তা গড়ে ওঠে এই ভাবেই। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু লিখলে তা বিপজ্জনক হতে পারত (যেমন, বঙ্কিম ছিলেন সরকারি কর্মচারী) — এই যুক্তিতে মাঝে মাঝে সেটিকে ন্যায্য প্রমাণ করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশের জায়গায় মুসলমানকে বসিয়ে, ঝি-কে মেরে বৌকে শেখানোর ফলও চরম ক্ষতিকর না-হয়ে যেত না। ‘স্বদেশী’ হিন্দু যুবকরা, বিশেষ করে ১৯০৫ থেকে, বঙ্কিমকে দেবতা করে তুলেছিল। … মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও অচিরেই তাঁদের নিজস্ব ধরণের ‘আনুকল্পিক জাতীয়তাবাদ’ গড়ে তুলতে থাকেন। যেসব কালপর্ব বা ব্যক্তিকে (যেমন, আওরঙ্গজেব) হিন্দুরা হেয় করতেন, বিশেষ করে সেগুলিকেই তাঁরা মহিমান্বিত করেন, আর বিশ্ব জুড়ে ইসলামের হৃত গৌরবের জন্য জাগিয়ে তোলেন স্মৃতিকাতরতা।”৩৭ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবদুল লতিফ প্রমুখ মুসলমান বুদ্ধিজীবীর উদ্ভট মনোভাব। ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপণ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা ও মুখপত্র আবদুল লতিফ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের জন্য উর্দু মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব জানান কারণ তাঁর মতে উর্দু না জানলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহলে কোনোপ্রকার গতিবিধি সম্ভব নয়। লতিফ সাহেবের আত্মজীবনী, ‘A short account of my life’ গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র নিয়ে বদরুদ্দীন উমর দেখিয়েছেন, লতিফ সাহেব মনে করতেন, “উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানরা আরব, ইরান, তুর্কি ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুসলমান বিজেতা, শাসনকর্তা, ধর্মনেতা, আলেম প্রভৃতিদের বংশধর। অর্থাৎ তাঁরা বাঙালী নন, কাজেই বাঙলা তাঁদের মাতৃভাষাও নয়। সেই হিসেবে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের বাঙলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন তাঁর কাছে ছিল সম্পুর্ণ অবান্তর।”৩৮ হুমায়ুন আজাদ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, “আবদুল লতিফের মতো সুবিধাবাদী সমাজবিলগ্নরাই উনিশ-বিশ শতকে সৃষ্টি করে উর্দু-বাঙলা কলহ। সমাজবিলগ্নরা দাবী করতে থাকে যে উর্দুই মুসলমানের ভাষা ; এক আহমরি ভাষা, যার পদ্যে পদ্যে ইসলামি সুগন্ধ আর পেশিতে ইসলামি জোশ! অন্যদিকে বাঙলা অমুসলমানের ভাষা – ভিরু ও পৌত্তলিক।”৩৯ তাই এই সময়ের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতা হস্তচ্যুত অভিজাত মুসলমান সমাজ অন্ধ আক্রোশে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুই বর্জন করেছেন, অন্যদিকে ‘অভিভাবকহীন’ বাংলার মুসলমান সমাজ সবার অলক্ষে একশ্রেণীর ধর্মান্ধের কুক্ষ কুক্ষিগত হলেন। বাংলা ভাষায় উচ্চ ও মধ্যশ্রেনীর মুসলমানদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে আবদুল লতিফ যেমন তাদের মাতৃভাষায় সংস্কৃতি চর্চার উদ্যোগকে বিনষ্ট করেছিলেন তেমনই সৃষ্টি করেছিলেন একটি বিচ্ছিন্নতার মনোভাবও। বদরুদ্দীন উমরের মতে, “উনিশ শতকে আবদুল লতিফের এই বিভ্রান্তিকর জাতিতত্ত্বের পরবর্তী সংস্করণ যে বিশ শতকের মহম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।”৪০ এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে হিন্দু উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে উনিশ শতকে যতখানি উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছিল, মুসলমানরা তা করতে সক্ষম হয় নি। এবং একই সঙ্গে ভারতবর্ষের মাটিকে, তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তাঁরা নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বলে মনে করতে পারেন নি। ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি আবদুল রসুল — “অতীতে বাংলার মুসলমানরা যে-দেশে থেকেছেন ও বড়ো হয়েছেন তার দিকে তাঁরা তাকান নি, তাকিয়েছেন ধর্মের দিকে।”৪১ সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলি এবং নবাব আবদুল লতিফের মতো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতারা চাইতেন যে, মুসলমানরা কংগ্রেসের থেকে দুরে থাকুক। বস্তুত, ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের আগে যখন রিসেপশন কমিটি থেকে মুসলমান প্রতিনিধি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হল তার প্রতিক্রিয়ায় সৈয়দ আহমদ খান আলীগড় মুসলিম গেজেট-এর ২৩শে নভেম্বর, ১৮৮৬ সংখ্যায় কংগ্রেস আন্দোলনকে ‘রাজদ্রোহমূলক’ আখ্যা দিয়েছিলেন। পরের বছর ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয় বদরুদ্দীন তায়েবজিকে, ফলে কংগ্রেসে শিক্ষিত মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তাতে আশঙ্কিত হয়ে সৈয়দ আহমদ খান ১৮৮৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর একটি বক্তৃতায় হুঁশিয়ারি দিলেন, “কংগ্রেসকে সমর্থন করলে মুসলিমরা বিপর্যয় ডেকে আনবে।”৪২
বাংলাদেশে হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে নবজাগরণের সূচনা মোটামুটিভাবে বলা যায় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ মোটামুটিভাবে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। কলিকাতায় প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রামমোহন রায় লর্ড আর্মহার্স্টকে যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চিঠিখানি লেখেন, তাতে তিনি স্পষ্টভাবে সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্ধকারের হাতিয়ার বলে বর্ণনা করে এর পরিবর্তন চাইলেন, “… a more liberal and enlighted system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anantomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing a collage furnished with necessary books, instruments and other aperatures.”৪৩ পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই, কলকাতা মাদ্রাসা এবং হুগলী মহসীন কলেজে ১৮৩৫ সালে যখন ইংরেজিশিক্ষার পক্ষে বেন্টিংক-মেকলের নুতন নীতি প্রবর্তিত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে কলকাতার মুসলমানসমাজ তীব্র প্রতিবাদ করেন। আট হাজার মুসলমানের স্বাক্ষরসহ একটি প্রতিবাদপত্র গভর্নমেন্টের কাছে পাঠানো হল। আবদুল লতিফের মতো রক্ষণশীল সমাজপতিদের প্রবল বিরোধিতায় বাধ্য হয়ে সরকার ১৮৭২ সালে হুগলী কলেজ থেকে মহসীন তহবিল প্রত্যাহার করে নিয়ে সেই অর্থে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন করে এবং মুসলমান সমাজ সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল পশ্চাদমুখী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হল। সাধে কি আর বদরুদ্দীন উমর আক্ষেপ করে বলেছেন, “উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করার জন্য কোনও বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়নি।”৪৪ এর ফলটা কি দাঁড়ালো? বিনয় ঘোষের মতে কলকাতা মাদ্রাসা (ওয়েলসলি) থেকে হিন্দু কলেজ (কলেজ স্কোয়ার, গোলদিঘি) বেশি দুর নয় কিন্তু “১৮৫০ সালে যখন মাদ্রাসার ইংরেজ অধ্যক্ষকে মুসলমান ছাত্ররা ইটপাটকেল ও পচা ফল ছুঁড়ে মেরেছিলেন, তখন ওয়েলসলি থেকে গোলদিঘির দুরত্ব একটি যুগের দুরত্বে পরিণত হয়েছে বলা চলে।৪৫ ফলে একদিকে যেমন হিন্দুসমাজে ক্রমেই একটি শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সমাজের বিকাশ হয়েছে, অন্যদিকে মুসলমান সমাজে পুরানো অভিজাত সমাজ ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে এবং দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে এবং বিদ্বৎসমাজেরও বিকাশ হয়নি।
এরই সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে বসবাস করা অশিক্ষিত সুবৃহৎ মুসলমান সমাজের মধ্যেও এক ধরণের নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে (তাছাড়া কি-ই বা বলা যায়!) সেই আন্দোলনগুলি শিক্ষাকেন্দ্রিক না হয়ে, হয়ে উঠলো ধর্মকেন্দ্রিক। ফরাইজি আন্দোলন ছিল মাটির কাছাকাছি থাকা অগণিত মুসলমান কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের লড়াইয়ের আন্দোলন। ১৮৩০ সালে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন হাজি শরিয়াতুল্লাহ। প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ সরকারের কৃষিনীতি এবং জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু একই সঙ্গে শোষিত মুসলমানদের বলা হয়েছিল, অ-ইসলামি রীতিনীতি ত্যাগ করে ধর্মীয় কর্তব্য অনুসারে কাজ করতে। এর পরবর্তী দাদু মিঞা এবং ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের কৃষক আন্দোলনও শোষণের প্রতিবাদ করবার পাশাপাশি ইসলামের পবিত্রকরণের উপর জোর দিল। আন্দোলনকারীরা হিন্দুদের থেকে গ্রহণ করা রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলো। পিটার হার্ডির মতে, “The Muslim reform movements of the nineteenth century helped to transform Muslim attitude towards Hindu. They were essentially rejections of medieval Islam in India in favour of early Islam in Arabia. … Muslims in India were to be made aware of what they did not share with their non-Muslim neighbours. India could br made by the reformers to feel not like a home, but like a habitat. [৪৬] এই ধরণের প্রচার ও আন্দোলন অনায়াসে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় রূপান্তরিত হতে পারতো কারণ, শোষক জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং শোষিত কৃষকরা মুসলমান; কিন্তু হয়নি এই কারণেই যে তিতুমীর শোষক মুসলমান জমিদারদেরও রেয়াত করে চলতেন না। হান্টার সাহেব লিখেছেন, “In the peasant rising around Calcutta in 1831, they broke into the houses of Musalman and Hindu landholders with perfect impartiality. Indeed, the Muhammadan proprietors had rather the worst of it, as tge banditti sometimes gave salvation to the daughter of an erring co-religionist by forcibly carrying her off, and appropriating her to one of the robber chiefs.” [৪৭] তবে মুল ক্ষতিটা যা হওয়ার তা হয়ে গেল, জানিয়েছেন যশোবন্ত সিংহ — “… এই ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ফলে ক্রমশ একটি শাণিত, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, সাম্প্রদায়িক বাগরীতি তৈরি হল। সেই সঙ্গে এই আন্দোলনগুলি পতনোন্মুখ উচ্চশ্রেণীর মুসলিম সংস্কৃতিকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলল। কবিতা, চিত্রাঙ্কন, সূক্ষ্ণ অনুভুতিগুলির চর্চা, উচ্চবিত্ত নাগরিক ভদ্রলোকের ‘সোনালি দিনগুলি’, যত কিছু সুখস্মৃতি, সবই ধর্মীয় সংস্কারের কঠোরতার আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল …।”৪৮
একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না, ‘বঙ্গদেশে কৃষক’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার কৃষক পরান মন্ধল ও হাসিম শেখদের নিয়ে প্রচুর অশ্রুবিষর্জন করলেও এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন নেপাল মজুমদার — “… বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য ‘বঙ্গদেশে কৃষক’এ, ‘পরান মন্ডলদের’ দেখা গেলেও তাঁর উপন্যাস ও গল্পে ‘পরান মন্ডলদের’ কোনো চরিত্র-চিত্রণ দেখা যায় না।”৪৯ দেখা যায় না হাসিম শেখদেরও।
(পাঁচ)
সত্যি কথা বলতে কি, এই সমস্ত ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে সাহিত্যজগতে সেই সময়টা ছিল এক উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগ। অর্ধেক ইতিহাস এবং অর্ধেক কল্পনা মিলিয়ে একের পর এক বীরত্বব্যাঞ্জক কবিতা ও উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পরবর্তীকালে (১৯২৭) ‘কালান্তর’ প্রবন্ধগুচ্ছের অন্তর্গত ‘বৃহত্তর ভারত’ প্রবন্ধে দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন, বাল্যকালে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক কাহিনী পড়তে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “তখন আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ করে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বারবার কিরকম পরাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিন ক্ষণ তারিখ ও নামমালা — সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি। এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত। সকলেই জানেন, সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কিরকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কিরকম উপবাসী হয়ে ছিল।”৫০
এমন একটি যুগে অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ‘বউঠাকুরানীর হাট’ লিখতে আরম্ভ করলেন। সেই উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগে প্রতাপাদিত্যের বীরগাথা না গেয়ে নিজের উপন্যাসে তাঁকে নৃশংস দুরাচাররূপে দেখালেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৬৯ সালে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের রচিত ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ গ্রন্থখানি ছিল রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসের প্রেরণা। পরবর্তীকালে উপন্যাসটির ভুমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল । এখনো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তার সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্ৰহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য র্তার ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না । সে সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না । আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম। তখনো তার পূজা প্রচলিত হয় নি।”৫১ স্পষ্টতই, ইতিহাস থেকে জাতির বীরত্বের উদাহরণ খুঁজে বার করবার নামে রবীন্দ্রনাথ সত্য-মিথ্যে-কল্পনা মিশিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করেন নি। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, “বঙ্গাধিপে প্রতাপাদিত্য কুচরিত্র দুরাচার দস্যুরূপে বর্ণিত, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কেবল দুরাচার মূর্তিতে দেখাইয়াছেন।”৫২ ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে লিখিত রামরাম বসুর ‘রাজা প্রতাপাদিত্য’ এবং ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী প্রচারিত হয়। কিন্তু তাতে সত্য, মিথ্যা ও মিথ এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। কবি ভারতচন্দ্রও ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের গুণগান করে গেছেন। ঐতিহাসিক প্রভাসচন্দ্র সেনের মতে, “খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের ঘটনা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে জনশ্রুতিতে কিরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল, কবি ভারতচন্দ্রের বিবরণ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।”৫৩ আরএক বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার স্পষ্টভাবে লিখে গেছেন, “অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তাঁহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেরই কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।”৫৪ প্রভাসবাবু ও রমেশবাবুর বিবৃতি পড়লে রীতিমত শক লাগারই কথা কারণ বাল্যকাল থেকেই আমরা ইতিহাসে, গল্পে, নাটকে (এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বনফুলের সুবিখ্যাত ‘প্রতাপাদিত্য’ নাটকখানি) বাংলার বারো-ভূঁইয়ার অন্যতম প্রতাপের বীরত্বের যে আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা পড়েছি এবং শুনেছি তাতে এই বিবৃতি এক বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দেওয়ার মতো।
এই সময়েই বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন কাশিমবাজারের জমিদারের সভাপণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির মতো নেতারা যাঁরা হাঁচি-টিকটিকি প্রমুখ কুসংস্কারের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করতে আরম্ভ করলেন। বঙ্গবাসী পত্রিকা নিপুণ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কুৎসিতভাবে যাবতীয় প্রগতির বিরোধিতা করে চলেছিল। সেই সময়ে বঙ্গের অনেক বুদ্ধিজীবীই বঙ্গবাসী পত্রিকার এই ধরণের প্রগতিবিরোধী মতামতকে সমর্থন করতেন — কবি নবীনচন্দ্র সেন একবার লিখেছিলেন, “পূজার্হ রামমোহন রায়ের মত ‘বঙ্গবাসী’-ও আর একবার দেশরক্ষা করিয়াছে। আমরা যেরূপ ইংরাজী সভ্যতার স্রোতে বিজাতীয় পথে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, ‘বঙ্গবাসী’ চাবুক পিটাইয়া তাহার গতি কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ করিয়াছে।”৫৫
ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সংকট আসে তার প্রতিক্রিয়াতে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর ব্রিটিশ ভক্তিতে ছেদ পড়ে। এর ফলস্বরূপ একদিকে শিক্ষিত বাঙালীর একাংশ যেমন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং জাতীয় কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করেন, অন্য অংশটি স্বজাতির অতীত গৌরব পুনরাবিস্কারের মাধ্যমে দেশের সম্মান বাড়ানোর প্রচেষ্টা করেন। এ কাজে এগিয়ে আসেন হিন্দুরাই কারণ আমরা আগেই দেখেছি, জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠার জন্য যে ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, মুসলমানরা তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কাজেই একেবারে গোড়া থেকেই বাংলাদেশের স্বাদেশিকতা মূলত হিন্দু স্বাদেশিকতার রূপ পেয়েছিল – তা সে হিন্দুমেলাই বলুন অথবা বঙ্কিমচন্দ্রই বলুন। উভয়ক্ষেত্রেই স্বদেশপ্রীতি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই হিন্দু পুনরুত্থান ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে যে কতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে তা অনুধাবন করেছিলেন লর্ড কার্জন, ১৮৯৯ সালে। ২৬ জুলাই জার্মান অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে লেখা এক চিঠিতে কার্জন লিখেছিলেন, “There is no doubt that a sort of quasi-religious, quasimetaphysical ferment is going on in India, strongly conservative and even reactionary in its general tendency. The ancient philosophies are being re-exploited, and their modern scribes and professors are increasing in numbers and fame. What is to come out of this strange amalgam of superstition, transcendentalism, mental exaltation, and intellectual obscurity – with European ideas thrown as an outside ingredient into the crucible – wo can say?”৫৬ বঙ্গভঙ্গ সহ একাধিক জনবিরোধী প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কার্জন যতোই নিন্দিত হন না কেন, তাঁর এই মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য।
আমরা দেখতে পাই, উগ্র হিন্দুয়ানি, যা প্রাচীন ঐতিহ্যের নামে কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসকে তোল্লাই দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বারবার শ্লেষে ফেটে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্যাটায়ারে রবীন্দ্রনাথ কি রূঢ়, ভয়ঙ্কর ও তীব্র তা ‘শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু’ এই ব্যঙ্গকবিতাটি পাঠ করলে বোঝা যায়। কবিতাটি ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে প্রাথমিক উগ্রতা কমলে কাব্যগ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতাটি বাদ পড়ে। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করেছি —
“দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে !
(আমার দামু আমার চামু !)
কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই !
সাত-রাজার-ধন মানিক ছেলের
মুখে ফুটছে খই!
(আমার দামু আমার চামু !)
দামু ছিল একরত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এতই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু !)
দামু বলেন ‘দাদা আমার’
চামু বলেন ‘ভাই’,
আমাদের দোঁহাকার মতো
ত্রিভুবনে নাই!
(আমার দামু আমার চামু !)
গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম !
(দামু আমার চামু !)
দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু,
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু।
(দামু আমার চামু !)
রব উঠেছে ভারতভূমে
হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন
ভয় নেইক আর।
(ওরে দামু ওরে চামু !)
লিখচে দোঁহে হিন্দুশাস্ত্র
এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যেকথা
চামু দিচ্ছে গাল।
(হায় দামু হায় চামু !)
এমন হিঁদু মিলবে না রে
সকল হিঁদুর সেরা,
বোস বংশ আর্য বংশ
সেই বংশের এরা।
(বোস দামু বোস চামু !)
কলির শেষে প্রজাপতি
তুলেছিলেন হাই,
সুরসুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন
আর্য দুটি ভাই।
(আর্য দামু আর্য চামু !)
দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলচে
হিঁদুশাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে
বাজার হুলুস্থুল।
(দামু চামু অবতার !)
মেড়ার মতো লড়াই করে
লেজের দিকটা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর
হিঁদুয়ানির খোঁটা।
(আমার হিঁদু দামু চামু !)
দামু চামু কেঁদে আকুল
কোথায় হিঁদুয়ানি !
ট্যাঁকে আছে, গোঁজ যেথায়
সিকি দুয়ানি !
(খোলের মধ্যে হিঁদুয়ানি !)
দামু চামু ফুলে উঠল
হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন
বেড়ায় নেচে নেচে !
(ষেটের বাছা দামু চামু !)
আদর পেয়ে নাদুস নুদুস
আহার করছে কসে,
তরিবৎটা শিখলে নাকো
বাপের শিক্ষাদোষে !
(ওরে দামু চামু!)
এসো বাপু কানটি নিয়ে,
শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু !)
পড়াশুনো করো, ছাড়ো
শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে ঘষে তোল্ রে বাপু
স্বভাব চাষাড়ে।
(ও দামু ও চামু!)
ভদ্রলোকের মান রেখে চল
ভদ্র বলবে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা
জেনে ফেলবে লোকে !
(হায় দামু হায় চামু!)
পয়সা চাও তো পয়সা দেব
থাকো সাধুপথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ
যাবৎ ন ভাষতে !”
(হে দামু হে চামু !)”৫৭
১লা চৈত্র ১২৯২, কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকায়। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের যুগে ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বসু এবং লেখক চন্দ্রনাথ বসু নিপুণ ও প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে কুৎসিতভাবে হিন্দু সমাজের সব রকমের প্রগতির, বিশেষত নারীসমাজ ও নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। তারই জবাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এই কবিতাটির মাধ্যমে। অনেকে মনে করেন যোগেশচন্দ্র-চন্দ্রনাথই এই কবিতার দামু-চামু। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর স্বভাবের বাইরে গিয়েই এই তীব্র শ্লেষাত্মক কবিতাটি রচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদককে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর এই আক্রমণের ব্যাখ্যা দিয়ে লেখেন — বাল্যবিবাহ লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার প্রথম বাদ-প্রতিবাদ হয়। সে আজ বছর দুই-তিন পূর্বের কথা। ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলি নাই। … তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে আমার কখনোই রুচি হইত না। … আপনি লিখিয়াছেন মানিলাম ‘চন্দ্রনাথবাবুর মতই অপ্রামণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই এক কথা একবার বলিয়াই তো রবীন্দ্রনাথবাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন কী? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথবাবু নিজের ভ্রান্ত মতসমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথবাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।’ মার্জনা করিবেন, আপনার এই কথাগুলি নিতান্ত কলহের মতো শুনিতে হইয়াছে, ইহার ভালোরূপ অর্থ নাই। … আপনি একটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, নিজের মত যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান না করা যায় তবে পৃথিবীতে কেহ কোনো কথা বলিতে পারে না। অবশ্য, কেন সত্য জ্ঞান করি তাহার প্রমাণ দিবার ভার আমার উপর। যদি আমার মত প্রচারদ্বারা পৃথিবীর কোনো উপকার প্রত্যাশা করি, এবং বিরুদ্ধ মতের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায় তবে যতক্ষণ প্রমাণ দেখাইতে পারিব ততক্ষণ নিজের মত প্রচার করিব ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিব ইহা আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য। এ কার্য যদি বারংবার করার আবশ্যক হয় তবে বারংবারই করিতে হইবে। কবে পৃথিবীতে এক কথায় সমস্ত কার্য হইয়া গিয়াছে? কোন্ বদ্ধমূল ভ্রমের মূলে সহস্রবার কুঠারাঘাত করিতে হয় নাই?”৫৮ সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের শেষ কটি লাইন অসংখ্য মুক্তমনা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মনের কথা।
হিন্দু পুনরুজ্জীবনের জিগিরে তৎকালীন বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রগতিবিরোধী মতামত সমর্থন করতেন ; “বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত” উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ সেই গোষ্ঠীর কথা বলতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ। আরেকজন পুনরুত্থান পন্থী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘আর্য ও অনার্য’ শীর্ষক রঙ্গরসাত্মক নাটিকাখানি যেখানে আমরা দেখতে পাই চিন্তামণি কুণ্ডু নামের একটি চরিত্রকে যিনি নিজেকে আর্য হিসেবে দাবী করে যাবতীয় কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, ঠিক আজকালকার কতিপয় রাজনৈতিক নেতার মতো। নাটিকাটির কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ পড়া যাক — “এখনো আর্যবংশীয়েরা তেল মাখার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে ভূমিতে তিন বার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন? … আমাদের আর্যেরা কী বলেন? প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণশক্তির উত্তেজনা হয় — এই তো ম্যাগ্নেটিজ্ম্। … হাই তোলবার সময় তুড়ি দেওয়া কেন? সেও ম্যাগ্নেটিজ্ম্। উত্তানবায়ুর সঙ্গে আধানশক্তির যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরিচালিত নিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ এই তিনটেকে অতিক্রম করতে থাকে তখন সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রমদশা ঘটে। এমন সময়ে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণ-জনিত বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবদেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না। একে বিজ্ঞান বলে না তো কাকে বিজ্ঞান বলে? … মাটিতে পাখা ঠোকার বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো সেও ম্যাগ্নেটিজ্ম্! সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ, বিপ্রকর্ষণ এবং নিকর্ষণ এই ক’টা ভৌতিক ক্রিয়ার যোগে — … উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতির হুঁকোয় তামাক খায় না কেন? এক জাতি আর-এক জাতির স্পৃষ্ঠ অন্ন খায় না কেন? আগে আর্য অনার্যের ছায়া মাড়াতেন না কেন? তার মধ্যে কি বিজ্ঞান নেই? অবশ্য আছে। আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেও ম্যাগ্নেটিজ্ম্। উত্তম মধ্যম এবং অধম এই তিন প্রকার দেহজ বিকিরণশক্তি”৫৯ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১২৯০ বঙ্গাব্দ (১৮৮৩) ‘কৃষ্ণানন্দ’ নাম নিয়ে জবরদস্ত তন্ত্রসাধনা আরম্ভ করেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, নিজেকে ‘কল্কি অবতার’ বলে ঘোষণাও করেছিলেন। কৃষ্ণানন্দের চেলাদের মধ্যে ছিল অসংখ্য তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালী ! এনাকে বিদ্রুপ করে প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছিলেন,
“ক্ষুদে ক্ষুদে ‘আর্য্য’গুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তারা বলেন ‘আমিই কল্কি’ গাঁজার কল্কি হবে বুঝি !
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি।
পাড়ায় এখন কত আছে কত কব তার,
বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা-অবতার !
দাঁতের জোরে হিন্দু শাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে।,
দাঁতকপাটি লাগে, তাদের দাঁত-খিঁচুনীর ভঙ্গী দেখে !”৬০
শশধর তর্কচুড়ামণির মতো পুনরুজ্জীবনবাদীকে বিদ্রুপ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘প্রত্নতত্ত্ব’ প্রবন্ধটি যাতে জনৈক মধুসূদন শাস্ত্রীর বচনে পুনরুজ্জীবনবাদীদের বক্তব্য তুলে ধরে তাকে তীব্র শ্লেষাত্মক কষাঘাত করা হয়েছে। বক্তব্যগুলি ঠিক এখনকার কিছু নেতার মতো — “আমাদের দেশে যে এক কালে গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেন বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ভাই বাঙালি, এ কথা তুমি বিশ্বাস করিবে কেন? তাহা হইলে তোমার এমন দশা হইবে কেন? আজ যে তুমি লাঞ্ছিত, গঞ্জিত, তিরস্কৃত, পরপদানত, অন্নবস্ত্রহীন, দাসানুদাস ভিক্ষুক, জগতে তোমার এমন অবস্থা হয় কেন? … আমি বিশ্বাস করি প্রাচীন ভারতে গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল এবং অক্সিজেন বাষ্পের অস্তিত্বও অবিদিত ছিল না। কেন বিশ্বাস করি? আগে নিষ্ঠার সহিত কূর্ম কল্কি ও স্কন্দ পুরাণ পাঠ করো, গো এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি স্থাপন করো, ম্লেচ্ছের অন্ন যদি খাইতে ইচ্ছা হয় তো গোপনে খাইয়া সমাজে অস্বীকার করো, যতটুকু নব্য শিক্ষা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও, তবে বুঝিতে পারিবে কেন বিশ্বাস করি। … তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, কীটে যতটা খাইয়াছে এবং মুসলমানে যতটা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার কি একটা হিসাব আছে! যে পাপিষ্ঠ যবন ভারতের পবিত্র স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে, ভারতের গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারির প্রতি যে তাহারা মমতা প্রর্দশন করিবে ইহাও কি সম্ভব! যে ম্লেচ্ছগণ শত শত আর্যসন্তানের পবিত্র মস্তক উষ্ণীষ ও শিখা-সমেত উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা যে আমাদের পবিত্র দেবভাষা হইতে অক্সিজেন বাষ্পটুকু উড়াইয়া দিবে ইহাতে কিছু বিচিত্র আছে? … এই তো গেল প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যদি যবনগণের দ্বারাই গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের প্রাচীন নাম লোপ না হইবে, তবে তাহা গেল কোথায়–তবে কোথাও তাহার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না কেন? প্রাচীন শাস্ত্রে এত শত ঋষি-মুনির নাম আছে, তন্মধ্যে গল্বন ঋষির নাম বহু গবেষণাতেও পাওয়া যায় না কেন? যে পবিত্র ভারতে দধীচি বজ্রনির্মানের জন্য নিজ অস্থি ইন্দ্রকে দান করিয়াছেন, ভীমসেন গদাঘাতের দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছেন এবং জহ্নুমুনি গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে পান করিয়া জানু দিয়া নিঃসারিত করিয়াছেন, যে ভারতে ঋষিবাক্যপালনের জন্য বিন্ধ্যপর্বত আজিও নতশির, সেই ভারতের সাহিত্য হইতে অক্সিজেন বাষ্পের নাম পর্যন্ত যে লুপ্ত হইয়াছে, সর্বসংহারক যবনের উপদ্রবই যদি তাহার কারণ না হয়, তবে হে বাঙালি, তাহার কী কারণ আছে জিজ্ঞাসা করি। … তৃতীয় যুক্তি এই যে, ইতিহাসের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, যবনেরা প্রাচীন ভারতের বহুতর কীর্তি লোপ করিয়াছে। এ কথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজ যে আমরা নিন্দিত অপমানিত ভীত ত্রস্ত ভয়গ্রস্ত রিক্তহস্ত অস্তংগমিতমহিমা পরাধীন হইয়াছি, ভারতে যবনাধিকারই তাহার একমাত্র কারণ। এতটা দূরই যদি স্বীকার করিতে পারিলাম, তবে আমাদের গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের নামও যে সেই দুরাত্মারাই লোপ করিয়াছে এটুকু যোগ করিয়া দিতে কুন্ঠিত হইবার তিলমাত্র কারণ দেখি না। … চতুর্থ যুক্তি, যখন এক সময়ে যবন ভারত অধিকার করিয়াছিল এবং নির্বিচারে বহুতর পূত মস্তক ও মন্দিরচূড়া ভগ্ন করিয়াছিল, যখন অনায়াসে যবনের স্কন্ধে সমস্ত দোষারোপ করা যাইতে পারে এবং সেজন্য কেহ লাইবেলের মকদ্দমা আনিবে না, তখন যে ব্যক্তি সভ্যতার কোনো উপকরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের দৈন্য স্বীকার করে সে পাষণ্ড, হৃদয়হীন, বিকৃতমস্তিষ্ক এবং স্বদেশদ্রোহী ! … এমন যুক্তি আমরা আরও অনেক দিতে পারি। কিন্তু আমরা হিন্দু, পৃথিবীতে আমাদের মতো উদার, আমাদের মতো সহিষ্ণু জাতি আর নাই। আমরা পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।”৬১ প্রিয় পাঠকপাঠিকা, ১২৯৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের বলা এই কথাগুলি আজ একশোত্রিশ বছর পরেও হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির কল্যাণে কি প্রাসঙ্গিক!
(ছয়)
এর পরেও ১৯০৪ সালে (১১ ভাদ্র, ১৩১১) রবীন্দ্রনাথ গাইলেন শিবাজীর জয়গান! উনবিংশ শতকের শেষ দশকে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে এক নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সার্বজনীন গণপতি উৎসব প্রচলনের ভিতর দিয়ে। দশদিন ধরে চলা এই উৎসবে তিলক মারাঠা জাতির অতীত গৌরবময় দিনগুলি স্মরণ করা এবং শিবাজী মহারাজের বিভিন্ন কীর্তিকলাপ, ধর্মপ্রীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করতেন। তিলকের রাজনৈতিক চরিতকার স্ট্যানলি ওলপার্ট মন্তব্য করেছেন, “Ironically enough Tilak predicted that the Ganapati festival ‘will more or less aid in Society’s currant tendency to function more harmoniously.’ By ‘society’ he meant Hindu society alone. In sponsoring the Ganapati festival he was in fact furthering his ambition of providing an institutional framework to which to channe regularly the mass of orthodox opinion heretofore awakened only intermittently.”৬২ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে (১৮৯৩) তিলক ‘গোরক্ষণী সভা’ আন্দোলন অর্থাৎ গোরক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কারকে জাগিয়ে তুলে তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে চাইলেন। নেপাল মজুমদারের মতে, “বলা বাহুল্য, — এই গোরক্ষা আন্দোলন রাজনীতিবিদদের চোখে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া বিবেচিত হইবে কিন্তু ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে সে যুগে এটাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই অংশ বলে গণ্য করতে হবে।”৬৩ গোরক্ষিণী সমিতির বাড়াবাড়িতে এমনকি পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের মতো তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল ব্যক্তিত্বও ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গোরক্ষা প্রচার সমিতির প্রচারকের কথা শুনে বিরক্তভরে বলে ওঠেন, “হাঁ গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি — তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করিবেন?”৬৪ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বোম্বাই বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সৃষ্টি হল। ১৮৯৩ সালের আগস্ট মাসে বোম্বাইতে ঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য বোম্বাই এর ইংরেজ গভর্ণর গােরক্ষণী সভার অত্যুৎসাহী সদস্যদের বাড়াবাড়িকেই দায়ী করেছিলেন।
এরই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ‘ইংরেজের আতঙ্ক’ প্রবন্ধে লিখলেন, “ইতিমধ্যে ইংরাজের ভারতশাসনক্ষেত্রে আর-একটা নূতন ভয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেটা আর কিছু নয়, গোরক্ষণী সভা। যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভাটা স্থাপন করা হইয়াছে তাহারা যতটা নিরীহ, সভাটাকে ততটা নিরীহ বলিয়া ইংরাজের ধারণা হইল না। কারণ, ইংরাজ ইহা বুঝিয়াছে যে স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য যে-হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতি রক্ষার জন্য চাইকি তাহারা এক হইতেও পারে। স্বাধীনতা স্বদেশ আত্মসন্মান মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোরুকে রক্ষা করা যে আমাদের পরমতর কর্তব্য, এ-কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে। গোহত্যা-নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত একমত।”৬৫ সমস্ত প্রবন্ধটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, গো-রক্ষা আন্দোলন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনও আগ্রহ অথবা সহানুভূতি নেই বরং এই আন্দোলনের বাহানাতে ব্রিটিশ সরকার যে সব অপকৌশল অবলম্বন করেছিল, তিনি তারই সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এর পরেও কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। যে রবীন্দ্রনাথ ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে নিখিলেশের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, “এদেশে মহিষেও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুও মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠেনিময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।”৬৬ সেই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাঁর রাজনৈতিক চরিতকার নেপাল মজুমদার অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেছেন, “… গোরক্ষার মতো একটি কুসংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া যখন হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্ররোচিত এবং উত্তেজিত হইতেছে, এবং যে সময়ে নাকি হিন্দু-মুসলিম জাতীয় ঐক্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচিত হইতেছে, তখনও তিনি ইহার প্রতিবাদ করিলেন না।”৬৭ অথচ আমরা আগেই দেখলাম, এই জাতীয় ধর্মীয় কুসংস্কারজনিত প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই শাণিত যুক্তি দ্বারা কেটেছেন। নেপালবাবুর মতে, তিলকের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবশতই রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সমালোচনা করেননি।
এইভাবে ধর্মীয় মেরুকরনের যে কাজটি তিলক শুরু করেছিরেন, তাকে সম্পূর্ণতা দিতেই ১৮৯৫ সালে রায়গড়ে তিনি প্রবর্তন করলেন শিবাজী উৎসব। লক্ষ্য ছিল, মারাঠা বীর শিবাজীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা — স্পষ্টতই, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে তিলক ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই কল্পনা করেছিলেন। জাতীয় ঐক্য আর হিন্দুর ঐক্য ছিল তিলকের কাছে সমার্থক। শিবাজিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবেই দেখেছিলেন তিলক — “The people of no other country in the world would have forgotten the great man who laid the foundation of our empire, who upheld our self respect as Hindus, and who gave particular direction to our religion.”৬৮ তাই পরবর্তীকালে তিনি যখন বলেন, “The Shivaji festival is not celebrated to alienate or even to irritate the Mahomedane. Times are changed, and, as we observed above, the Mahomedans and the Hindus stand in the same boat or on the same platform so far as the political condition of the people is concerned. Can we not both of us derive some inspiration from the life of Shivaji under these circumstances?”৬৯ তখন তাঁর এই আবেদন বস্তুত কুমিরের কান্নার মতো শোনায়!
তিলকের সম্বন্ধে একটি খুব লাগসই কথা বলেছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর ‘ভারতবর্ষ ও ইসলাম’ গ্রন্থে, “টিলকের অকপট জাতীয়তাবাদী সাধনাকে এক কথায় বলা যায় তীব্র দেশপ্রেমের সঙ্গে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সমীকরণ সম্পন্ন করার প্রাণান্ত প্রয়াস এবং এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত।”৭০ তিলক ঘোষণা করেছেন, স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার, কিন্তু ‘কেশরী’ পত্রিকার প্রবন্ধেই হোক বা বক্তৃতাতে, ‘স্বরাজ’ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ‘হিন্দু স্বরাজ’এর আদর্শকে, যেখানে অহিন্দুদের স্থান নেই। প্রথমে সার্বজনীন গণপতি উৎসব, তারপর গোরক্ষিণী সভা এবং অবশেষে শিবাজি উৎসব প্রবর্তনের ফল অচিরেই দেখা গেল, ১৮৯৫ সালে পুনাতে আয়োজিত কংগ্রেসের সম্মেলনে স্থানীয় মুসলমানরা যোগ দিলেন না, কারণ কংগ্রেসের হিন্দুদের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ততদিনে শিথিল হয়ে গেছে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে লিখেছেন, “ইহার জন্য দায়ী ছিলেন লোকমান্য টিলক।”৭১ সুরজিৎ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, “কংগ্রেসের ভিতর থেকেই যখন কোনও উদারপন্থী নেতা টিলককে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমালোচনা করেন তখন টিলক তার উত্তর দেন, ‘There was nothing wrong in providing a platform for the Hindus of all high and low classes to stand together and discharge a joint national duty.’ স্পষ্টতই টিলকের জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মবাদ।”৭২ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিনগুলি নিয়ে আলোচনাকালে তিলকের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমালোচনা করে মাইকেল এডওয়ার্ডস যথার্থই লিখেছিলেন, “Tilak had been first to recognise the power of religious feeling as a weapon against the British, Jinnah learned the lesson and turned it against Congress.”৭৩
যাইহোক, ১৯০৪ সালে সখারাম গণেশ দেউস্কর শিবাজী উৎসবকে বাংলায় প্রবর্তনে সক্রিয় হলেন। এই প্রসঙ্গে ‘জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে প্রফুল্লকুমার সরকার লিখেছেন, “১৯০৪ সালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা কলিকাতায় ‘শিবাজী উৎসব’। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নব জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে এই শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র-নেতা লােকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই উৎসবে যােগ দিবার জন্য পুণা হইতে কলিকাতায় আসেন। এই শিবাজী উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা। ছত্রপতি শিবাজী মোগলের দাসত্বমুক্ত যে স্বাধীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই আদর্শ জাতির সম্মুখে ধরিবার জন্য এই শিবাজী উৎসবের পরিকল্পনা হইয়াছিল।৭৪
সখারাম দেউস্কর ‘শিবাজীর দীক্ষা’ নামে একটি পুস্তিকা লিখলেন এবং এই দেউস্করেরই ব্যক্তিগত অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকাস্বরূপ ‘শিবাজী উৎসব‘ কবিতাটি লিখে দিলেন এবং উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হল, রবীন্দ্রনাথ তাতে কবিতাটি পাঠ করলেন। কবিতাটির শেষাংশে আছে —
“মারাঠার প্রান্ত হ’তে এক দিন তুমি ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা ব’লে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।
তোমার কৃপাণ -দীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগ-দিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।
মৃত্যু সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর মূরতি —
সমুন্নত ভালে
যে রাজ-কিরীট শোভে লুকাবে না তা’র দিব্য-জ্যোতি
কভু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর ল’য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।
সে-দিন শুনিনি কথা — আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি’ লবো।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি’ উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী’ বসন
দরিদ্রের বল।
‘এক-ধর্ম্ম-রাজ্য হবে এ ভারতে’ এ মহাবচন
করিব সম্বল।
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
‘জয়তু শিবাজি।’
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে আজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।”৭৫
প্রশ্ন একটাই, শিবাজি তথা মারাঠাজাতির গুণগান গাইবার আগে, “মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক সঙ্গে” চলবার আগে, রবীন্দ্রনাথের একবারও বাংলার নারীপুরুষের উপর করা মারাঠী বর্গিদের অকথ্য অত্যাচার আর ধর্ষণের কথা মনে পড়লো না? প্রসঙ্গক্রমে জানানো আবশ্যক যে, ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে জনৈক কবি, গঙ্গারাম বঙ্গে মারাঠা আক্রমণ নিয়ে একটি কাব্য লেখেন, যার নাম তিনি দেন ‘মারাঠা পুরাণ’, ভিন্নমতে ‘মহারাষ্ট্রা পুরাণ’। এই কবিতায় তিনি মুলত বঙ্গে ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণাবলীর বিবরণ দেন। ভাষাবিদ সুকুমার সেন লিখেছেন এই পুঁথিটি “বর্গীর হাঙ্গামার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ … আধুনিকপূর্ব বাংলা সাহিত্যে এইটিই একমাত্র ঐতিহাসিক কবিতা।”৭৬ ১২৪৯-৫০ বঙ্গাব্দে মারাঠা বর্গীদের বঙ্গ লুন্ঠন ও অবশেষে ভাস্কর পণ্ডিতের পরাভব ও নিধন এই কাব্যের উপজীব্য। বিপ্লব দাশগুপ্ত এই কাব্য থেকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, “কিভাবে মারাঠা আক্রমণ জনজীবন ও বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সাধারণ মানুষ কলার বিচি খেয়ে বেঁচে ছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সৈন্যের পিছনে যান এবং গ্রাম লুঠ করতে থাকেন। লোকে পালাতে শুরু করে; ব্রাহ্মণ তার বই নিয়ে পালায়, স্যাকরা তার মানদণ্ড নিয়ে, পটুয়া এবং কামাররা তাদের চক্র নিয়ে, জেলে তার জাল নিয়ে, মেয়েরা মাথায় একটা ঘোমটা দিয়ে, এবং রাজপুত ও ক্ষেত্রীরা তাদের তরোয়াল নিয়ে পালায়। … সর্বমোট চল্লিশ হাজার মানুষ এই আক্রমণে প্রাণ হারায়।”৭৭ শেষোক্ত বাক্যটি বিপ্লববাবু পি. জে. মার্শালের বই থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং প্রভাসচন্দ্র সেন লিখিত বঙ্গের ইতিহাসে আমরা বর্গীর যে অত্যাচারের বর্ণনা পাচ্ছি তাতে মৃতের সংখ্যা এর দশগুণ হলেও বিস্মিত হব না। রমেশবাবু তাঁর গ্রন্থে পূর্বোক্ত মারাঠা পুরাণ কাব্যের অনুবাদ থেকে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করে বর্গী অত্যাচারের যা বিবরণ দিয়েছেন তা পড়লে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়,
“মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া॥
কারূ হাত কাটে কারূ নাক কান।
একি চোটে কারে বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া যাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভয়ে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥”৭৮
সমসাময়িক ইংরেজ ও বাঙালী লেখকরা এই বিভৎস অত্যাচারের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তা চিরদিন মারাঠা জাতির কলঙ্কের বিষয় হয়ে থাকবে। আকবরউদ্দিন অনুবাদিত গোলাম হোসায়েন সলিম-এর ‘রিয়াজ-উস সালাতীন’ গ্রন্থে লেখা আছে, “গ্রাম শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ পুড়িয়ে, লোকজনকে হত্যা অথবা বন্দী করে, শস্যভাণ্ডারে আগুন দিয়ে মারাঠা দস্যুরা ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করেছিল। বর্ধমানের শস্যভাণ্ডার শেষ হলে এবং বাইরে থেকে শস্য সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অনাহারে মৃত্যু এড়াবার জন্য মানুষ কলাগাছের মূল, পশুপাল ও বৃক্ষপত্র খেতে লাগলো। … এই নরহন্তা দস্যুগণ বহু লোকের নাক, কান ও হাত কেটে নদীতে ডুবিয়ে মারে। অন্যদের মুখে আবর্জনার থলি বেঁধে, অঙ্গহানি করে অবর্ণনীয় অত্যাচারের পর তাদের পুড়িয়ে মারে। এইরূপে তারা বিরাট একটা অঞ্চলের অগণিত পরিবারের সন্মান নষ্ট করে এবং সমস্ত অঞ্চল জনশুন্য করে দেয়।”৭৯ ধারণা করা হয়, বাংলার প্রায় ৪,০০,০০০ অধিবাসী মারাঠা আক্রমণকারীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল। “Contemporary Dutch sources believed that the Bargis killed 4 lakh Bengalis and a great many merchants in western Bengal.”৮০ এছাড়াও বিপুলসংখ্যক নারী মারাঠাদের হাতে ধর্ষিত হয়। শেষপর্যন্ত আলীবর্দী খান ১৭৪৪ সালে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে কৌশলে হত্যা করে এবং পরবর্তীকালে ১৭৫১ সালে চৌথ বাবদ প্রতি বছর বারো লক্ষ টাকা রঘুজী ভোঁসলেকে দেওয়ার অঙ্গীকার করে বাংলাকে মারাঠা অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন।
আমরা বর্গিদের অত্যাচারের কথা শুনলাম। শিবাজী ১৬৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রথম সুরাট লুণ্ঠনের সময় যে নৃশংসতার নিদর্শন রেখেছেন তার তুলনাও কিন্তু ভারতের ইতিহাসে দুর্লভ। সুরাটের জনগণ প্রধানত ছিল শান্তিপ্রিয়, দুর্ব্বল এবং ভীরু, অধিকাংশই অহিংস জৈন, পারসী এবং হিন্দু গুজরাটি। শিবাজীর সুরাট আক্রমণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন, “মারাঠা অশ্বরোহিগণ অমনি অরক্ষিত অর্ধ জনশূন্য শহরে ঢুকিয়া বাড়ীঘর লুট করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। একদল শহরের মধ্য হইতে দুর্গের দেওয়াল লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল, ভয়ে দুর্গরক্ষী বীরগণ কেইই মাথা তুলিল না, বা শহরলুটে বাধা দিল না। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই চারিদিন ধরিয়া শহর অবাধে লুণ্ঠিত হইল। মারাঠারা প্রত্যহ নূতন নূতন পাড়ায় ঘর জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। সে সময় সুরতে পাকা বাড়ী দশ-বিশটার অধিক ছিল না, বাকী হাজার হাজার বাড়ীতে কাঠের খুঁটি, বাঁশের দেওয়াল, খড় বা খোলার চাল, এবং মাটির মেঝে। এ হেন স্থানে মারাঠাদের অগ্নিকাণ্ড সহজেই ‘রাত্রিকে দিনের মত উজ্জ্বল এবং ধুমবৃষ্টি দিনকে রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া তুলিল — সূর্যের মুখ ঢাকিয়া দিল।’ … মারাঠারা সুরতবাসীদের ধরিয়া আনিয়া কোথায় তাহারা নিজ নিজ ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার সন্ধানের জন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুর পীড়নই বাকী রাখিল না ; চাবুক মারা হইল, প্রাণ বধের ভয় দেখানো হইল, কাহারও এক হাত কাহারও বা দুই হাত কাটিয়া ফেলা হইল, এবং কতক লােকের প্রাণ পৰ্য্যন্ত লওয়া হইল। মিষ্টার এন্টনি স্মিথ (ইংরাজ-বণিক) স্বচক্ষে দেখিলেন যে, শিবাজীর শিবিরে একদিনে ছাব্বিশজনের মাথা এবং ত্রিশজনের হাত কাটিয়া ফেলা হইল ; বন্দীদের যে-কেহ যথেষ্ট টাকা দিতে পারিল না তাহার অঙ্গহানি বা প্রাণবধের আজ্ঞা হইল। শিবাজীর লুঠের প্রণালী এইরূপ, প্রত্যেক বাড়ী হইতে যাহা সম্ভব লইয়া, গৃহস্বামীকে বলা হইল যে যদি বাড়ী বাঁচাইতে চাও ত তাহার জন্য আরও কিছু দাও। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সেই টাকা আদায় হইল, অমনি নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ঘরগুলি পুড়াইয়া দিলেন।”৮১ জে. সি. দে রচিত ‘শিবাজী’জ সুরাট এক্সপিডিশন অফ ১৬৬৪’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে আমিনুল ইসলাম লিখেছেন, “যে তিনদিন শিবাজী সুরাট নগরে ছিলেন, সেই তিনদিন এমন কোনও পাশবিক কাজ নেই যা তাঁর দল করেনি। লুঠপাট, ঘরে আগুন দেওয়া, হাজার হাজার মানুষের হাত কেটে দেওয়া, মাথা কেটে দেওয়া, নারীদের ওপর চরম নির্যাতনে সুরাট অধিবাসীর কান্না যে কোনও মানুষকেই ব্যথিত করে তোলে।”৮২
“এক-ধর্ম্ম-রাজ্য” কি এতোটাই মহিমময়? রবীন্দ্রনাথ কি আদৌ বোঝেননি যে, শিবাজির বীরত্বের যে গাথা, তা তৈরি হয়েছে মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইএর জন্যেই এবং স্বভাবতই এই উৎসবে মুসলমান সম্প্রদায় যোগদান করবে না? আসলে কবি তখনও সনাতন বৈদিক ধর্মের আদলেই ভারতের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠবে — এই তত্ত্বে বিরাজমান। বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্মবান্ধবের মাধ্যমে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশে পরিপুষ্ট হয়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ তখনও তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি।
(সাত)
রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, একটু দেরীতে হলেও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে, “শিবাজী উৎসব আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবােধ হইতে উদ্ভূত ; শিবাজী মহারাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। সুতরাং শিবাজী সম্বন্ধে গৌরববোধ হিন্দুদেরই হওয়া সম্ভব, মুসলমানদের নহে; সুতরাং, বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর কোনও বীরকে অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথ বােধ হয় এই কবিতাটির দুর্বলতা কোনখানে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য তাঁহার কোনও কাব্যগ্রন্থে স্থান দেন নাই।”৮৩ একই কারণে তিনি সরলা দেবী প্রবর্তিত ‘প্রতাপাদিত্য উৎসব’-কেও বিন্দুমাত্র সমর্থন করেন নি। অচিরেই শিবাজী উৎসব ভবানীপূজার সঙ্গে সংযুক্ত হল ১৯০৬ সালের জুন মাসে এবং খুব শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করেন এমনকি একে “এক লক্ষ্মীছাড়া শিবাজী মেলা” বলেও অভিহিত করলেন।
তাই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে বসলে, এ কথাও মাথায় রাখতে হবে, ‘রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা’ প্রবন্ধে গোপাল হালদার যেমন বলেছেন — নবগোপাল মিত্র এবং বিশেষত রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ হিন্দু মেলার “উদ্যোক্তাদের নিকট ‘হিন্দু’ ও ‘ন্যাশনাল’ ছিল সমার্থক, আর ‘ভারতবর্ষীয়ত্ব’ অর্থ ‘হিন্দুত্ব’, …”৮৪ রবীন্দ্রনাথের কাছে তেমনটা আদৌ নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা তাঁর জীবনদর্শনের অঙ্গ, যার মুল বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রগতিশীলতা। বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী — “রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশিকতা ও হিন্দুত্ব নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহার ফলে তিনি যেমন ভুলিতে পারিতেন না যে, তিনি ভারত বা বাংলার সন্তান, তেমনই ইহাও ভুলিতে পারিতেন না যে, তিনি বাঙালী হিন্দু। কিন্তু তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ও হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। এই দিক হইতেই তাঁহার সহিত তাঁহার যুগের বাঙালীর মিল ছিল না, আরও বলিব, আজিকার বাঙালীর সঙ্গেও নাই ; কারণ এই — সাধারণ বাঙালীর, তা সেকালেরই হউক বা একালেরই হউক, দেশপ্রেম যত না দেশের প্রতি ভালবাসা তার চেয়ে অনেক বেশি ইংরেজ বিদ্বেষ; আর হিন্দুত্ব যত না উহার প্রতি শ্রদ্ধা তার চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান বিদ্বেষ ;”৮৫ তাই কোনও একটি-দুটি রচনাকে এবং ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়, ‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা-ই লিখেছেন — “আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। … রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি — জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।”৮৬ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুই-একটি ছোটখাটো চড়াই-উতরাই বাদে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিংশ শতকের প্রথম দশক হতে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবতাবাদের পথে উত্তরণ ঘটেছে, যা ক্রমেই পরিস্ফুট হয়েছে বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী দিনগুলিতে। সে কাহিনী না হয় অন্য পরিসরে বলা যাবে।
দ্বিতীয় পর্বের লিঙ্ক
https://www.itihasadda.in/hindumela-shivajiutsav-rabindranath-secularism-ii/
তথ্যসূত্র :
১) সত্তর বৎসর, বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৬৮
২) রাজনারায়ণ বসু : নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, দে বুক স্টোর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৫৭
৩) রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ৪৬
৪) রবিজীবনী প্রথম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৬৮
৫) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯
৬) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ১৯০৯,পৃষ্ঠা ২৫৮
৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৯২০, পৃষ্ঠা ১২৮
৮) প্রবাসী দ্বাবিংশ খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ সন ১৩২৯, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবাসী কার্যালয়, ১৯২২, পৃষ্ঠা ৩৬০
৯) জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৬
১০) সত্তর বৎসর, বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ২৬৮
১১) জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৭৮
১২) রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য নিকেতন, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৭৫
১৩) রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১২-১৩
১৪) সোমপ্রকাশ সপ্তদশ খণ্ড সন ১২৮১, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, ১৮৭৫, পৃষ্ঠা ২৩৪
১৫) রবিজীবনী প্রথম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১
১৬) রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৮-৯
১৬) জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স,
১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৮৭
১৭) রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬
১৮) চিঠিপত্র উনবিংশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৪
১৯) রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৫১৮-৫১৯
২০) ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড, নেপাল মজুমদার, সাহিত্য তীর্থ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৩২
২১) রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৪-২৫
২২) রাজনীতির রুদ্ধ দ্বার ও রবীন্দ্রনাথ, সন্দীপন সেন, অনুষ্টুপ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৫৪
২৩) রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩
২৪) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ১৯০৯, পৃষ্ঠা ৩০৮
২৫) সমকালে বিদ্যাসাগর, স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১১-১২
২৬) বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ১৫০
২৭) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৮
২৮) বাণী ও রচনা দশম খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৬১
২৯) বাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১৬১
৩০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৯
৩১) আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭, সুমিত সরকার, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬১
৩২) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩
৩৩) বাল গঙ্গাধর তিলক : হিজ রাইটিংস এ্যাণ্ড স্পিচেস, অরবিন্দ ঘোষ সংকলিত, গনেশ এ্যান্ড কো, ১৯১৮, পৃষ্ঠা ১৩-১৪
৩৪) নবযুগের বাংলা, বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭
৩৫) বঙ্কিম রচনাবলী প্রথম খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৭৮৭
৩৬) নবযুগের বাংলা, বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ২১৭
৩৭) আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭, সুমিত সরকার, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৭০-৭১
৩৮) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, বদরুদ্দীন উমর, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৫
৩৯) বাঙলা ভাষার শত্রু মিত্র, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৯
৪০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, বদরুদ্দীন উমর, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৫
৪১) রাজনীতির রুদ্ধ দ্বার ও রবীন্দ্রনাথ, সন্দীপন সেন, অনুষ্টুপ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৭
৪২) জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা, যশোবন্ত সিংহ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২০
৪৩) লাইফ এণ্ড লেটারস অফ রাজা রামমোহন রায়, সোফিয়া ডবসন সম্পাদিত, হেমচন্দ্র সরকার প্রকাশিত, ১৯১৪, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯
৪৪) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, বদরুদ্দীন উমর, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪৯
৪৫) বাংলার বিদ্বৎসমাজ, বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ২৪
৪৬) দ্য মুসলিমস অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, পিটার হার্ডি, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৫৯
৪৭) দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস, ডাবলু ডাবলু হান্টার, ট্রাবনার এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৮৭৬, পৃষ্ঠা ১০৯
৪৮) জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা, যশোবন্ত সিংহ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৩
৪৯) ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড, নেপাল মজুমদার, সাহিত্য তীর্থ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৪৩
৫০) রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্বিংশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ৩৬৮
৫১) রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ৩৭৪
৫২) রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ১৪৩
৫৩) বাঙলার ইতিহাস, প্রভাসচন্দ্র সেন, কথাশিল্প প্রকাশ, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ৩৩৩
৫৪) বাংলাদেশের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ১৩১
৫৫) রাজনীতির রুদ্ধ দ্বার ও রবীন্দ্রনাথ, সন্দীপন সেন, অনুষ্টুপ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৫২
৫৬) আত্মঘাতী বাঙালী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২২
৫৭) কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ চৌধুরী সম্পাদিত, পীপলস লাইব্রেরি, ১৮৮৬, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৭
৫৮) রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৭৩
৫৯) রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৭৩
৬০) রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪১, পৃষ্ঠা ৫১
৬১) রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৫০৮-৫১০
৬২) তিলক অ্যান্ড গোখলে : রিভোলিউশন অ্যান্ড রিফর্ম ইন মেকিং অফ মডার্ন ইন্ডিয়া, স্ট্যানলি ওলপার্ট, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৬৮
৬৩) ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড, নেপাল মজুমদার, সাহিত্য তীর্থ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৮৫
৬৪) বাণী ও রচনা নবম খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৯
৬৫) রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ৫৩৯
৬৬) রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্টম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪১, পৃষ্ঠা ২৯৪
৬৭) ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড, নেপাল মজুমদার, সাহিত্য তীর্থ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৮৮
৬৮) তিলক অ্যান্ড গোখলে : রিভোলিউশন অ্যান্ড রিফর্ম ইন মেকিং অফ মডার্ন ইন্ডিয়া, স্ট্যানলি ওলপার্ট, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৮০
৬৯) বাল গঙ্গাধর তিলক : হিজ রাইটিংস এ্যাণ্ড স্পিচেস, অরবিন্দ ঘোষ সংকলিত, গনেশ এ্যান্ড কো, ১৯১৮, পৃষ্ঠা ৪৯
৭০) ভারতবর্ষ ও ইসলাম, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, শঙ্কর প্রকাশন, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১৮২
৭১) রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ৩৭৭
৭২) ভারতবর্ষ ও ইসলাম, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, শঙ্কর প্রকাশন, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ২৩১
৭৩) দ্য লাস্ট ডেজ অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, মাইকেল এডওয়ার্ডস, ক্যাসেল অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ২৩০
৭৪) জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লকুমার সরকার, আনন্দ-হিন্দুস্তান প্রকাশনী, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ৪৪
৭৫) পূরবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯২৫, পৃষ্ঠা ২৪৩-২৪৪
৭৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৪৫০
৭৭) বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা : প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব, বিপ্লব দাশগুপ্ত, অরুণা প্রকাশন, ২০০০, পৃষ্ঠা ২৫৩-২৫৪
৭৮) বাংলাদেশের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ১৫০
৭৯) রিয়াজ-উস-সালাতীন, আকবরউদ্দিন অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৭০
৮০) ফরগটেন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি : দ্য ব্রুটাল মারাঠা ইনভেনসনস অফ বেঙ্গল, শোয়াইব ড্যানিয়েল, স্ক্রোল ডট ইন, ২১ ডিসেম্বর ২০১৫
৮১) শিবাজী, যদুনাথ সরকার, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯২৯, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৫
৮২) শিবাজী : একটি বিতর্কিত ঐতিহাসিক চরিত্রের অনুসন্ধান, আমিনুল ইসলাম, নবজাগরণ ডট কম, ১১ আগস্ট ২০২০
৮৩) রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ১২৭
৮৪) রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন, গোপাল হালদার সম্পাদিত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ১৩৫
৮৫) আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১০১
৮৬) রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্বিংশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ৪৩৭

গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে অনেক অজানা কথা চোখের সামনে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে, হিন্দুত্ব আর ধর্মনিরপেক্ষতায় রবীন্দ্রনাথথের মানসিক উত্তরণের চিত্রটিও ফুটে উঠেছে।লেখককে ধন্যবাদ।
শিবাজী উৎসব কবিতাটা পড়ে আমি খানিক হকচকিয়ে গেছিলুম যে রবীন্দ্রনাথ মারাঠা আক্রমণ সম্পর্কে কি কিছুই জানতেন না! এখন ওনার বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সমসাময়িক ঘটনাবলী জেনে বিষয়টা খোলসা হল। ধন্যবাদ লেখককে।