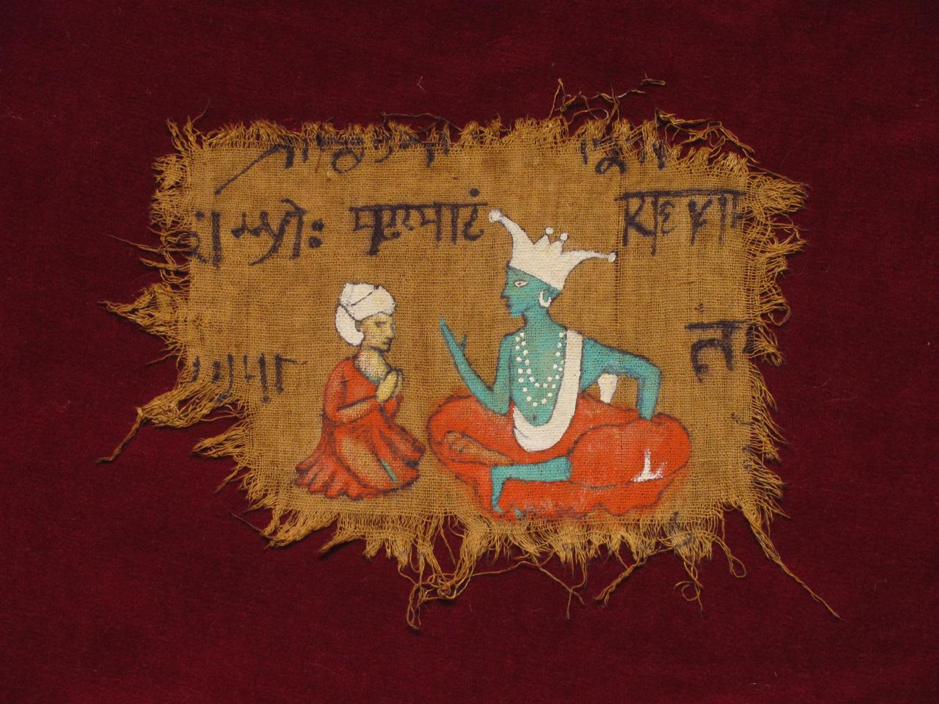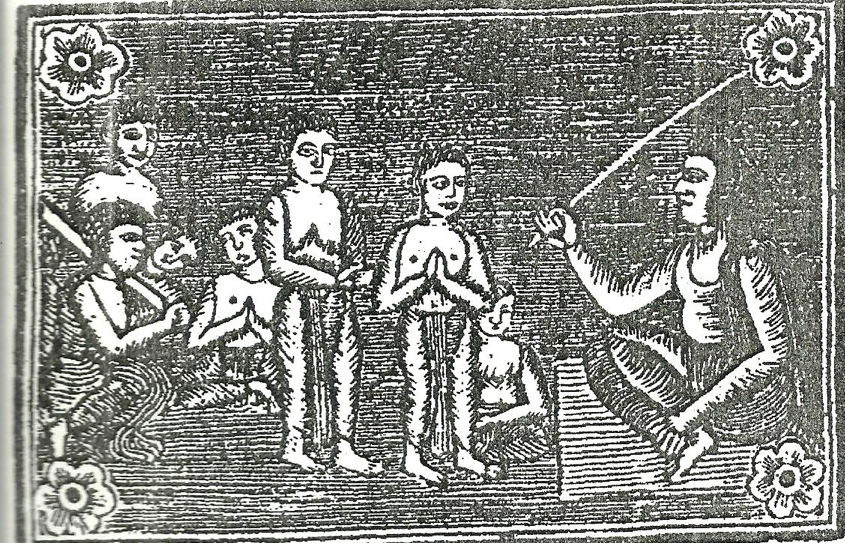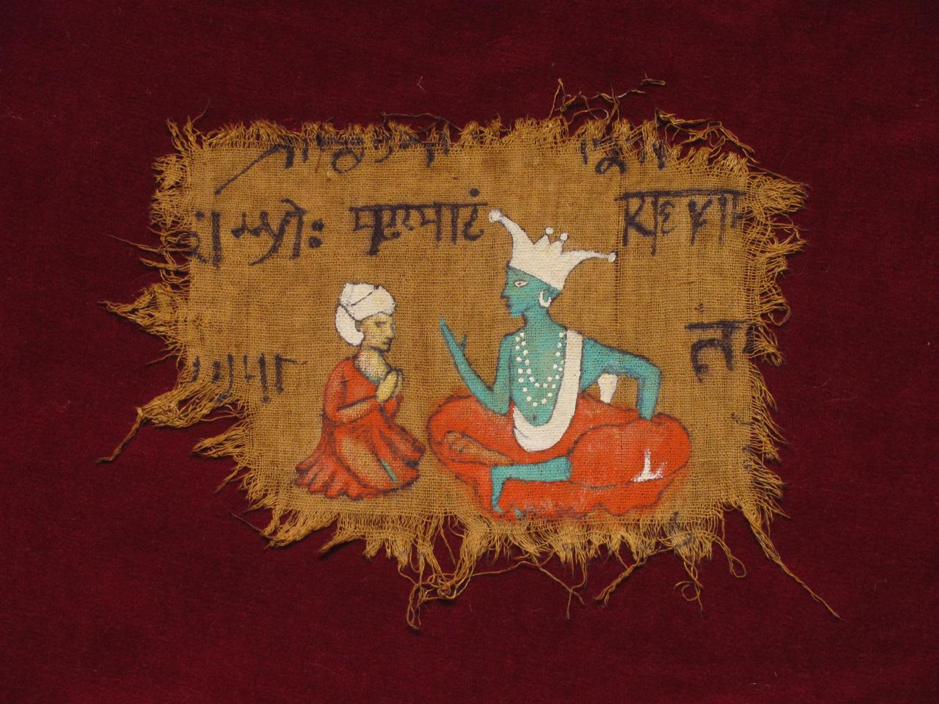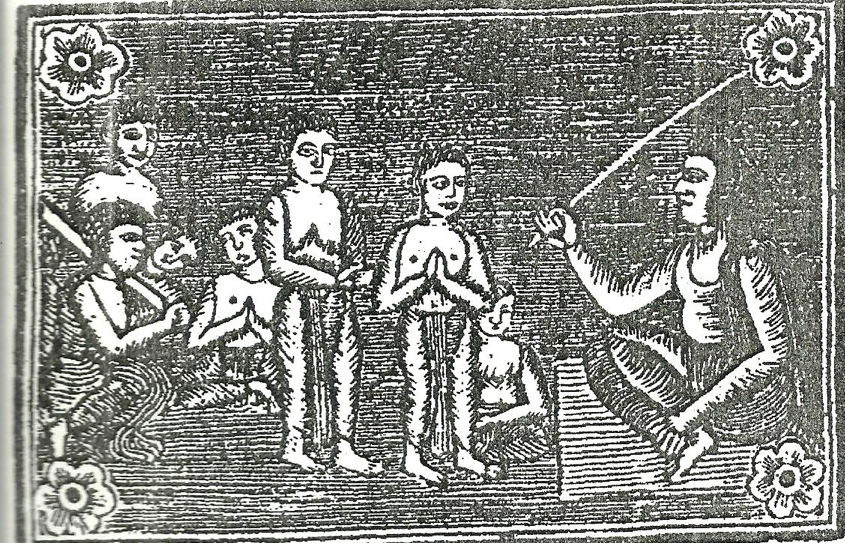‘না, না, না, ট্যাক্স না দিলে কোনও মতেই ছাড়া যাবে এগুলোকে’ ব’লে উঠেন হেডেন। হেডেন (পুরো নাম: Edward long Hedden ১৮২৮-১৮৯৩) তখন ন্যু ইয়র্ক জাহাজঘাটার ‘কন্ট্রোলার অব দ্য পোর্ট অব ন্যু ইয়র্ক' পদে কর্মরত ছিলেন। বন্দর দিয়ে আমদানিকৃত পণ্যর উপর ট্যাক্স সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর কাজ।
‘আরে ট্যাক্স তো আনাজের উপর ধার্য করেছেন সরকার। ফলের উপর আবার কিসের ট্যাক্স?’ প্রশ্ন করেন আনাজ ও ফল ব্যবসায়ী জন নিক্স। ঝানু ব্যবসায়ী নিক্স যে কিছু খবর রাখেন না তা নয়। ন্যু ইয়র্ক শহরের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান তখন। স্বাভাবিক ভাবেই জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে আনাজ ও ফলের চাহিদা। কিন্তু আনাজ বা ফলের সেই চাহিদার তুলনায় আনাজের জোগান কোথায়? শহরে আনাজ বা ফলের ঘাটতি দেখেই না ১৮৩৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন ‘জন নিক্স অ্যান্ড কো. ফ্রুট কমিশন’। বারমুডা, কিউবা, ফ্লোরিডা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে জাহাজে করে আনাজ আর ফল আমদানি করে বেশ দু’পয়সা কামিয়েও ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। ন্যু ইয়র্ক শহরে নিক্স অ্যান্ড কো.-এর ভালোই পসার তখন। শুধু নিক্সই নন, নিক্সের মতো আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী সস্তায় আনাজ আমদানি করে ভালোই পসার জমিয়েছেন শহরে। আর এটা যে কেবল ন্যু ইয়র্ক শহরের চিত্র তা নয়। দেশের বিভিন্ন শহরে আনাজ আমদানির ব্যবসা করে লক্ষ্মী লাভ করেছেন বেশ কিছু ব্যবসায়ী। এই ব্যবসাদারদের দাপটে আবার প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছেন না দেশি চাষিরা। লাভ তো পরের কথা, দেশের মাটিতে আনাজ উৎপাদন করতে যা ব্যয় করতে হচ্ছে তাঁদের, সেই টাকাটাই ফেরত পাচ্ছেন না তাঁরা। দেশের মাটিতে আনাজ চাষ আর লাভজনক নয় দেখে আনাজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন কিছু চাষি। কেউ কেউ পড়েছেন বিরাট লোকসানের মুখে। দেশি আনাজ বনাম বিদেশি আনাজের দ্বন্দ্ব তখন জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হতে শুরু করেছে। বিষয়টা নিয়ে সরগরম হতে শুরু করেছে রাজনীতির আঙিনা। সরকারও পড়েছেন চিন্তায়। দেশি চাষিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে তার প্রভাব পড়বে ভোট ব্যাঙ্কে। আর ঝুঁকি নেননি সরকার। দেশি চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় আনলেন নতুন আইন। ৩ মার্চ ১৮৮৩, ইউএস-এর প্রেসিডেন্ট (১৮৮১-১৮৮৫) চেস্টার আর্থার (পুরো নাম : Chester Alan Arthur ১৮২৯-১৮৮৬) সই করলেন নতুন আইন ‘ট্যারিফ অ্যাক্ট অব ১৮৮৩’তে। সেই আইন মোতাবেক, সমস্ত আমদানিকৃত আনাজের উপর বসল ১০% কর। তবে ছাড় দেওয়া হলো ফলের ক্ষেত্রে। ফল আমদানিতে নতুন কোনও ট্যাক্স চাপানো হলো না।
আমরা সবাই ছোটবেলায় বিদেশি লোক-কাহিনীর সেই ছোট্ট জঙ্গলবাসী মেয়ে রেড রাইডিং হুড-এর কথা পড়েছি, যাকে ধরে খাবে বলে বনের এক নেকড়ে চাদর মুড়ি দিয়ে তার ঠাকুমার রূপ ধরে তার কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়েছিল। ছোট্ট মেয়ে যখন জিজ্ঞেস করল, ও ঠাকুমা, তোমার দাঁতগুলো অত বড় বড় কেন গো, নেকড়ে তার উত্তরে বলেছিল, কেন হে, তোমাকে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবার পক্ষে সে তো ভালই হবে! ওই ছোট্ট মেয়ের পক্ষে মর্মান্তিক উত্তরই বটে। তবে কিনা, ঋষি অ্যারিস্টোটল ঘটনাটা জানতে পারলে হয়ত খুশি হয়ে নেকড়ে বাবাজির পিঠ চাপড়ে দিতেন, কারণ, সে অন্তত তার বড় বড় দাঁতগুলোর অস্তিত্বের একটা ‘উদ্দেশ্যমূলক কারণ’-এর কথা স্বীকার করেছে, জীবনকে অর্থহীন বলে মেনে নেয় নি। জগত-সংসারের মধ্যে অর্থ সরবরাহকারী এই রকম ‘উদ্দেশ্যমূলক কারণ’-কে অ্যারিস্টোটল যে নাম দিয়েছিলেন, আজকের দর্শনবেত্তারা ইংরিজিতে তার তর্জমা দাঁড় করিয়েছেন ‘ফাইনাল কজ’ --- বাংলায় হয়ত ‘পরমকারণ’-ও বলা চলতে পারে। অ্যারিস্টোটল বলতেন, সমস্ত ঘটনার পেছনে আমরা যে ‘কারণ’ খুঁজি, সেই ‘কারণ’ আসলে চার রকমের ............