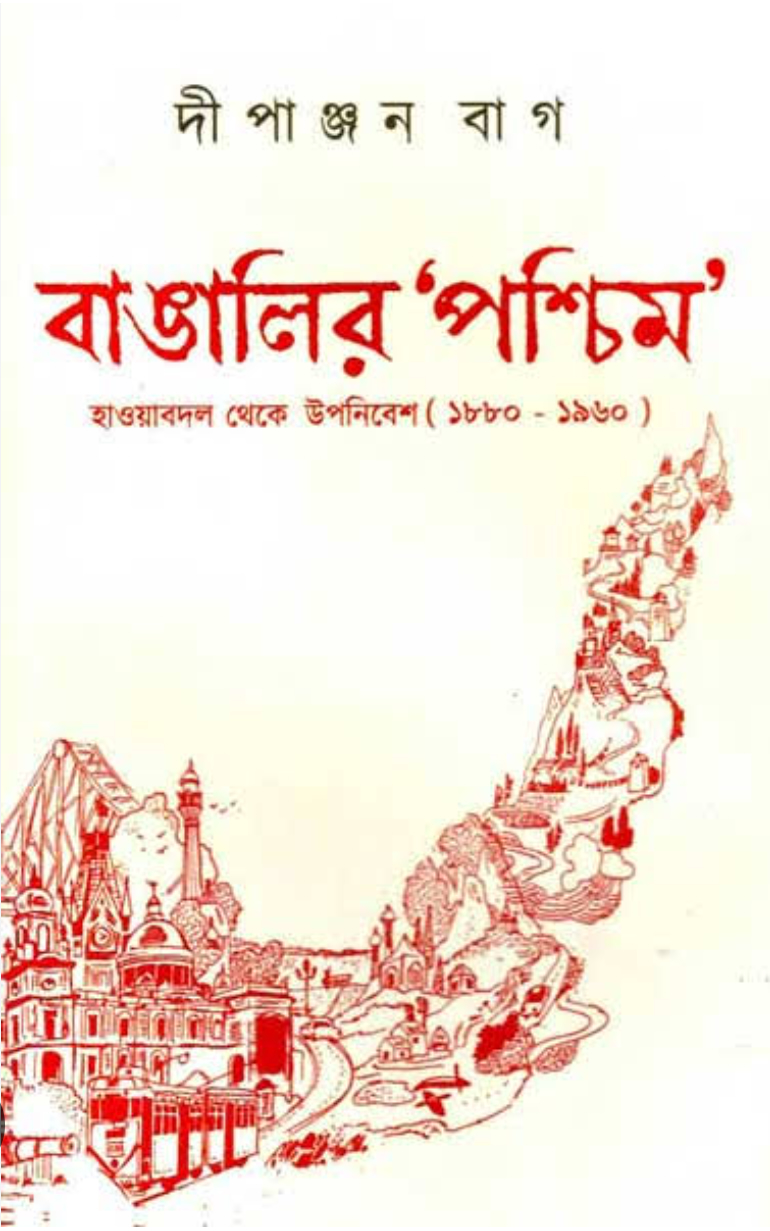
বাঙালির ‘পশ্চিম’ দর্শন ও যাপন
(গ্রন্থ নাম: বাঙালির ‘ পশ্চিম’: হাওয়াবদল থেকে উপনিবেশ (১৮৮০–১৯৬০); লেখক: দীপাঞ্জন বাগ; পঞ্চালিকা প্রকাশনী; প্রথম প্রকাশ ২০২২)
দীপাঞ্জন বাগের বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে তাঁর পরিশ্রমসাধ্য এম.ফিল. গবেষণার ফসল। ভারতীয় উপমহাদেশের উনিশ-বিশ শতকের ইতিহাস আলোচনা যেখানে অনেক সময়ই ১৯৪৭ সালে এসে থেমে যায়, সেখানে লেখক স্বাধীনতার পরের এক দশকের কিছু বেশি সময়কাল দুই মলাটের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন। সময়ের এই অগ্রগামিতা বাঙালির ভ্রমণের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে খুবই দরকারি ছিল। উপাদান হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছেন ঔপনিবেশিক মহাফেজখানা ও বেসরকারি সূত্রের তথ্যভাণ্ডার, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম, বিবরণী, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, এবং আলোকচিত্র।
এই ‘পশ্চিম’ কোথায়? লেখক দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই বইয়ের ‘ পশ্চিম’ ইউরোপ-আমেরিকা নয়, বরং সাবেক বিহার, অধুনা ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত কিছু অঞ্চল। সেখানকার বাঙালির বসতি স্থাপনের ইতিহাস তিনি আলোচনা করেছেন। তবে, লেখক যেমন দাবি করেছেন যে, সাঁওতাল পরগনা ছিল “ বর্তমান বিহার-ঝাড়খণ্ড লাগোয়া” ( পৃ. ৬৬), ঠিক তেমনটা তা ছিল না। সাঁওতাল পরগনার নিজস্ব জন্মবৃত্তান্ত আছে। ১৮৫৫-৫৬-র ‘হুল’-এর পর সাবেক বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম ভাগের দুই-তৃতীয়াংশকে আলাদা করে এই প্রশাসনিক বিভাগটি তৈরি হয়েছিল, যা আজকে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত।
‘ পশ্চিম’ নিয়ে বাঙালি প্রবুদ্ধ সমাজের আগ্রহের শেষ নেই। সেই সূত্রে দু-একটি কথা বলা যায়। ঔপনিবেশিক আমলে যখন থেকে বাঙালি পশ্চিমে গেছে হাওয়াবদল করতে, তার সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রায় সেই সময় থেকেই লেখা শুরু হয়েছে। মধ্য-উনিশ শতকে ভোলানাথ চন্দ্র ‘ পশ্চিমের’ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ইংল্যান্ডের মতো শিল্পোন্নত শহর গড়ে ওঠার কল্পনায় মশগুল হয়েছিলেন, সেটাই ছিল তাঁর কাছে বস্তুগত উন্নতির সর্বোচ্চ শিখর। পক্ষান্তরে, বিশ শতকের সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ‘ পশ্চিমের’ নিসর্গ মানেই ধু-ধু প্রান্তর, নিরালা দিগন্ত; তাঁর আরণ্যক রোম্যান্টিক ভ্রমণ-আখ্যান। এতদ্ব্যতীত, ‘ পশ্চিম’-এ বসতিস্থাপন বাঙালির চেতনায় প্রবাসযাপনের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ। পশ্চিমভ্রমণ এবং প্রবাসে বসতিস্থাপন উভয়েরই ইতিবৃত্ত থাকা সম্ভব, কিন্তু এ-দুটি আলাদা-আলাদা বর্গ। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মনিয়ের মনিয়ের-উইলিয়ামস তাঁর অভিধানে দেখিয়েছেন যে, ধ্রুপদী সংস্কৃতে ভ্রমণ এবং প্রবাস শব্দদুটি বহুক্ষেত্রে সমার্থক। কিন্তু, আমাদের বিচারে ভ্রমণের সঙ্গে প্রবাসযাপনের প্রভেদ লক্ষণীয়। দেশপর্যটন করে ঘরে ফেরার অভিজ্ঞতা ঠাঁই পেয়েছে ভ্রমণবৃত্তান্তে, তা জীবনের একটি বৃত্তের সম্পূর্ণতা বুঝিয়েছে। অন্যদিকে, প্রবাসী বাঙালির একদা ‘বিদেশ’-কেই ‘ ঘর’ করে তোলার স্থায়ী যাপন-অভিজ্ঞতা প্রকীর্ণ রয়েছে নানা সাহিত্যকর্মে, যার খানিকটা লেখক যুক্তিসংগত ভাবেই ব্যবহার করেছেন নিজের গবেষণার সূত্র হিসাবে। বাঙালির আত্মপরিচিতি নির্মাণে প্রায় শতাব্দীকালীন এই ভ্রমণ/যাপন কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তার পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কাম্য। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ( উত্তর ভারত) থেকে বর্তমানে আলোচ্য বইটি পর্যন্ত নানা আখ্যানে ‘ পশ্চিমের’ বাঙালির ইতিহাসে ধারাবাহিকতার মধ্যে পরিবর্তনের মনোজ্ঞ কাহিনি উঠে এসেছে। সমসাময়িক সংবাদ-সাময়িকপত্রের অজস্র লেখাপত্র থেকে শুরু করে হালের গবেষণা সন্দর্ভ, অ্যাকাডেমিক জার্নালের সাজানো-গোছানো প্রবন্ধ কিংবা ওজনদার মোনোগ্রাফে যেভাবে পশ্চিমের প্রসঙ্গ এসেছে তার সবটুকু একটি বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে ধরা না গেলেও আশা করা যায় লেখকের পরবর্তী কোনও বিস্তৃততর গবেষণায় সেই প্রসঙ্গ আসবে।
আলোচ্য বইটির ‘ পশ্চিম’ বঙ্গদেশের অব্যবহিত পশ্চিম। কিন্তু, লেখক ‘ পশ্চিম’ বলতে যে বিশিষ্ট একটি ভূরাজনৈতিক অঞ্চলের কথা বলেছেন, তার বাইরের অনেক বড়ো ভৌগোলিক এলাকাও ‘ পশ্চিম’ হিসাবে নানা সময়ে গণ্য হয়েছে, ‘ পশ্চিম’-এর ধারণা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য মহাদেশে প্রসারিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের সময়ের রচনাকর্মগুলিতে ‘ দেশভ্রমণ’, ‘ হাওয়াবদল’, ‘ দেশ দেখা’, ‘ স্বদেশবর্ণন’, ‘ প্রবাস’ ইত্যাদি শব্দের বহুল উল্লেখ থেকে হৃদয়ঙ্গম হয় কীভাবে ‘ পশ্চিম’ একটি ভূরাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সত্তা হিসাবে বাঙালির ‘ মনোচিত্রে’ স্থান করে নিয়েছিল। ভ্রমণের নেশা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশদর্শনের সঙ্গে মিশেছিল ধ্রুপদী মাপকাঠিতে সমকালীনকে পরখ করার সতত প্রয়াস। ঔপনিবেশিক আমলের বাঙালি হিন্দু তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের জগতে পুণ্যতোয়া গঙ্গা-যমুনাবিধৌত ‘ পশ্চিম’-কে ‘ হিন্দু’/‘আর্য’ সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বলে ভাবা হত। ‘ পশ্চিম’-এ যাওয়া ছিল বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোলের বাইরে পা-ফেলা, যা একটি প্রায়-অনির্দিষ্ট ভূখণ্ড — নানা তীর্থক্ষেত্রশোভিত; গাঙ্গেয় বাংলার তুলনায় বেশ খানিকটা ভিন্নধরনের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর দেশ। এই জলবায়ুর নিজস্বতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সুলভ ( ‘ ড্যাম চীপ’, বা উচ্চারণের বিশিষ্টতায় ‘ ড্যাঞ্চি’) খাদ্যদ্রব্যের কল্যাণে অঞ্চলটি স্বাস্থ্যকর, আকর্ষণীয়, ও বসতিযোগ্য। পাশাপাশি ‘ পশ্চিম’ ভ্রমণ/বাস অরণ্যগিরিনদীশোভিত, প্রাকৃতিক ও মানবিক সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে ভরপুর একটি সুবিশাল দেশের আলেখ্য হাজির করত, যা বাঙালি এবং ভারতীয় এই যুগ্মজাতীয়তাবাদী চেতনাকে পুষ্ট করত। ‘ পশ্চিম’-এর আরেকটি দিক পর্যটক/প্রবাসী বাঙালির চোখে ধরা পড়ত — উন্নতিশীল নগরকেন্দ্র এবং পশ্চাৎপদ এলাকার বৈপরীত্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ‘ পশ্চিম’-এর কোনও কোনও এলাকার বস্তুগত উন্নতি যে ওইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাজাত্যপ্রিয়তা এবং স্বাভিমানের লক্ষণ তাও ব্রিটিশের হাতে সর্বপ্রথম পরাধীন বঙ্গভূমির বাঙালি ভ্রমণার্থীর চোখ এড়ায়নি। ব্রিটিশ ভারতের কর্তৃত্ববাদী শাসনের আওতার মধ্যে থেকেও পশ্চিমের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন, আধুনিকতা, এবং ধর্ম তথা সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা হিসাবে আখ্যানগুলিতে প্রশংসিত হয়েছে। নগরায়িত ‘পশ্চিম’-এর নারী বাঙালি নারীর চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে ছিল এমন বর্ণনাও বিরল নয়।
এ ছাড়া, উপমহাদেশের ভূগোলের ভিতর ছিল আরেক ‘ পশ্চিম’ — বাঙালি মুসলমানের ‘পশ্চিম’। আর্যাবর্তের বহুকথিত গরিমা নয়, বরং সেই জগতটিকে নির্মাণ করেছিল মধ্যযুগের শাসকীয় দার্ঢ্যের বস্তুগত স্মৃতি এবং আধ্যাত্মিক জগতের নক্ষত্রস্বরূপ নানা মুর্শিদের স্মৃতিধন্য স্মারকগুচ্ছ। দিল্লি-আগ্রা-আজমের ভ্রমণের আলোচনা এ প্রসঙ্গে যে কেউই করতে পারেন। ধর্মীয় প্রতীকের ছায়াতে উপমহাদেশের অন্যান্য প্রান্তের সমধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে একাত্মতাজ্ঞাপন — সে-ও তো কাঙ্ক্ষিত; একই সঙ্গে চলতে থাকে বিভিন্নতার উপলব্ধি। ‘ পশ্চিম’ যাপনের ইতিবৃত্তে কীভাবে সেই অভিজ্ঞতা স্থান করে নিতে পারে, তাও ভাববার কথা।
আলোচ্য বইতে ‘ পশ্চিমে’ হাওয়াবদলের ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে লেখক একাধিক ‘ পুশ ফ্যাক্টর’ এবং ‘ পুল ফ্যাক্টর’ নির্দেশ করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিঘাতে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে গড়ে ওঠা বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি নানা রোগব্যাধি এড়াতে কেন ‘পশ্চিমে’ অভিপ্রয়াণ করল নানা তথ্য সহযোগে তা আলোচিত হয়েছে। রেলপথের বিস্তার এক্ষেত্রে জরুরি ভূমিকা পালন করেছিল। ইংরেজ আমলে ‘ হিল স্টেশনে’ গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যাবাস হাওয়াবদলের স্থান হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি আঠারো-উনিশ শতকের ইউরোপীয় রোম্যান্টিকতাবাদের প্রভাব ‘পশ্চিমে’ যেতে বাঙালিকে প্রলুব্ধ করেছিল।
‘ পশ্চিমে’ বাঙালির বসবাসের ক্ষেত্রে ১৯৬০ সালকে লেখক একটি সীমারেখা হিসাবে ধরেছেন। উপসংহারে লেখক নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, “ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতির” (পৃ. ১৮৪) ধারকবাহক ‘পশ্চিমের’ বাঙালি সমাজ দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা পরম্পরাকে রক্ষা করে চলতে পারল না কেন? তাঁর মতে, যে বাঙালিরা ‘ পশ্চিমে’ স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেছিলেন, অথবা অবকাশযাপনের জন্য সেখানে যেতেন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীনতার মোটামুটি এক দশক পর থেকেই জীবনজীবিকার প্রয়োজনে ক্রমশই সেই শিকড় থেকে বিচ্যুত পড়েন। “ স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে” (পৃ. ১৮২) লেখক জেনেছেন যে, প্রাদেশিক রাজনীতির টানাপড়েন, ‘ পশ্চিম’ — মূলত বিহারের —উদীয়মান ‘ অবাঙালি’ ব্যবসায়ী ও জোতদার শ্রেণির আর্থসামাজিক উত্থান তথা একদা বাঙালি-অধ্যুষিত পল্লিগুলোতে সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্যোগ, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ও হিন্দির দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণেই ‘পশ্চিমে’ বাঙালির পায়ের তলায় জমি সরতে শুরু করেছিল।
এই প্রেক্ষাপটে ‘ পশ্চিমে’ বাঙালিদের বসতি এবং অবদানকে লেখক লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। ‘ পশ্চিমের’ নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পৌরসভা গঠন, গ্রন্থাগার স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র নির্মাণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত নামী-অনামী বাঙালি প্রতিভার উপভোগ্য বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন ( বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়)। এই বইয়ের এটিই প্রধান জোরের জায়গা। ‘ পশ্চিমে’ যারা “আগমন” করেছিলেন, তাঁদের অনেকের সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া-সদৃশ পরিচিতিজ্ঞাপন পাঠকসহায়ক হবে। বইয়ের পরিশিষ্ট হিসাবে কয়েকটি আলোকচিত্র সংযোজিত হয়েছে, যার মধ্যে লেখকের নিজস্ব সংগ্রহের আলোকচিত্রগুলি সাম্প্রতিক নথি হিসাবে বইটির মান বাড়িয়েছে।
তরুণ লেখকের প্রথম বইয়ের ছাপা ও বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশক পারিপাট্য দেখিয়েছেন, কুশল ভট্টাচার্যের প্রচ্ছদটিও মনোগ্রাহী। তবে আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। বইতে আলোচিত সময়কালের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ। তাতে ‘পশ্চিমের’ বাঙালির অংশগ্রহণ নিয়ে সবিশেষ উল্লেখ জরুরি ছিল। বৃহত্তর দেশ-জাগরণের ঘটনাপ্রবাহ তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কি ‘ পশ্চিমের’ স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালিকে নাড়া দেয়নি? তাঁদের কাজকর্ম কি সমাজসেবা-শিক্ষাবিস্তার-সাংস্কৃতিক নৈপুণ্যের স্ফূরণেই সীমাবদ্ধ ছিল? এগুলি দেশসেবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু, প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরত্বকে (স্বেচ্ছাকৃত?) কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, বিশেষত কলকাতা তথা বঙ্গদেশ যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা প্রবাহে ভাসমান? এই বইতে সেই প্রশ্নের উত্তর তেমন ভাবে পাওয়া গেল না। স্বদেশি আন্দোলনের সময় জসিডিতে বাঙালি বিপ্লবীদের কার্যকলাপ (পৃ. ১২৮), বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গিরিডিতে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখের কর্মসূচি (পৃ. ১৪২), এবং দেওঘরে অনুশীলন সমিতির আখড়ার (পৃ. ১৪৭-৮) উল্লেখ বিক্ষিপ্ত, ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বলেই কি ধরতে হবে?
আরেকটি প্রসঙ্গ আলোচ্য গ্রন্থে একেবারেই আসেনি। তা হল, ‘ পশ্চিমের’ আদিবাসী সমাজ ও বাঙালিদের মধ্যেকার সংযোগ এবং/অথবা বিচ্ছিন্নতার কাহিনি (ব্যতিক্রম : একটি সাহিত্যিক সূত্রে “ সাঁওতাল রমণীদের” উল্লেখমাত্র, পৃ. ১৭২)। উপসংহারে দাবি করা হয়েছে যে, ‘ পশ্চিমে’ বাঙালির উপনিবেশ “ আধুনিক কালের [. . .] সাম্রাজ্যবাদের ‘ কলোনি’ ” ছিল না, “ বরং”, লেখকের মতে, “ প্রাচীন কালের গ্রিক উপনিবেশের” সঙ্গে তার মিল ছিল। এই মতটি অবশ্য তর্কসাপেক্ষ। আধুনিক ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সরিয়ে রাখলে ‘পশ্চিমে’ বাঙালির বিস্তারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি আদৌ উপলব্ধি করা যাবে? নাকি, এক বড়ো ‘উপনিবেশের’ ময়দানের মধ্যেই সৃষ্ট হয়েছিল এই ছোটো ‘ উপনিবেশের’ ক্রীড়াভূমি, বিশেষত যখন লেখক নিজেই দেখিয়েছেন যে ‘ পশ্চিমে’ বহু স্থানেই বাঙালির যাত্রা শুরু হয়েছিল ইংরেজ আমলে রেলপথ, ডাকঘর, খনি, কালেক্টরি ইত্যাদির কাজে? যেসব স্থানে ইংরেজ আনুকূল্যে বাঙালির ‘উপনিবেশ’ গড়ে উঠল সেইসব স্থান কি আদৌ ‘জনবিরল’ ছিল? আখ্যানের এমনধারা নির্মাণ কি একপ্রকারে ‘ উপনিবেশ’ স্থাপনের পক্ষেই বৈধতা দান করে না? ‘পশ্চিমে’ বাঙালির ‘উপনিবেশ’ কি আক্ষরিক অর্থেই সেই দিকে নির্দেশ করে না?
আমাদের আগের প্রশ্নটির নিরিখে এ-কথাও বলা চলে যে বাঙালি, আদিবাসী, অন্য প্রদেশীয় ভারতীয়, ইউরোপীয় অধ্যুষিত ‘পশ্চিমের’ বহুমাত্রিক যাপনের আরেক ধরনের ইতিহাস রচনাও হয়তো সম্ভব, যা মৃদু রোম্যান্টিকতা এবং স্মৃতিবিজড়নের আঁশ ছাড়িয়ে মূলে পৌঁছনোর চেষ্টা করবে (ব্যতিক্রম : একটি ক্ষেত্রে সুনির্মল বসুর স্মৃতিকথায় “ সাহেবদের সঙ্গে ক্রিকেট” খেলার প্রসঙ্গ এসেছে, পৃ. ১৬৬)। তদুপরি, ‘ পশ্চিম’-কে স্থায়ী ঘরবাড়ি করে তোলা মানুষজনের ক্ষেত্রে প্রবাসী অভিধাটি সুপ্রযুক্ত কি না তাও আরেকবার ভেবে দেখা দরকার।
বইয়ের বিষয়বস্তু আলোচনার সময় লেখক সাঁওতাল পরগনার ভৌগোলিক সীমানার বিবরণ দিয়েছেন এল.এস.এস. ও’ম্যালি-র গেজেটিয়ারের সাহায্যে। কিন্তু, তাতে দু-এক জায়গায় ফাঁক থেকে গেছে। পি.সি. ( প্রণব চন্দ্র?) রায়চৌধুরী সম্পাদিত সাঁওতাল পরগনার জেলা গেজেটিয়ার ( ১৯৬৫ সংস্করণ) লেখক ব্যবহার করলেও ( পৃ. ১৫০), বইয়ের শেষে প্রাথমিক উপাদানের তালিকায় সেটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সূত্র হিসাবে লেখক একটি সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন ( পৃ. ২২, ১৩১পাদটীকা), কিন্তু বইয়ের ভূমিকায় ( পৃ. ২২) উল্লেখিত হলেও শেষের সূত্রনির্দেশে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে কি সেটি আলাদাভাবে দেওয়া যেত না? এটি তো লেখকের পরিশ্রমসাধ্য ক্ষেত্রসমীক্ষার নজির। তদুপরি, একই উপাদান তথ্যসূত্র হিসাবে পৌনপুনিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি সংক্ষিপ্তকরণ কাম্য ছিল না? ( দ্র. পৃ. ৯১-৯৫ পাদটীকা) আরেকটি প্রশ্ন, তথ্যসূত্র হিসাবে উইকিপিডিয়া ( পৃ. ৬৯, ৭০, ১২২) পণ্ডিত ও গবেষক মহলে প্রামাণ্য সূত্র হিসাবে কতদূর গ্রহণযোগ্য? এই বইয়ে স্যর জর্জ ক্যাম্বেল ( পৃ. ১০৮) এবং স্যর অ্যাশলে ইডেনের ( পৃ. ৫৭) পরিচয় দেওয়া হয়েছে বাংলার গভর্নর হিসাবে। কিন্তু, উভয়েই যথাক্রমে ১৮৭১-৭৪ ও ১৮৭৭-৮২ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একাধিকবার সূত্রনির্দেশ হিসাবে উল্লেখিত সরোজ কুমার দে ও শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ‘ গিরিডির ঔপনিবেশিক বাঙালী ও ব্যবসা-বাণিজ্য’ ( প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪১) প্রবন্ধে গিরিডিতে রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর রূপে কর্মরত দুজন রাখালচন্দ্রের নাম জানা যায়। লেখক এঁদের একজনের পরিচিতি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর পুরো নাম উল্লেখিত হয়নি ( পৃ. ৯৪)। তাঁর নাম রাখালচন্দ্র তা, যিনি ‘ লতাবৈহার’ মৌজা ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু, উক্ত প্রবন্ধের লেখকদের মতে, গিরিডিতে আগত প্রথম বাঙালি ছিলেন রাখালচন্দ্র কুণ্ডু। তিনিও একজন রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর ছিলেন এবং স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজি বালক বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর উদ্যোগ ছিল। ‘ পশ্চিমে’ বিদ্যাসাগরের জনহিতৈষণার নমুনা হিসাবে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত সারণীটির স্ক্রিনশটের পরিবর্তে পৃথক ভাবে উল্লেখ কাম্য ছিল ( পৃ. ১৭২)।
বিশেষ পরিতাপের কথা, অজস্র মুদ্রণপ্রমাদের জেরে বইটির মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পাণ্ডুলিপি থেকে বই নির্মাণ যে নিছক মুদ্রণ নয়, বরং রূপান্তর, সেই সত্যটি বাংলা বাজারে এখনও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরিচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানস বা পরিমল ভট্টাচার্যের ড্যাঞ্চিনামা : একটি স্মৃতির প্রত্নসন্ধান বইগুলির নামোল্লেখের সময় যত্নশীল হওয়া দরকার ছিল। একই ভাবে, করমাটাঁড় স্থানটির নাম বইয়ের নানা স্থানে (পৃ. ১২২-২৩) নানা ভাবে মুদ্রিত। পাঠ্যে ও নির্ঘণ্টের ব্যক্তিনামের কিছুক্ষেত্রে, যেমন শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ( “শম্বুচন্দ্র”), হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ( “হেরেম্বচন্দ্র”), হেমন্তবালা দেবী ( “হেমেন্দ্রবালা”) ইত্যাদি মুদ্রণপ্রমাদ চোখকে পীড়া দেয়। আলোকচিত্রগুলির মধ্যে একটির ক্ষেত্রে পরিচিতি জ্ঞাপনের ( পৃ. ২১৯-২০) ভুলটি না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। ‘ পশ্চিমের’ জীবনের প্রতিবিম্ব উঠে এসেছে যেসব সাহিত্যকর্মে তাঁদের রচয়িতাদের ( পৃ. ১৭১, সারণী দ্র.) মধ্যে সীতা দেবী ও মণীন্দ্রলাল বসুর জন্মসাল ও প্রয়াণবর্ষ একটু সন্ধান করলেই পাওয়া যেত। এঁদের জীবনকাল যথাক্রমে ১৮৯৫-১৯৭৪ এবং ১৮৯৭-১৯৮৬। এ ছাড়া, পুরানো সূত্র থেকে আহৃত উদ্ধৃতির বানান মূলানুগ হওয়া উচিত।
তবে, আশা করা যায়, পরবর্তী সংস্করণে এইসব ত্রুটি সংশোধিত হবে এবং সুসম্পাদিত রূপে বর্তমান বইটি প্রকাশিত হবে। আরও আশার কথা, বইটি যে প্রশ্নগুলি তুলেছে এবং তার সন্তোষজনক সমাধান করতে চেয়েছে, তাতে ‘ পশ্চিম’ সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ বাড়ল বই কমল না।

ভালো লাগলো। পরিমল ভট্টাচার্যের বইয়ে ( ড্যাঞ্চিনামা ) এই নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা পেয়েছিলাম। এই বইও পড়তে ইচ্ছা রইলো। ধন্যবাদ
ধন্যবাদ।