
বাংলা চলচ্চিত্রের বিষয়-আশয়
১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ রায়কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যখন সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করে, সে সভায় তিনি বলেন “এখন এই উপমহাদেশে এমন একটা সময় এসেছে যেখানে চলচ্চিত্র পাঠ একাডেমিক স্তরে কেবলমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য নয়, চলচ্চিত্রবিদ্যার জন্য, যেমনভাবে আমরা সাহিত্য নিয়ে পড়ি, তেমনভাবে সিনেমা নিয়ে পড়া দরকার। এই রকম ভাবনা থেকেই ইউ.জি.সি., যারা আমাদের পড়াশোনার বিষয়গুলি পরিচালনা করে তারা নবম পরিকল্পনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ফিল্ম স্টাডিজ’ শুরু করেন। এই পঠনের সূচনায় যে তিনজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, তাদের মধ্যে আমি একজন। যাদবপুরে এরকম দুটো বিষয় শুরু হয়েছিল, যার একটি হল ‘কম্পারেটিভ লিটারেচার’ বা ‘তুলনামূলক সাহিত্য’ – বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয়টি হল ‘ফিল্ম স্টাডিজ’ বা ‘চলচ্চিত্রবিদ্যা’।
আজকে আমরা আলোচনা করব সিনেমার বিষয়-আশয় নিয়ে। সিনেমার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা তুলনামূলকভাবে সহজ, কারণ আমরা যদি প্রথম সিনেমা দেখার দিনটি কথা উল্লেখ করি, অন্তত ইউনেস্কোর মত অনুযায়ী, যদিও এই তারিখটি নিয়ে বিতর্ক আছে, সেটি হল ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর। এই দিনটিতে প্রথম ফিল্ম দেখানো হয় প্যারিস শহরে। প্যারিসের বুলভার দ্য ক্যাপিচিনো নামে একটি জায়গায় লুমিয়ে ভাইদের চেষ্টায় অর্থাৎ অগাস্ট লুমিয়া এবং লুই লুমিয়ার উদ্যোগে প্রথম ছবি দেখানো হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের গ্রহে ছবির বয়স মাত্র ১২৫ বছর মত। এই ১২৫ বছরের ইতিহাস লেখা তুলনামূলকভাবে সহজ, আবার খুবই কঠিনও। কঠিন হওয়ার কারণ, আজকে আমরা সিনেমায় যে নানা ধরনের বিভাগ দেখতে পাই, তার কোন বিভাগের ইতিহাস লিখব? অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী আমাদের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে এসে বলেছিলেন যে, যখন ‘হোয়াট ইজ হিস্টরি’ লেখা হল, তারপরে ইতিহাস লেখাটাই পাল্টে গেল। আবার সুশোভন সরকার ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে ছিলেন ক্লাসিক্যাল একটি রূপ টেনে। ঠিক তেমনি, সিনেমার ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন। যখন আমরা সিনেমার সম্বন্ধে পড়ি, চরিত্রগুলি কী আছে, গল্পটি কী আছে – এর মধ্যেই আমরা সিনেমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখি। এখানে একটি কথা বলার, তা হল চলচ্চিত্র দুইভাবে শিল্প। এটা যেমন আর্ট অর্থে শিল্প, তেমনি ইন্ডাস্ট্রি অর্থও শিল্প। ইন্ডাস্ট্রি কেন? ভারতবর্ষে দেখা যায় কত লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিনেমার কারণে জীবিকা নির্বাহ করেন। ভারতবর্ষের যে সমস্ত বড় বড় সিনেমা তৈরির কেন্দ্র যেমন বলিউড, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, এছাড়াও এখনকার বহু ছোট ছোট কেন্দ্র যেমন – কলকাতা, ভুবনেশ্বর, আসাম, পাঞ্জাব – ইত্যাদিতে যে পরিমাণ শিল্প উৎপাদন হয়, তাতে যথার্থভাবেই সিনেমাকে ফিকি শিল্পের তকমা দিয়েছে। আমরা চাইলে এই শিল্পের ইতিহাস লিখতে পারি। এছাড়া চলচ্চিত্র এমন একটি প্রকাশমাধ্যম যা সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রনির্ভর। এইকারণে আমরা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রের ইতিহাস লিখতে পারি, অর্থাৎ টেকনোলজির ইতিহাস। সেলুলয়েড জিনিসটা পদার্থ হিসেবে আজ প্রায় অচল হয়ে এসেছে। এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে যে ছবিগুলো নির্মাণ করা হয় ম্যাগনেটিক টেপ, রে ইত্যাদির মাধ্যমে; সত্যজিৎ রায়রা এভাবে ছবি করতেন না বা পথের পাঁচালীকে এভাবে দেখা উচিৎ বলে মনে হয় না।
এবিষয়ে আপনাদের একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। যদি সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে পথের পাঁচালী ছবিটি টিভির পর্দায়, কম্পিউটারের পর্দায় বা মোবাইলে – আপনি যেখানেই দেখুন না কেন, যে সিনেমাটা আপনারা আসলে দেখবেন পথের পাঁচালীর নামে, সেই ছবিটা সত্যজিৎ রায় বানাবেন বলে কল্পনাও করেননি। কেন করেননি তার অনেক কারণ আছে, তার মধ্যে একটা কারণ বলি। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর ১ সেকেন্ডে ২৪টি ফ্রেম হয়। যারা ফিজিক্স পড়েছেন তারা খুব সহজেই জানেন যে পার্সেপশন অফ ভিশন নামে একটা জিনিস আছে। আসলে চলমান চিত্রমালা বা মুভিং ইমেজেস বলে কিছু হয় না। সবকিছুই স্থিরচিত্র বা স্টিল ইমেজেস। প্রতি সেকেন্ডে যদি এমন ২৪টি ছবি দেখানো যায় তবে এক ধরনের দৃষ্টিভ্রম হয়। যার ফলে তাকে চলমান চিত্র মনে হয়। এই চলমান চিত্র দিয়ে যখন সেলুলয়েডে সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালী তৈরি করেন তখন প্রতি সেকেন্ডে ২৪টি চিত্র চলে, অথচ আমরা যখন টিভির পর্দায় বা ক্যাসেটে বা ভিডিওতে এই সিনেমাটা দেখি, তখন প্রতি সেকেন্ডে ২৫ বার চিত্রটি যায়। এর ফলে ছবিগুলো ভাঙে, ডায়লগ ভাঙে, মিউজিক ভাঙে এমনকি নয়েজ ট্রাকও ভাঙে। এর ফলে পাখি ডাকছে বা পুকুরে একটা ঢিল পরল – এই শব্দগুলো বদলে যায়। এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়।
যাই হোক, চলচ্চিত্রের প্রযুক্তির নানা ধরনের পরিবর্তন হয়েছে – একসময় নির্বাক ছিল সবাক হয়েছে, সাদা-কালো ছিল রঙিন হয়েছে, ক্যামেরাগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। যদি আপনারা শিল্পের দিক দিয়ে দেখেন, তাতে নানা পরিবর্তন হয়েছে। যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র বিভাগে ‘মিডিয়া ল্যাব’ নামে একটি জায়গায় বিভিন্ন সময়ের চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি সম্বন্ধে লেখা রয়েছে, পুরনো যন্ত্রপাতিগুলি কিছুটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে; এমনকি যে ক্যামেরায় সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী সিনেমাটি তোলেন, ক্যামেরাটিও সংরক্ষিত করা আছে। যদিও সেই ধরনের ক্যামেরায় আজকাল আর ছবি তোলা হয় না। এছাড়াও আপনারা যদি আর্ট হিসেবে চলচ্চিত্রকে দেখেন, তার একটা আলাদা ইতিহাস হতে পারে। যদি কেমিক্যাল পরিবর্তন থেকে দেখেন তারও একটি ইতিহাস আপনারা খুঁজে পাবেন অর্থাৎ কেমিস্ট্রির দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে সেলুলয়েডটা কী, তাতে যে নাইট্রেট সলিউশন ব্যবহার করা হয় – সেটা কী, বা পরবর্তীকালে সেটা পালটে যা দাওয়া হল সেটাইবা কী – ইত্যাদি। এছাড়াও দেখতে পারেন গত ১০০ বছরে কিভাবে দর্শক পাল্টে যাচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অথবা দেখতে পারেন প্রোডাকশন এবং তার ডিস্ট্রিবিউশনের পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সুতরাং সিনেমার ইতিহাস একরকম নয় বরং বহু রকম এবং এই বহুরকম জায়গা থেকে ইতিহাসকে দেখা যেতে পারে।
সিনেমার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে আরেকটা প্রশ্ন ওঠে। যেমন ধরুন কালিদাসের ‘মেঘদূত’, রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’, অবনীন্দ্রনাথের ছবি, জীবনানন্দ দাশের কবিতা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস – এগুলো বিশেষ এক ধরনের প্রশিক্ষিত মানুষের কাছে আলাদা অর্থ বহন করে যারা এই ধরনের শিল্পের বিষয়ে আগ্রহী। কিন্তু ধরুন একজন নিরক্ষর ইংরেজের কাছে আপনি যতই বলুন যে শেক্সপিয়ার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, তার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। ঠিক একই রকমভাবে একজন নিরক্ষর বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা কেন অনন্য, তার কোনো কারণ তিনি বলতে পারবেন না।
সিনেমার একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা কোন সাক্ষরতার অপেক্ষা করে না। আমরা ‘লিটারেসি’ শব্দটা বহুবার শুনি কিন্তু ‘সিনেমাসি’ কথাটা কখনো শুনি না। সিনেমাহলে যে কেউ যেতে পারেন এবং একজন নিরক্ষর মানুষও নিজের মত করে সিনেমা বোঝার ক্ষমতা রাখেন। হয়তো বোঝার ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে কিন্তু সিনেমার জয়যাত্রা এখানেই যে, যে কোন মানুষ তা বুঝতে পারেন। এইজন্যই একে আধুনিক যুগের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ মাধ্যম বলে মনে করা হয় কারণ সিনেমা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক একটি প্রকাশমাধ্যম। রবীন্দ্রনাথের গোরা যেমন অনেকেই বুঝবেন এবং আবার আনেকে বুঝবেনও না, কিন্তু সিনেমা দেখলে সকলেই বুঝবেন। এই পিকটরিয়াল মাধ্যম অর্থাৎ চিত্রিতভাষা সর্বজনীন কিন্তু লিখিত ভাষা সর্বজনীন নয়। সকলের কাছে গণিতের প্রয়োগ থাকলেও তা কিন্তু একটি প্রতীকী ভাষা – তাই সবাই তা বুঝতে পারেন না। এছাড়াও সাহিত্যের চিহ্নায়ন সর্বজনগ্রাহী নয় কিন্তু সিনেমার চিত্রায়ন সর্বজনীন। সিনেমা সাংস্কৃতিক স্তরান্তর দাবি করে না, ফলে সত্যজিৎ রায়ের পাশে বসে একজন সাধারণ মানুষও অবলীলায় সিনেমা দেখতে পারেন, অনেকটা নামাজ পড়ার মতো। একজন বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে সিনেমা কীকরে আমাদের সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ভেঙে দিল। সেসময় প্রতি সেকেন্ডে দশটি ফ্রেম দেখানো হত, যন্ত্রের এই গতিশীলতা কিভাবে আমাদের সভ্যতার ধারণাকে পাল্টে দিল। এইযে এক সময়ে শিল্পায়ন, গণতান্ত্রিক মনোভাব এল – তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা সিনেমার আবির্ভাব এবং উৎকর্ষকে বিবেচনা করি তাহলে বুঝবো যে আমেরিকায় কেন সিনেমার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার কারণ তখন এটা ছিল নতুন দেশ। এখানে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মত কোন ধরনের সামাজিক হায়ারার্কি ছিল না। কে লর্ড বা ‘কালচার্ড’, আর কে ‘আনকালচার্ড’ তার পার্থক্য আমেরিকার মতো দেশে করা কঠিন ছিল। কারণ এখানে প্রায় সবাই শ্রম বিক্রি করত এবং একটি নির্দিষ্ট অবসরে ও নির্দিষ্ট স্থানে তারা সংস্কৃতির কোন একটি বিষয় নিয়ে মিলিত হতে চাইছিল, তাই এখানে সিনেমা জনপ্রিয় হয়। ফলত আজকে সিনেমার রাজধানী বলে যে হলিউড বিখ্যাত, তা একটি গ্রাম থেকে ক্রমশ প্রকাণ্ড সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়। প্রথমদিকে আমেরিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে সিনেমাগুলি তৈরি হলেও পরবর্তীকালে জলবায়ু এবং অন্যান্য কারণে সিনেমা হলিউডে চলে আসে।
এবার আমরা যদি বাংলা সিনেমার শুরুর ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে হতাশ হতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহু আগেই বলেছিলেন, বাংলার কোন ইতিহাস নেই। পরবর্তীকালে বাংলার ইতিহাস নিয়ে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি করেন, তাতে যদুনাথ সহ অনেকেই আগ্রহী হন। তার বক্তব্য ছিল, ‘ইতিহাস কে লিখবে? তুমি, আমি সকলেই লিখবে’। কারণ বাংলার প্রাচীন ইতিহাস লেখার জন্য ঐতিহাসিক উপাদান অত্যন্ত কম। বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। যদি বাংলা ছবির আদি ইতিহাস আপনি জানতে চান তাহলে খুব জোর দিয়ে বলতে পারি ‘তা নেই’। এই ‘নেই’-এর প্রথম কারণ মেটেরিয়ালের অভাব, দ্বিতীয় কারণ সিনেমা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব।
বই সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা আছে যে, বই গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করতে হয় – সে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতেও ছিল, এমনকি নালন্দাতেও ছিল। কিন্তু সিনেমা সংরক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন মানসিকতা নেই। আসলে সিনেমা যখন এসেছিল, তখন তাকে হালকা বিনোদন ছাড়া আর কিছুই ভাবা হয়নি। সিনেমা যখন প্রথম আসে তখন তা দেখে সাধারণ মানুষের মনে ছিল এটা একটা ম্যাজিক, যেখানে মানুষ হাঁটে, চলে, কথা বলে। কেউই তখন সিনেমাকে আর্ট হিসেবে গ্রহণ করেননি। এমনকি সিনেমা আবিষ্কারক হিসেবে যাদের কথা বলা হয় অর্থাৎ সেই লুই লুমিয়ে এবং অগাস্ট লুমিয়ে- তারা পর্যন্ত সিনেমার পেটেন্টটাকে বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন ১৯০২ সালে। কারণ তাদের মনে হয়েছিল সিনেমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সিনেমা অনেকটা বাচ্চাদের খেলনার মত। কিছুদিনের আকর্ষণের পর তা উঠে যাবে । কিন্তু সিনেমা তো উঠলোই না, এমনকি সোয়া’শ বছর পরে সবচেয়ে শক্তিশালী এক্সপ্রেশন হিসেবে জায়গা দখল করে আছে। শুধু মুভি নয়, যেকোনো অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম, সে ফিচার ফিল্ম বা ডকুমেন্টারি বা যেকোনো ধরনের ভিডিও হোক না কেন, বর্তমান সভ্যতার কিওয়ার্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
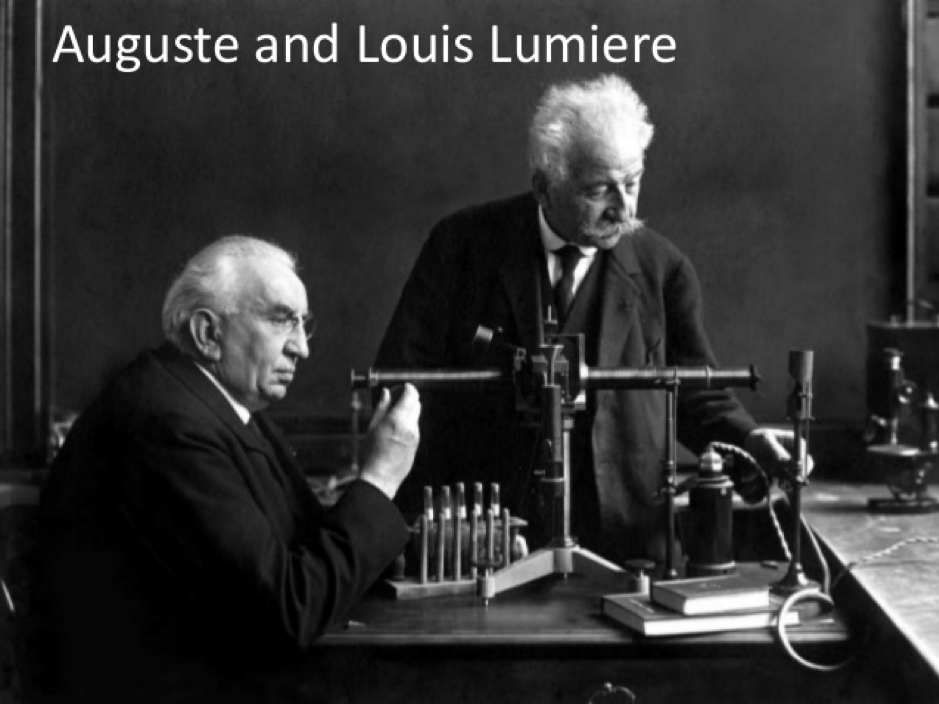
যাই হোক, এই যে সিনেমা শুরু হল ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর, তা মাস ছয়েকের মধ্যে তা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়। ভারতবর্ষে প্রথম সিনেমা দেখানো হয় ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই একটি বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যাতে বোম্বের ওয়াটসন হোটেলে। এই হোটেলটা আজ আর নেই, ভেঙে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এর ছবি রয়েছে। এই হোটেলটায় সেদিন সন্ধ্যায় যে সিনেমা দেখানো হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত খরচার, টিকিট ছিল এক টাকা। বুঝতেই পারছেন ১৮৯৬ সালে এক টাকার টিকিটের যথেষ্ট মূল্য ছিল। তাই ভারতবর্ষে সেই প্রথম সিনেমা দেখতে পেরেছিলেন বিলিতি সাহেবরা এবং তাদের কিছু নেটিভ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। সাধারণের পক্ষে সেদিন সিনেমা দেখা সম্ভব হয়নি। এখানে একটি বড় প্রশ্ন আছে। সে সময় ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল কলকাতা, অথচ লুমিয়ে ভাইয়েরা বোম্বেতে সিনেমা দেখিয়ে সোজা চলে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার দিকে, কিন্তু কলকাতায় কেন এলেন না? এটা কেন হল, সে প্রশ্নের উত্তর আমরা আজও দিতে পারিনি। যাই হোক, তখনকার দিনের আমদানি করা ছবিগুলি কিন্তু কোনটাই কাহিনীছবি নয়। ছোট ছোট রিল হত। ছবি তোলা হত কেবলমাত্র দিনের বেলায়, আলোক নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, শব্দ তো ছিলই না – এমনকি ক্যামেরা ছিল স্টিল। এগুলোকে আজকের অর্থে চলচ্চিত্র বলা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। পৃথিবীর প্রথম ছবি তৈরি হয় ‘ট্রেন অ্যারিভিং অ্যাট গিয়ার্ডো নর্থ’ (L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat)। ছবির বিষয় ছিল ফ্রান্সের গিয়ার্দো নর্থ নামে একটি রেল স্টেশনে ট্রেন আসার দৃশ্য। এই ছবিটা দর্শকদের কাছে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। মনে রাখবেন সে দর্শক কিন্তু আমাদের দেশের বিহারি বা বাঙালি বা ওড়িয়া দর্শক নয়, সুশিক্ষিত ফরাসি দর্শক। ট্রেনটা যখন আসছে তা দেখে সেই দর্শকরা এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যা প্রায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা হতে চলেছিল। তার কারণ, দর্শকরা ভেবেছিল যদি ট্রেনটা এসে তাদেরকে পিষে ফেলে! অর্থাৎ এই ঘটনা বোঝা যায় যে এই ছবিগুলি সেই সময়ের মানুষের মধ্যে কতটা বিস্ময় বিষয়ে তৈরি করতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষের ছবির আলোচনায় ফিরে আমরা দুজন মানুষের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করব। তারা হলেন বম্বেতে হরিশচন্দ্র ভাদবদেকর ও বাংলায় হীরালাল সেন। এই দুজন ভারতে প্রথম সিনেমা বানাতে শুরু করলেন। শুরু করলেন কারণ সাহেবদের জীবন দেখে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছিল না। এরা কাহিনী ছাড়া এক ধরনের ছবি তৈরি শুরু করলেন, যেমন মালাবার উপকূলে ডাবগাছ নুইয়ে পড়েছে এবং তা থেকে ডাব ছেড়া হচ্ছে। বোম্বেতে জুহু বিচের কাছে কুস্তি খুব জনপ্রিয় ছিল, তাই কুস্তি নিয়ে কয়েকটা ছবি তৈরি হল, আর আমাদের এখানে ছবি তৈরি করলেন হীরালাল সেন। হীরালাল সেন আসলে একজন ভাগ্যাহত পদাতিক। তার সম্বন্ধে আমরা বেশি কথা বলতে পারিনি। আজ থেকে বছর দুয়েক আগে ফিল্ম ফেস্টিভাল উদ্বোধন করতে এসে অমিতাভ বচ্চন হীরালাল সেনের কথা উল্লেখ করেন। তাই হয়তো আমরা হীরালাল সেনের কথা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানতে পারলাম। আগে তার কথা হয় জানতাম না, বা জানলেও তত গুরুত্ব দিতাম না। বর্তমানে তাকে নিয়ে বাংলাদেশ এবং কলকাতায় বই প্রকাশিত হয়েছে এবং ইংরেজিতেও কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। হীরালাল সেনের পিসতুতো ভাই অত্যন্ত বিখ্যাত, তার নাম দীনেশচন্দ্র সেন, যিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নামকরা একজন অধ্যাপক ছিলেন। হীরালাল সেন কলকাতায় এসে ছবি তোলা শুরু করেন এবং তার ছবি তোলার দক্ষতা এতই ভালো ছিল যে সে যুগে Bourne & Shepherd নামক একটি দামি ফটোগ্রাফি সংস্থা, যারা বার্ষিক কম্পিটিশনের ব্যবস্থা করত, সেখানে হীরালাল প্রথম হন। তবে হীরালাল এর চেহারা তেমন আকর্ষণীয় ছিল না, এবং এমনকি তিনি ইংরেজিও বলতে পারতেন না, তাই সেই কোম্পানির ছবির যিনি বিচারক অর্থাৎ বিচারপতি ম্যাকফার্লেন সাহেব তার কাজে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। হীরালাল ‘সানসেট অন হুগলি’ নামে একটি ছবি তুলেছিলেন, যেটি নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই সন্দেহ নিরসন করতে আরেকজন সাহেবের সাথে হীরালাল সেন আবার গঙ্গার ঘাটে গেলেন এবং সেই ছবিটি তুলে দেখালেন। এরপর হীরালাল চলমান ছবি দেখেন এবং তিনি এই ছবি দেখে এতটাই আকর্ষিত হন যে নিজেই ছবি তুলে দেখানো শুরু করেন কলকাতা সহ ভোলার (দক্ষিণ বরিশালর এস.ডি. বাংলোয়) মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত তিনি ছবি দেখিয়েছিলেন। হীরালাল সেনকে আমরা মনে রাখিনি এ এক গভীর অপরাধ, কারণ হীরালাল সেন কেবলমাত্র ছবি বানিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি ছবি বানানোর কিছু টেকনিক্যাল পরিবর্তনও করেন। তখন কলকাতায় বিদ্যুৎ ছিল না। যদিও ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম কমার্শিয়াল বিদ্যুৎ আসে কিন্তু সেই বিদ্যুৎ সর্বত্র ছিল না। ছিল ফোর্ট উইলিয়ামে এবং হাওড়া ব্রিজের কাছে। হীরালাল একটা বড় ট্যাঙ্ক তৈরি করে তার মধ্যে গ্যাস পাইপ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে তার মাধ্যমে সিনেমা দেখানো শুরু করেন। এই টেকনোলজির আবিষ্কারের কথাগুলো আমাদের লেখা উচিত ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা তা লিখতে পারিনি। ১৮৯৮ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়ে হীরালাল সেন ও তার ভাই মতিলাল সেন একটি কোম্পানি তৈরি করে (রয়াল বায়েস্কোপ কোম্পানি) বিভিন্ন জায়গায় সিনেমা দেখান। প্রায় এই সময়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘আলিবাবা’ নাটক কলকাতায় হচ্ছিল। তখন থিয়েটারের একটা সংকটের সময়। তাই থিয়েটারকে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করতে মাঝে কিছু প্রলোভন অর্থাৎ অন্যরকম কিছু দেখানোর চেষ্টা চলছিল। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরিচালকরা এই চেষ্টা করছিলেন। তারা হীরালালকে এই কাজে নিয়োগ করলেন এবং হীরালাল নাটকের মাঝখানে কিছু এই ধরনের চলমান চিত্রমালা দেখানো শুরু করলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আলিবাবা এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমর উপন্যাসের কিছু অংশ এই সময় তিনি তুলেছিলেন। এগুলো আধুনিক-অর্থে সিনেমা কিনা তা বলা দুষ্কর কারণ তিনি স্টেজের কিছু অংশ তুলেছিলেন। আজকের ছবির পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোকে হয়তো কাহিনীচিত্র বলা নাও যেতে পারে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার যে, হীরালাল সেন হলেন ভারতবর্ষের প্রথম তথ্যচিত্র নির্মাতা। বঙ্গভঙ্গের সময় অর্থাৎ ১৯০৫ সালে হীরালাল সেন টাউনহলের দোতলা থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র মিছিল পরিচালনা করছেন, তার ছবি তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে বক্তৃতা দিচ্ছেন সেই ছবিও ছিল। দুঃখের বিষয় ছবিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে।

হীরালাল সেন
হীরালালের তৃতীয় কৃতিত্ব, আমাদের দেশে প্রথম অ্যাড ফিল্ম তিনিই নির্মাণ করেন। জবা কুসুম তেল এবং এডওয়ার্ড জেনারেল ম্যালেরিয়া স্পিসিফি (ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ওষুধ, এই সময় ম্যালেরিয়া খুব ভয়াবহ ছিল) -এর বিজ্ঞাপন হীরালাল তৈরি করেন। এছাড়া তিনি রাজেন মল্লিকের মার্বেল প্যালেস, কলকাতার শোভাযাত্রা ইত্যাদি তোলেন। দুঃখের বিষয় ১৯১৭ সালে হাতিবাগানের একটি বাড়ির দোতলায় তার যে গোডাউন ছিল সেটা অগ্নিদগ্ধ হয়ে সেই সমস্তকিছু নষ্ট হয়ে যায়। এই আগুন লাগার ঘটনায় হীরালাল সেনের সম্পত্তি যেমন পুড়ল, বাংলা ছবির অতীত ইতিহাসও পুড়ে গেল এবং সেই সাথে সাথে আমাদের ইতিহাস লেখার উপাদানগুলিও শেষ হয়ে গেল। সিনেমা যে সংরক্ষিত করতে হয়, সে ধারনা আমাদের আগে ছিল না। হীরালাল সেন তো অনেক দূরের কথা, আজকে উত্তম কুমারের সব ছবি আপনি চাইলেই দেখতে পাবেন না। কারণ বেশিরভাগ ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। একথা সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রেও সত্যি, কারণ অপরাজিতর বেশ কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। বাঙালি হিসেবে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। ঋত্বিক ঘটকের ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’-এর ক্রেডিট টাইটেল নষ্ট হয়ে গেছে। এর কারণ আমাদের সচেতনতার অভাব, তাই আমরা সংরক্ষণ করে রাখিনি। এই যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তারও সব ছবি আপনি দেখতে পাবেন না। আমরা জানি বই হলে তা লাইব্রেরিতে রাখতে হয়, কিন্তু সিনেমা হলে যে আর্কাইভে রাখতে হয় সেই সচেতনতা আমাদের নেই। ভারতবর্ষে যেমন ন্যাশনাল আর্কাইভ রয়েছে, কলকাতাতেও আমরা একটা ছোট আর্কাইভ করার চেষ্টা করেছিলাম যা এখনো খুব বড় হয়েছে এমন বলা যায় না। কারণ আর্কাইভ করারও কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, যেমন -3 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা রাখতে হয়, হিউমিডিটি রাখা যায় না – যেগুলো অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। তাই অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে এর বিপুল আকার বা আয়তন দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখনও ভারতবর্ষের ফিল্ম আর্কাইভিং-এর পদ্ধতি অত্যন্ত দুর্বল।
যাই হোক, হীরালাল সেন আমাদের প্রথম ছবি দেখানোর পথ করলেন এবং এখানে ছবি যে তৈরি করা যায় সে পথও দেখালেন। তবে আমাদের বাংলা ছবির প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন এবং এক্সিবিশন এই তিনটি বিষয় এক সুতোয় গাঁথলেন যিনি তিনি বাঙালি নন, পার্শি। জামশেদজি ফার্মজি ম্যাডক, তার নামেই ম্যাডক স্ট্রিট। তিনি ব্যবসা করতেন চাঁদনিচকের কাছাকাছি। তিনি যে ছবি করতেন তার মধ্যে পার্শি নাটকের প্রভাব বেশি ছিল, বাঙালিয়ানা খুব বেশি ছিল না; অন্ততপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ দেব ইত্যাদিরা তা লিখেছেন। তিনি ছবি করার সময় সেগুলোকে একেবারেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাক্ট ভাবতেন। একটা ক্যামেরা আছে, তাকে সুইচ-অন এবং সুইচ-অফ করা এবং যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি একটা ছবি শেষ করে দেওয়া। ঘটনাক্রমে এদেরই একটি ছবি ‘কাল পরিণয়’ সত্যজিৎ রায়ের জীবনের প্রথম দেখা ছবি। বড়দিনের সময় তার মামার সাথে গিয়ে এই ছবিটি দেখেন। অবশ্য ইচ্ছে করে তারা এই ছবিটা দেখতে যাননি। তার মামা চেয়েছিলেন বড়দিনের ছুটিতে ভাগ্নেকে একটি বিলিতি ছবি দেখতে, কারণ মামা ছিলেন ব্রাহ্ম। কিন্তু বিদেশী ছবি সব হাউসফুল হয়ে যাওয়ায় ওরা একটা বাংলা ছবিতে ঢুকতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই কাল পরিণয় ছবিতে ধীরাজ ভট্টাচার্য এবং এক ফিরিঙ্গি অভিনেত্রী রেনিস স্মিথ অভিনয় করেছিলেন। ওখানে নববিবাহিত দম্পতির একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্য ছিল যা আজকের দৃষ্টিতে একেবারেই নিষ্পাপ দৃশ্য। কিন্তু সেই সময়ে যেই মুহূর্তে সে দৃশ্য আসছে অমনি মামা তার ভাগ্নের চোখ হাত দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন। কারণ মামা তার ভাগ্নেকে কোন খারাপ দৃশ্য দেখতে দেবেন না। আর ভাগ্নেও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বারবার চোখে হাত চাপা দিয়ে দেওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্নের বয়স তখন অত্যন্ত কম, সাত-আট বছর হবে। ফলত কাল পরিণয় পুরো ছবিটা আর সত্যজিৎ রায়ের দেখা হল না।
এই ম্যাডকরাই প্রথম কাহিনীচিত্র তৈরি করলেন। ১৯১৭ সালে ‘সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র’ নামে একটি সিনেমা তারা করলেন। তার আগে বোম্বেতে দাদাসাহেব ফালকে রাজা হরিশচন্দ্র ছবিটি তুলেছিলেন ১৯১৩ সালে। তার একটি বঙ্গীয় সংস্করণ হল এই ‘সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র’। এরপরে ১৯১৯ সালে ‘বিল্বমঙ্গল’ ছবিটি তারা করেছিলেন। এটি আমাদের কাছে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। আজকে দেখা যেতে পারে এমন প্রথম ছবি এটাকেই বলা যায়। আর কিছুদিনের মধ্যে এই ছবিটি হয়তো সবাই দেখতে পারবেন। এর পরের ছবি ১৯২১ সালে। গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন তখন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মশাই, যিনি শান্তিনিকেতন থেকে পড়াশোনা করেছেন, পরে হায়দ্রাবাদে নিজাম কলেজ অফ আর্টস পড়াতেন, তিনি একটা ছবি তৈরি করলেন যার নাম ‘বিলেত ফেরত’। এই ছবিটির মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় বা পৌরাণিক ছবি থেকে সামাজিক বিষয়ের ছবিতে পরিবর্তিত হলাম। যারা লন্ডনে বৃষ্টি হলে কলকাতায় বসে ছাতা খুলতেন অর্থাৎ একেবারে ইংরেজ নকলনবিশ, তাদের বিদ্রূপ করে এই ছবিটি নির্মিত হয়েছিল। তাই এটি প্রথম সামাজিক চিত্র। এরপর ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের মানভঞ্জন গল্পটি থেকে সিনেমা হয়েছিল। অবশ্য মূল কাহিনী থেকে ছবি তৈরি হয়েছিল আরও পরে, ১৯৩০ সালে মধু বসু, সাধনা বসু ‘গিরিবালা’ নামে ছবিটি তৈরি করেন। শোনা যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বক্সে বসে ছবিটি দেখেছিলেন। তবে তার বিশেষ কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সাধারণত রবীন্দ্রনাথ শিষ্টাচার বশত সকলকেই ভালো বলতেন, এক্ষেত্রেও হয়তো তিনি ভালোই বলে থাকবেন। তবে তখনও রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রকে যথার্থ শিল্প বলে মনে করতেন না। এমনকি সেই সময় অনেক বুদ্ধিজীবীরাই – বলতে গেলে কেউই তা মনে করতেন না। যেখানে সিনেমার জন্ম অর্থাৎ ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি পল ভ্যালেরি বা মার্সেল প্রুস্তের মত উপন্যাসিক পর্যন্ত মনে করতেন ছবি তো আসলে বাস্তবতার ওপর চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নেওয়া সমাজের একটা চিত্র মাত্র, তা শিল্প হয় কীকরে। ম্যাক্সিম গোর্কির রুশদেশে বিশ্বাস করা হত এমন সাদাকালো নিষ্প্রাণ জিনিসের থেকে শিল্প হয় না। এমনকি ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচ্যুড’ উপন্যাসে গ্যাব্রিয়েল গার্জিয়া মার্কেজ লিখছেন যে হলদে ট্রেনে করে যখন মৃতদেহ আনা হচ্ছে তখন দর্শকরা তার তীব্র বিরোধিতা করছেন কারণ আগে মারা গেছে আর পরের দৃশ্যে তিনি কথা বলেন কি করে! এসব দেখে জনগণ যখন খুব বিরক্ত তখন তাদের ঠান্ডা করতে তাদের বলছেন যে, এ তো ছবি, একে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই।
অর্থাৎ সে যুগে ছবিকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু ছিল না। রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবেন একেবারেই তার জীবনের শেষের দিকে এসে। তিনি মস্কোতে সের্গেই আইজেনস্টাইনের ‘ব্যাটেলশিপ পটেমকিন’ দেখেন। ১৯২৫ সালে তিনি ইতালি থেকে ফেরার পথে কিছু ছবি দেখেছিলেন। তা দেখার পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। যদিও তা সিনেমা সম্বন্ধে পছন্দের কথা নয়, কিন্তু খুব মৌলিক মন্তব্য। তিনি নিজে জার্মানিতে থাকাকালীন একটি ছবি বানানোর কথা হয়েছিল এবং উফার স্টুডিও তাকে নিয়ে ছবি বানানোর কথা ভেবেছিল। তিনি এর জন্য লিখেছিলেন ‘দা চাইল্ড’। কিন্তু সেই সময়ের ফ্যাসিস্ট সরকার এই ছবি তৈরি করতে নিষেধ করে ফলে ওই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে ‘শিশুতীর্থ’ নামে এটির বাংলা অনুবাদ করেন। এই শিশুতীর্থ থেকে ঋত্বিক ঘটক ‘সুবর্ণরেখা’ নামে একটি ছবি করেছিলেন। তবে সেখানে শিশুতীর্থ থেকে কিছু লাইন তিনি নিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ শিশুতীর্থ নয়। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভাই মুরারি ভাদুড়িকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে চিঠিতে তিনি আজ পর্যন্ত ভারতীয় ফিল্ম তাত্ত্বিকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পেরেছিলেন। আজও ফিল্ম স্টাডিজ-এর নন্দনতত্ত্বের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ পড়ানো হয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠিতে বলেছিলেন যদি সিনেমাকে শিল্প হয়ে উঠতে হয় তাহলে সাহিত্যের নকলনবিশ ছাড়তে হবে। “সুরের চলমান ধারায় সংগীত যেমন বিনা বাক্যে আপন মাহাত্ম লাভ করতে পারে তেমনই রূপের চলৎপ্রবাহ থেকে কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি উন্মোচিত হবে না? এবং কাহিনীনির্ভরতাকেই তিনি বিপদসংকেত ভেবেছিলেন।
অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগের প্রশ্নটা আসে না; টেকনিক্যালি দু টাকা খরচ করে একটা নোবেল প্রাইজ পাওয়া যেতে পারে। কারণ আপনি এই টাকায় একটা খাতা এবং কলম কিনতে পারেন আর তাতে কিছু লিখে সুইডিশ অ্যাকাডেমির মনোনয়নে নোবেল পেতে পারেন। কিন্তু একটা সিনেমা কখনো কয়েক লক্ষ টাকার কমে তৈরি করতে পারবেন না। কারণ সিনেমায় উপযোগ আছে, বিনিয়োগ আছে, আর এই বিনিয়োগ যারা করেন তারা ব্যবসায়ী। তারা আপনাকে পথের পাঁচালী করার জন্য টাকা দেবে না, দেবে সারাক্ষণ নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় অর্থাৎ যা থেকে তাদের মুনাফা হবে সেই সব কাজে। অর্থাৎ তাদের টাকা যখন সাইক্লিং এবং রিসাইক্লিং হবে তখনই দেবে।
যাই হোক, সিনেমার ইতিহাস প্রসঙ্গে যেটা বলার, নির্বাক যুগের প্রায় কোন বাংলা ছবিই আজ আর সংরক্ষিত নেই। আমরা সে সময়ের লেখা থেকে কিছু তথ্য হয়তো যোগাড় করতে পারি এই মাত্র। যেমন মধু বসু, সাধনা বসু – যারা গিরিবালা তৈরি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের ‘মেয়ে মানুষ’ ইত্যাদি কিছু শব্দ পাল্টে ‘কত্তামশাই’, ‘গিন্নিমা’ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, ভাষাকে পরিশীলিত করতে বলেছিলেন – সেগুলো হতে পারে আলোচনার বিষয়। এইসময়ে গান্ধীজী ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন এবং তার প্রভাব বাংলার যুবকদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে পড়ল। একদিন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মশাই, যার কথা উল্লেখ হয়েছে ‘বিলেত ফেরত’ ছবির ক্ষেত্রে, তিনি একদিন হ্যারিসন রোডের ওপর দিয়ে হাঁটছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন এক ‘ভদ্রলোকের’ ছেলে গামছা বিক্রি করছে। তাই দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি গামছা বিক্রি করছ কেন? ছেলেটি উত্তর দিল ‘আমি স্বদেশী করি, তাই খদ্দরের গামছা বিক্রি করছি’। তিনি অবাক হলেন, জানতে চাইলেন সে কোথায় থাকে। জানতে পারলেন বর্ধমানের শক্তিগড়ে, শক্তিগড়ের জমিদার বংশের ছেলে। তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন, তুমি সিনেমা করবে? সেই ছেলেটি পরে, ১৯২৭ সাল নাগাদ Flames of Flesh (কামনার আগুন) নামে একটি চিত্রনাট্য লেখেন, যা ছিল আলাউদ্দিন এবং পদ্মিনীর গল্প, আজকের পদ্মাবত। সেই লেখক হলেন দেবকি কুমার বসু। এই সময়ই আসামের গৌরীপুরের মহারাজ প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া, যিনি প্রেসিডেন্সির ফিজিক্সের ছাত্র ছিলেন ও পরে বিলেতেও গিয়েছিলেন। তিনি, দেবকি কুমার বসু ইত্যাদি এবং ধীরেন গাঙ্গুলীদের মাধ্যমে সিনেমায় ‘ভদ্রলোক’ সমাজের আগমন শুরু হল ১৯৩০ সাল নাগাদ ।
এর পরেই বাংলা ছবিতে মূল বিপ্লবটি ঘটল। সেটা হল, ১৯৩১ সালে বাংলা সিনেমায় শব্দ এল। বোম্বেতে ‘আনারকলি’ এবং বাংলায় ‘দেনা পাওনা’ সিনেমায়। কলকাতায় একটুর জন্য, বলতে গেলে ফটোফিনিসে এই কাজে সেকেন্ড হয়ে গেল, আর বোম্বে হল প্রথম। শব্দ আসার পর থেকেই বাংলা ছবির আজকে আমরা যে অভিজ্ঞতা করছি তা শুরু হল। কারণ আমরা সিনেমাকে ‘বই’ বলে থাকি, ‘বইটা কেমন ছিল রে?’ বা সিনেমার আলোচনা করতে গেলে আমাদের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে থাকে তার গল্পটা, আর কিছুটা গান, এর সাথে সামান্য অভিনয় নিয়ে আগ্রহ। এটা কেন হয়েছে? এটা হয়েছে তার কারণ, স্যার বীরেন্দ্রনাথ সরকার, তিনি ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উল্টোদিকের বাড়ির থাকতেন, তিনি মিত্রা হলটা বানিয়েছিলেন। যখন মেয়র হিসেবে হল উদ্বোধন করার সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন বীরেন্দ্রনাথ সরকারের মনে হচ্ছিল সিনেমা দিয়ে হয়তো দেশোদ্ধারের কাজ করা সম্ভব হতে পারে। নেতাজির কথায় বীরেন্দ্রনাথ সরকার এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে সিনেমা তৈরির কাজে নেমে পড়েন। অদ্ভুত জিনিস এই ফিল্ম, এখানে আমার মত তুচ্ছতম লোক যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে এসেছে আবার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মানুষ এসেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে। যেমন বিখ্যাত ফিল্মতাত্ত্বিক ও ফিল্ম নির্মাতা সের্গেই আইজেনস্টাইন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে রুশ দেশের বিপ্লবের সময় সিনেমা তৈরি করতে চলে গেলেন। স্যার বীরেন সরকার আমাদের দেশের প্রথম চলচ্চিত্র সম্রাট যিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে চলে আসেন।

স্যার বীরেন্দ্রনাথ সরকার
এই বীরেন সরকার মশাই একটা জিনিস বুঝেছিলেন, বাঙালিরা সাহিত্য ভালোবাসে ও সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাঙালির যত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সকলেই সাহিত্যিক, এমনকি জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে সাহিত্য নিয়ে লিখতে হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন; তাকেও সাহিত্য লিখতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বড় ধর্মগুরু হতে পারেন কিন্তু তাকেও সাহিত্য লিখতে হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ বড় রাজনৈতিক নেতা হলেও তাকেও সাহিত্য লিখতে হয়। অর্থাৎ বাঙালি সাহিত্য ছাড়া কাউকে কলকে দেবে না। বীরেন্দ্রনাথ সরকার বুঝলেন যদি বাঙালিকে সিনেমায় মজাতে হয় তাহলে সাহিত্যনির্ভর সিনেমা তৈরি করতে হবে। সাহিত্যনির্ভর সিনেমা তৈরি করতে গেলে সংলাপ ভালো করতে হবে, আর সংলাপ ভালো করতে গেলে সাহিত্যিকদের দিয়ে সে সংলাপ লেখাতে হবে। কারণ সাহিত্যিক হলে আর যাই হোক তিনি ‘মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে’ জাতীয় সংলাপ লিখবেন না। তারা আর একটু শিক্ষিত স্তরের কাজ করবেন। ফলে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ইত্যাদি একগুচ্ছ সাহিত্যিককে অনুরোধ করলেন, আপনারা চিত্রনাট্য লিখে দিন আমরা তার ছবি বানাবো। এদের সবার মাথার উপর ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বীরেন সরকার আরেকটা বিষয় আনলেন। তিনি জানতেন বাঙালি গান খুব পছন্দ করে। তাই সিনেমায় গান লাগাতেই হবে। তখনো বাংলা সিনেমায় প্লেব্যাক শুরু হয়নি। মান্নাদের কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে, এমনকি নজরুল ইসলাম পর্যন্ত সিনেমায় গানের জন্য পরিচিত ছিলেন। নজরুল ইসলাম নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তিনি কেমন অভিনয় করতেন তা কেউ মনে রাখেনি, কিন্তু তাদেরকে দিয়ে গান গাওয়ানোটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। এইসব চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সুকণ্ঠি হওয়ার দরকার ছিল। নজরুল ইসলাম খুব ভালো গান গাইতেন, তাই তিনি বড় অভিনেতা হয়ে গেলেন। এমনকি নজরুল ইসলাম ১৯৩৩ সালে একটি ছবিও পরিচালনা করেছেন ‘ধ্রুব’ নামে। এর কারণ নজরুল ইসলাম ভাল সিনেমা পরিচালক ছিলেন তা নয়, বরং তিনি ছবিতে এলে গানে গানে ভরে যাবে এই কারণে।

‘নারদ’ চরিত্রে কাজী নজরুল ইসলাম (ধ্রুব)
যাই হোক, ১৯৩২ সালে ভারতীয় সিনেমায় ব্লকবাস্টার এল, যা লাহোর থেকে ইয়াঙ্গণ অব্দি ভাসিয়ে দিল। তার নাম ‘চন্ডীদাস’, দেবকী কুমার বসুর তৈরি। যদি এই ছবিটা আজকে আপনারা দেখেন তাহলে হয়তো একটু স্লথ লাগতে পারে, তবুও দেখলে হয়তো বুঝবেন কিভাবে বাংলা ছবি সময়ের দাবি পূরণ করছে। গান্ধীজী তখন সদ্য গোলটেবিল বৈঠক থেকে খালি হাতে ফিরে এসেছেন এবং তিনি বুঝতে পারছেন হিন্দু, মুসলমান, ডিপ্রেসড ক্লাস – তাদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা কীরকমভাবে ধর্মের তাস খেলছে। তিনি তাই ডিপ্রেসড ক্লাসকে ‘হরিজন’ নামে হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রমে অন্তর্ভুক্ত করার একটা পলিসি শুরু করলেন। এই চণ্ডীদাস সিনেমাটায় আমরা আসলে দেখতে পাব একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী হিসেবে নিউ থিয়েটার্স-এর ব্যানারে দেবকী কুমার বসু তৈরি করেছেন রামী ধোপানী ও চণ্ডীদাসের প্রণয়ের সম্পর্ক। চণ্ডীদাসের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একজন ব্রাহ্মণের সাথে প্রণয়ের সম্পর্ক। এই ছবিতে কিছু পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল তাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির রেজোলিউশনের কোন অংশ বলে মনে হতে পারে। তিনি হয়তো এই ছবির মাধ্যমে সমকালীন রাজনীতির খানিকটা দায় মেটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তিরিশের দশকের শুরুতে আমাদের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও এমন যে সমাজ ছবিটাকে খুব সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল। এই কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতীয় সিনেমা সবসময় সমকালীন রাজনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে। এর উদাহরণ দিতে আমরা অনেক পরের এক সিনেমায় চলে যাচ্ছি – শোলে। শোলে এত জনপ্রিয় হয়েছিল কেন? নিঃসন্দেহে এই ছবির অনেক গুণ আছে। ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনী, অমিতাভ বচ্চন ইত্যাদিরা অভিনয় করেছেন। বেশকিছু নিসর্গ দৃশ্য আছে। কৃতিত্ব আছে ক্যামেরাম্যানের, চিত্রনাট্যের। কিন্তু খেয়াল করবেন শোলে মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। সে সময়টা জরুরি অবস্থা চলছে। হোয়েন অর্ডার ইজ ইনজাস্টিস এন্ড ডিসঅর্ডার ইজ বিগিনিং অফ জাস্টিস। এই যে মাস্তাননির্ভর ছবিগুলি একে একে মুক্তি পেল – শোলে, জাঞ্জীর, দেওয়ার ইত্যাদি এবং আমাদের সুন্দর নায়কের ট্র্যাডিশন চলে গেল; অমিতাভ বচ্চন তার চোয়ারে মুখ এবং অপরিশীলিত ভাষা নিয়ে এত জনপ্রিয় হলেন, তার কারণ একটা সুষম নিয়ন্ত্রণ ভাঙ্গার প্রয়োজন জনগণ অনুভব করেছিল এবং তাই তা জনপ্রিয় হল।
যাহোক, আমরা কথা বলছিলাম তিরিশের দশক নিয়ে। ১৯৩৫-এ নিউ থিয়েটার্স এমন একটি সিনেমা তৈরি করল যা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ছবির রোলমডেল। ১৯১৮ সালে শরৎচন্দ্রের লেখা একটি দুর্বল উপন্যাস অবলম্বনে ‘দেবদাস’ সিনেমা হল। এই দেবদাস কাহিনীটা ভারতীয় প্রণয়োপাখ্যানের রোল মডেল হিসেবে আজও টিকে আছে। দেবদাস মুখুজ্জে এবং পার্বতীর অসফল প্রেমের কাহিনী ভারতবর্ষের প্রায় সব ভাষাতেই সিনেমা হিসেবে তৈরি হয়েছে। এমনকি একাধিকবার তৈরি হয়েছে। বাংলা ভাষায় অন্তত সাত-আটবার তৈরি হয়েছে আপনারা জানেন। এছাড়াও প্রথম দেবদাসের যিনি ক্যামেরাম্যান ছিলেন অর্থাৎ বিমল রায় তিনি ১৯৫৩ সালে হিন্দিতে তৈরি করলেন দেবদাস। এরপর সঞ্জয় লীলা বানসালির দেবদাস, অনুরাগ কাশ্যপের দেবদাস এমনকি পাকিস্তানের টিভি সিরিয়ালে পর্যন্ত দেবদাস তৈরি হয়েছে। একটা কাহিনী নিয়ে মোট ৩৭ বার সিনেমা হয়েছে। এই একটি ছবি ভারতবর্ষকে কাঁপিয়ে দিল। এই ছবিটি হিন্দিতে করে নিউ থিয়েটার্স। প্রমথেশ বড়ুয়া যেহেতু খুব ভাল হিন্দি বলতে পারতেন না তাই পাঞ্জাবি যুবক কুন্দন লাল সায়গলকে নেওয়া হয়। তিনি ভাল গানও গাইতেন। আর পার্বতীর অভিনয় করেছিলেন যমুনা বড়ুয়া। প্রমথেশ বড়ুয়া ছিলেন পরিচালক। এই ছবিটা আমাদের হাতে ছিল না, শোনা যায় যে বাংলাদেশ থেকে ভারত সরকার ছবিটা আনতে পেরেছে।
ঠিক এরপরেই আসে ‘মুক্তি’। পুজোর সময় আমাদের যেমন বিভিন্ন ছবি রিলিজ হয়, ঠিক তেমনই ১৯৩৭ সালে মুক্তি সিনেমাটি প্রকাশ পায়। মুক্তি ছবিটি শুরু হল আসামের গৌরীপুরের নিসর্গ চিত্র থেকে। একজন আর্টিস্ট নাগরিক সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন, কানন দেবীর সুরেলা গলা, মেনকা দেবী সুরেলা গলা ‘ওগো আমার প্রিয়তমা রবির উত্তরীয়’ এইসব। বলা হয় মুক্তি ছবিতেই প্রথম রবীন্দ্র সংগীত প্রয়োগ করা হয়েছিল ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’। এটা রবীন্দ্রনাথের লেখা কিন্তু পঙ্কজ মল্লিক সুর দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। কারণ এর আগেই ‘চিরকুমার সভা’ তৈরি হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া কি চিরকুমার সভা হতে পারে? সেটা মনে হয় সম্ভবই নয়। কিন্তু এই ছবিগুলি আজ আর আমাদের হাতে নেই। যাই হোক, এই যে ছবিকে ‘বই’ করা, আজ পর্যন্ত আমাদের রক্তের মধ্যে, ধমনীর মধ্যে ছবি মানে হল দৃশ্য দিয়ে ধ্বনি দিয়ে, একটি ভালো গল্পের বা সাহিত্যের অনুবাদ। এই ধারণাটা গেঁথে দিল নিউ থিয়েটার্স এবং তার ফলেই সিনেমা ‘বই’ হয়ে গেল।
১৯৪০ এর দশকে সিনেমায় আরো কিছু পরিবর্তন এল। চল্লিশের দশক শুরু হল ৪২-এর আন্দোলন, ৪৩-এর মন্বন্তর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান, আইপিটিএ ফর্মেশন ইত্যাদি দিয়ে। এই সময়ে বিমল রায়ের পরিচালনায়, ‘উদয়ের পথে’তে আমরা প্রথম দেখলাম শ্রমিক নেতার ঘরে কার্ল মার্কসের ছবি। এই যে বড়লোকের মেয়ের সাথে গরিবের ছেলের প্রেম – এটা প্রথম সিনেমায় নিয়ে এলেন বিমল রায়। এই ছবিটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল, এতদিন আমরা যে সিনেমা দেখতাম, তার বেশিরিভাগটাই কিন্তু আমরা আসলে শুনতাম। সেই সময়ের একজন বড় লেখক এবং পরিচালক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ‘অ্যাকশান’ বলে চোখ বন্ধ করে ফেলতেন। তিনি চোখ বন্ধ করে শুনতেন ডায়লগগুলো কেমন শুনতে লাগছে। সেই সময় তো ডাবিংয়ের পদ্ধতি খুব ভাল ছিল না তাই খুব ভালো করে ডায়লগ বলতে হত। তখন দর্শকও মন দিয়ে ডায়লগগুলো শুনত। এমনকি অনেক বাঙালির ‘উদয়ের পথে’র ডায়ালগ মুখস্থ ছিল। যেমন পরবর্তীকালে শোলের ডায়লগ অনেক ভারতীয় মুখস্থ করেছিল। এখানে মনে রাখতে হবে ভারতীয়রা সিনেমা যেমন দেখে তেমনি কিন্তু শোনেও এবং তারা ডায়লগগুলো মনে রাখে। আমাদের দেশে শ্রুতি-সংস্কৃতি খুব শক্তিশালী। তুলসীদাসের রামায়ণ খুব কম লোকেই পড়ে কিন্তু অনেকেই শুনে মনে রাখে। রামায়ণকথা, লোককথাগুলো শ্রুতি পথেই মানুষের কাছে আসে। সিনেমা আসলে আর্বান ফোকলোর, বা শহুরে লোকনাট্য। তাই সেইসময়ে সিনেমা এই নীতিটাকে গ্রহণ করেছে।
যাই হোক, তখন সিনেমা খুঁড়িয়ে হোক বা যে করেই হোক দৃশ্য এবং শব্দের মাধ্যমে একটা গল্প বলতে চাইছে। তবে এই গল্প বলার ক্ষেত্রে নতুন পাখা মেলল দুটো ছবির মাধ্যমে। তার একটি ছিল উদয় শঙ্করের পরিচালনায় তৈরি ১৯৪৭ সালের হিন্দি ছবি (তবে কলকাতায় তৈরি হয়েছিল) ‘কল্পনা’। এই ছবিটির মাধ্যমে উদয় শঙ্কর রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন পূরণ করতে চেষ্টা করলেন। নৃত্য যদি স্থবির হয়ে উঠতে পারে সেই থেকে এল ‘কল্পনা’। এছাড়া আরেকটি ছবি আধুনিক যুগের প্রবর্তন করল, তার নাম হচ্ছে ‘ছিন্নমূল’।
আপনার জানলে অবাক হবেন যে, আমি যখন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলাম এবং সেখান থেকে দেশ বিভাজনের উপর যখন একটি এক্সিবিশন করতে গিয়েছিলাম, তখন দেখলাম যে দেশ বিভাজনের উপর ভিজুয়াল মেটেরিয়াল প্রায় কিছুই নেই! স্টিল মেটেরিয়ালের জন্য তখনকার স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে কিছু ছবি কিনতে হয়েছিল কিন্তু ভিজুয়াল মেটেরিয়াল প্রায় নেই বললেই চলে। নিমাই ঘোষের এই ‘ছিন্নমূল’ সিনেমাটিই একমাত্র সম্বল। এই নিমাই ঘোষ কিন্তু ফটোগ্রাফার নিমাই ঘোষ নন। এই নিমাই ঘোষ সত্যজিৎ রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি একটিমাত্র বাংলা ছবি করার পর ব্যর্থ হয়ে তামিল ছবি শুরু করেন। ক্যামেরাম্যান হিসেবে তারই পথের পাঁচালী করার কথা ছিল, কিন্তু ডেট দিতে পারেননি বলে সুব্রত মিত্র চলে আসেন। এই নিমাই ঘোষের হাতে সে সময় অত্যন্ত অল্প টাকা ছিল। আজ আমরা যারা ছবি তুলি তারা মনিটরের মাধ্যমে দেখতে পাই ছবিটা কেমন হচ্ছে। কিন্তু সেই যুগে মনিটরের মাধ্যমে দেখা যেত না। তাই একসাথে অনেকগুলো ছবি তুলে অন্য মেশিনে ফেলে দেখতে হত তার এক্সপোজার কেমন। ফলে তা খুব খরচসাপেক্ষ ছিল। নিমাই ঘোষ ১:১ অর্থাৎ প্রতিটি ছবি একটি টেকেই ওকে হবে এই হিসেবে শিয়ালদহ স্টেশন এবং তখনকার লেক ক্যাম্পের বস্তিতে ছবিগুলো তোলেন। ফলে আমাদের এই সময়ের একমাত্র ভিজুয়াল ইলাস্ট্রেশন অফ হিস্ট্রি অর্থাৎ রিফিউজিরা কীভাবে ওই হোগলার ঘরে থাকত; যেগুলো ট্রাংগুলার ছিল, যা আজ আর কোলকাতায় দেখা যায় না, তারা রাস্তায় কীভাবে খাবার কুড়িয়ে খেত, কীভাবে কুকুরের সঙ্গে মারামারি হত, কীভাবে মৃত একটা বাচ্চা হয়তো পড়ে আছে আর তার পাশে মানুষ খাবার কুঁড়িয়ে খাচ্ছে সেসব তুলে রেখেছেন। এই যে ১০ মিনিটের রিল – এ মনে হয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক অলৌকিক সম্পদ। এবং নিমাই ঘোষ যে এই ছবিগুলো করেছিলেন একেবারেই নন-প্রফেশনালদের নিয়ে। অভিনেতা ছিলেন গঙ্গা চরণ বসু, ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য, শোভা সেন – এরা সকলেই তখন আই.পি.টি.এ. কর্মী এবং কেউ সিনেমা করেননি। তাদের দিয়ে এত ভালো কাজ ভাবা যায় না। স্বর্ণকমল বসুর গল্প অবলম্বনে নিমাই ঘোষ এই ছবিটি তৈরি করেছিলেন।

ছিন্নমূল ছবির একটি বিজ্ঞাপন
এই ছবিটি দর্শকদের কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত এবং ফিল্ম হিস্ট্রিতে যার কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় সেই রুশ পরিচালক পুদস্কিন যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি এই ছবিটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান, ভারতীয়রা এত কম রসদে এত ভাল ছবি বানাল কিভাবে! এই ছবিটি তিনি দেখেন এবং দেশে ফিরে গিয়ে বিখ্যাত প্রাভদা পত্রিকার প্রথম পাতায় এই ছবিটির অত্যন্ত প্রশংসা করেন। আজ হয়তো সেই সোভিয়েত ভেঙে গেছে, কিন্তু মনে রাখবেন সেই যুগে যখন স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, সেই সময় তিনি নিমাই ঘোষের এই ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটি সম্ভবত নিমাই ঘোষের কাছে প্রাপ্তির উপরিপ্রাপ্তি।
এবার যে সময়টার কথা আমরা আলোচনা করছি, তখন স্বাধীনতা এসে গেছে। আমাদের সেই স্বাধীনতা একটি বিভক্ত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা মলাটমলিন। আমাদের জাতীয় নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু নিখোঁজ, কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি এবং আমরা ভগ্নহৃদয়ে এই স্বাধীনতাকে দেখছি। এই সময় বাংলায় এক ঝাঁক তরুণ মনে করলেন সিনেমাকে নাচ, গান, ফুল, তারা, চাঁদ, পাখি, পদ্যের মধ্যে আটকে রাখলে চলবে না। সিনেমা প্রকৃত কী তা মানুষকে বোঝাতে হবে। তার ফলে সুকুমার রায়ের ছেলে, তিনি তখন বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করেন এবং একটি সিনেমাও বানাননি, তিনি এবং তার কতিপয় বন্ধুবান্ধ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করলেন। তারা সকলেই পরবর্তীকালে বিখ্যাত হলেন, যেমন – চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার হরিসাধন গুপ্ত, ঋত্বিক ঘটক – এরকম সব মিলে ৩৫ জন ছিল। মৃণাল সেন পয়সা দিতে পারতেন না কিন্তু গিয়ে বসে পড়তেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিতে। তবে কার্ড হোল্ডার মেম্বার ছিলেন না। এটি তৈরির উদ্দেশ্য হিসেবে সত্যজিৎ রায় বলেছেন, ‘ইন দা ইয়ার অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স উই ফরমড দ্য ফার্স্ট ফিলম ক্লাব অফ ক্যালকাটা, দেয়ার বাই শ্যাকলিং উইলিংলি আওয়ারসেলভস টু দ্য টাস্ক অফ ডিফ্যামিনেটিং ফিল্ম কালচার ইভেন আমংস্ট দ্য ইন্টেলিজেন্সিয়া’ অর্থাৎ উনি বুঝতে পেরেছিলেন এমনকি শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও চলচ্চিত্রের রুচির অভাব রয়েছে। চলচ্চিত্র বলতে কখনোই মানুষ কোন সিরিয়াস জিনিস ভাবে না, বরং একটা লঘু বিনোদন হিসেবে দেখে। তাই তারা এক ভিন্ন চলচ্চিত্র রুচি তৈরি করবেন ভেবে এই ফিল্ম সোসাইটির পত্তন করলেন। এই সোসাইটি তৈরি হয় ১৯৪৭ সালে, তখনও পথের পাঁচালী হতে ৮ বছর বাকি।
আমরা যদি ভাবি এই সময়ের সিনেমার ইতিহাস লিখব তাহলে অপরাজিত উপন্যাসটি পড়তে হবে। অপু কলকাতায় এসে প্রথমেই আশ্রয়দাতা অখিলবাবুকে যে প্রশ্নটা করেছিল সেটা পড়লে অবাক হয়ে যাবেন। কারণ বিভূতিবাবুর সিনেমায় খুব আগ্রহ ছিল, এমনকি তিনি সিনেমা বানাতেও চেয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল বিভূতিবাবুর মত একজন ঈশ্বরপ্রতিম সাহিত্যিকও বিশ্বাস করতেন সিনেমার লেখা আর সাহিত্যের লেখা এক নয়। তিনি নিজে সিনেমার জন্য একটা লেখা লিখেছিলেন ‘দম্পতি’ যা বিভূতিবাবুর মত লেখকের হাত থেকে বেরিয়েছিল এটা ভাবতেও কষ্ট হয়। যাই হোক, বিভূতিবাবুর লেখায় অপরাজিত উপন্যাসে অপু তার আশ্রয়দাতাকে প্রথম যে প্রশ্নটি করেন তা হল, যে স্থানে সিনেমা দেখানো হয় সে জায়গাটি এখান হইতে কত দূর? এটা সত্যজিৎ রায়ের অপরাজিততে নেই – তিনি পালটে দিয়েছেন। কেন পাল্টে দিয়েছেন সেটা আমরা পরে দেখব। অপরাজিত উপন্যাসে অপু যে শহরে এল, সেখানে সে তার শৈশবের স্মৃতিচারণে বলছে দেওয়ানপুরের স্কুলে দেখা তার সিনেমার অভিজ্ঞতা, ‘মানুষ দৌড়াইতেছে, কেহ খেলিতেছে’ – এইসব অপু দেখেছিল ছোট ছোট ছবিতে। এখানে থেকে গল্প বলার ছবি অপূর্ব রায় দেখতে চেয়েছেন এবং আমাদের সৌভাগ্য হল আমরাও দেখতে পেয়েছি। সুকুমার রায়ের ছেলে, তিনিও একটা গল্প দেখাতে চেয়েছেন। এবার প্রশ্ন হল তিনি গল্পটা কিভাবে দেখাবেন।
ইতিমধ্যে কলকাতায় দুটো বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে যার প্রভাব অপরিসীম। তার প্রথম ঘটনা হল বিখ্যাত রুশ পরিচালক পুদস্কিন কলকাতা ঘুরে গেলেন। তার সাথে দেখা হয়েছিল সেই সময়ের কলকাতার তরুণ কমিউনিস্ট ছেলেদের, যাদের দুজন সেই সন্ধ্যার বিবরণ দিয়েছেন। তারা সরাসরি পুদস্কিনের সাথে আলাপ করেছিলেন এবং ঋত্বিক ঘটক নিজে সিনেমায় শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য কি তা নিয়ে পুদস্কিনকে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সন্ধ্যের বিবরণে হেমাঙ্গ বিশ্বাসরা লিখেছেন যে তারা খুব অবাক হয়েছিলেন এরকম একটা বাচ্চা ছেলে পুদস্কিনকে কিভাবে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে পারলেন। অর্থাৎ এই ছেলেটি সিনেমা নিয়ে কতটা পড়াশোনা করেছেন। সেই সন্ধ্যায় পুদস্কিনকে দেখভালের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি দুজন ভলেন্টিয়ারকে নিযুক্ত করেছিলেন। তখন তারা দুজনেই একেবারে বাচ্চা ছেলে এবং অত্যন্ত সোৎসাহে পুদস্কিনের সাগরদী করছিল, তাদের একজন হলেন সলিল চৌধুরী এবং অপরজন ঋত্বিক ঘটক।

পুদস্কিন
দ্বিতীয় ঘটনাটা হল বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জ্যঁ রানোয়া (Jean Renoir) ‘দ্য রিভার’ সিনেমাটি তৈরি করার জন্য হলিউড থেকে কলকাতায় এলেন। তার এই আসাটা ছিল বাংলা সিনেমার জন্য সুদূরপ্রসারী, কারণ তিনি ছবিটা তৈরি করার জন্য স্থানীয় কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এই কারণে তিনি স্টেটসম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন যে তার কিছু সহকারী দরকার। এই বিজ্ঞাপন দেখে সত্যজিৎ রায় সহ আরো অনেকে আগ্রহী হয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলেন। অবশ্য তাদের প্রত্যেকেই ইন্টারভিউতে ফেল করেন। যেমন সত্যজিৎ রায়, তাকে দেখেই জ্যঁ রানোয়া বললেন, আপনি তো অত্যন্ত শিক্ষিত, আপনার মত এত শিক্ষিত লোক আমার দরকার নেই। তখন সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, আমি একটু শুটিং দেখতে চাই। তাই সত্যজিৎ রায়ের যখন উইকএন্ড অর্থাৎ ছুটির দিন সেই সময় তিনি জ্যঁ রানোয়ার সাথে শুটিংয়ে ঘুরতে পারেন এই অনুমতি পান। কিন্তু ক্রেডিট টাইটেলে এদের কারো নাম থাকবে না। একমাত্র যার নাম ছিল তিনি হলেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। পরে ঋত্বিক ঘটকের নাগরিক সিনেমায় তিনি ক্যামেরাম্যান হন। আর বাকি সবাই অর্থাৎ সুব্রত মিত্র, সত্যজিৎ রায় এরা সবাই অবজারভার ছিলেন। এমনকি সুব্রত মিত্র, যিনি পথের পাঁচালীর ক্যামেরাম্যান অর্থাৎ এত ভালো ক্যামেরাম্যান তিনিও যখন জ্যঁ রানোয়ার কাছে যান, তাকে সরাসরি বাতিল করা হয়। তারপর সুব্রত মৈত্রের বাবা গিয়ে জ্যঁ রানোয়া সাহেবের কাছে কাকুতি-মিনতি করেন যে ও শুধু শুটিং দেখবে, অন্য কিছু চায় না, তখন তিনি রাজি হয়ে দেখার অনুমতি দেন। কিন্তু এই দেখার সুযোগটা প্রচণ্ড উপকারী হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের নিজের একটি লেখা রয়েছে ‘রানোয়া ইন ক্যালকাটা’, সেখানে সত্যজিৎ রায় বলছেন যে, তিনি এখানেই প্রথম বুঝলেন যে সিনেমার কি-ফ্যাক্টর হল আলো। এখানে সত্যজিতদের হাতে ধরে জ্যঁ রানোয়া সাহেব বুঝিয়েছিলেন যে আমাদের দেখা সবুজ রঙের মধ্যেই কত তফাৎ আছে, ক্যালিফোর্নিয়ার সবুজ আর কলকাতার একটা কচি কলাপাতা সবুজের মধ্যে রংয়ের কত তফাৎ, সকাল এবং সন্ধ্যার আলোর মধ্যে কতটা তফাৎ; যদিও দুটোই কম আলোর সময়। আর সকালের আলো এবং সন্ধ্যের আলোর এই যে তফাৎ সেটা সত্যজিৎ রায় প্রয়োগ করেছেন অপরাজিত সিনেমাটিতে। দেখবেন দশাশ্বমেধ ঘাটে ভোর হচ্ছে আর দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যা হচ্ছে এই দুটো ছবির মধ্যে তফাৎ আছে। এই আলোর দিকটা সত্যজিৎ রায় অনেক যত্ন করে করেছিলেন। সেই প্রথম ভারতীয় সিনেমা বুঝল আলোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, আলো মানেই কম আলো আর বেশি আলো নয়। তার তারতম্য আছে। সন্ধ্যার আলো যেভাবে হয়, সকালের আলো সেভাবে হয় না।

জ্যঁ রানোয়া
জ্যঁ রানোয়া ও পুদস্কিনের আসা, বারবার কলকাতা ফিল্ম সোসাইটিতে বিদেশি ছবি দেখা এবং সত্যজিৎ রায়ের বিলেত ভ্রমণ – এগুলো বাংলা ছবির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞাপনের অফিস সত্যজিৎ রায়কে বিদেশে ট্যুরে পাঠিয়েছিল আর সত্যজিৎ রায়ের নিয়তি হাসছিল। তখন জাহাজে বিলেত যেতে হত। বিলেতে গিয়ে প্রথম দিনই যে কাজটি সত্যজিৎ রায় করলেন, তা হল টেমস নদীর পাশে যেখানে ছবি দেখানো হত সেখানে তিনি প্রথম যে ছবিটি দেখলেন তার নাম হল ‘বাইসাইকেল থিভস’ (Ladri di biciclette)। এই ছবি ওর জীবন পালটে দিল। তিনি ভাবলেন যদি কোনদিন ছবি বানাতে হয় তাহলে এই ছবির মতই ছবি বানাতে হবে। এই ছবিতে তিনি দেখলেন, স্টুডিওর যে বাস্তবতা প্রমথেশ বড়ুয়ারা তৈরি করেছিলেন অর্থাৎ স্টুডিও লাইটিং, তার বাইরের বাস্তবতা সিনেমায় কীভাবে দেখানো হয়। অপেশাদার অভিনেতারা কীভাবে অভিনয় করতে পারেন এবং সিনেমার জীবন কীভাবে বাস্তব জীবনের মত হয়। এখানে জীবনের কোন সাজানো-গোছানো রূপ হয় না অর্থাৎ পাউডার মাখা মুখ আর বাস্তবে ঘামে ভরা মুখ একই হতে পারে না। এই প্রচেষ্টাগুলির ফলস্বরূপ ১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালী মুক্তি পায়। ১৯৫২ সালে তিনি পথের পাঁচালী তৈরি করা শুরু করেন। মধ্যের কিছুদিন অর্থের অভাবে তা থেমেছিল। সত্যজিৎ রায়ের লেখাতেই আছে পরবর্তীকালে এক মধ্যস্থতাকারীনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে কনভিন্স করায়, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সেই ছবিতে টাকা দেন। এই কাজে যে ফাইলটা পাঠানো হয়েছিল সেটা খুব চমৎকার, সে ফাইলটা আমি দেখেছি নিজের স্বার্থে। সে ফাইলটা যখন প্রথমবার বিধান রায়ের কাছে প্রস্তাব করা হয়, সে যুগের তথ্যসচিব প্রথমেই একেবারে সরাসরি নাকচ করেন – এই ধরনের সিনেমা করে সরকারের কোনো লাভ হবে না। এরপর দ্বিতীয়বার যখন একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তি অনুরোধ করেন তখন বিধান রায় টাকাটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সরকার তো নিজে সিনেমার জন্য টাকা দিতে পারে না, তাই তিনি একটি কমিটি করেন। এই কমিটির একজন সেক্রেটারি থাকেন আর থাকেন নাট্যকার মন্মথনাথ রায়। সেক্রেটারি যদিও আগের মতোই অটল থাকেন কিন্তু নাট্যকার মন্মথ রায় সিনেমাটির ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত ছিলেন এবং তিনি বলেন যে এই ছবিটি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। বিধান রায় তার তলায় কিছু লিখে দেননি। তবে পথের পাঁচালী নামকরণ থেকে আমলাদের মনে হয়েছিল এটা হয়তো p.w.d. সংক্রান্ত কিছু বিষয় হতে পারে। তারা মনে করেন এটা পথ উন্নয়ন বা পথ সংস্কারের জন্য কোন প্রজেক্ট, তাই পথের পাঁচালী পেল p.w.d. থেকে গ্রান্ট।
পথের পাঁচালী ছবিটার গুরুত্ব কি? সত্যজিৎ রায় কিন্তু বাংলা সিনেমার পথিকৃৎ নন। তার ছবি করার আগেও বাংলা সিনেমা হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় বাংলা সিনেমায় আধুনিকতার পথিকৃৎ। এমনকি চলচ্চিত্র ভাষার পথিকৃৎ। কেন একথা বলছি? তার কারণ, সত্যজিৎ রায় হলেন প্রথম চলচ্চিত্রকার যিনি উপন্যাসের পুরোটা দেখাতে চাননি। আপনারা যারা পথের পাঁচালী পড়েছেন এবং সিনেমাটার সাথে যদি মিলিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন উপন্যাসের তিনভাগের একভাগ মাত্র দেখানো হয়েছে। তিনি আসলে এখানে উপন্যাসটি দেখাতে চাননি। সত্যি বলতে এই ছবিটিতে তিনি গল্পটাকে একটা কমলালেবুর মতো দুই ভাগে ভাগ করেছেন যার দুদিকে দুটো মৃত্যু। একদিকে দুর্গার মৃত্যু এবং অপরদিকে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু। মাত্র পাঁচটা মূল চরিত্র অর্থাৎ অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়া, পিসিমা। এই পাঁচটা চরিত্র নিয়ে তিনি পুরো গল্পটা বলেছেন। আগে কেবলমাত্র চরিত্রের মধ্যে দিয়েই গল্প বলা হত। অর্থাৎ এতদিন ধরে আমরা গল্পনির্ভর এবং চরিত্রনির্ভর সিনেমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলাম; যদিও তার ভাল বা খারাপের মধ্যে যাচ্ছি না, আপনি যদি আজকে পথের পাঁচালী ছবিটা চোখ বন্ধ করে দেখেন তাহলে বুঝবেন যে এটি প্রায় হাফ সাইলেন্ট মুভি অর্থাৎ খুব বেশি কথা নেই। যা আছে, তা হল নয়েজ এর ব্যবহার। এখানে নয়েজ বলতে ইন্সিডেন্টাল নয়েজের কথা বলা হচ্ছে। গানের ব্যবহার একেবারেই নেই, যদি ‘হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল’কে গান বলেন তাহলে আছে, তা ছাড়া আর কিছুই নেই। আর বাকি ছবিটা নিসর্গকে অসাধারণ ভাবে ধরেছে। নিসর্গ আর মানুষ যে এক সেটা বোঝানো হয়েছে।
ছবির শুরুতে একটা বাচ্চা মেয়ে তার হাতে একটা পেয়ারা, যখন জঙ্গলে লোকাচ্ছে আলোর রিফ্লেক্টর পাতায় ও তার গালে পড়ে। একটা পাতা আর একটা মানুষ যেন এক হয়ে যায়। বা ধরুন বিরাট একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে অপু দুর্গা গরু খুঁজতে যাচ্ছে, সেখানে লং-শটে অপু ও দুর্গাকে খুব ছোট ছোট লাগছে। এখানে পুরো ধানক্ষেতটা আর আকাশটা পরস্পর দিগন্ত চুম্বন করছে – সেখানে চরিত্র কিন্তু শুধু এই দুটো মানুষ নয়। বাংলাদেশ যে এত সুন্দর তা আমরা আগে জানতাম না। যেমন ধরুন পথের পাঁচালীর বৃষ্টি। বৃষ্টি আমরা কমবেশি সবাই দেখেছি কিন্তু সত্যজিৎ রায় যে বৃষ্টি দেখালেন সেটা একেবারেই অন্যরকম। একজন মানুষ মাছ ধরছিলেন প্রথম ফোটাটা তার টাকের উপর পড়ল এবং আমরা দর্শক হিসেবে হেসে ফেললাম। তার পরমুহূর্তেই বাংলার আকাশ-বাতাস ঝেঁপে বৃষ্টি শুরু হল। এবং এই যে বৃষ্টি শুরু হল এর শব্দটা সত্যজিৎ রায় মুছে দিয়েছিলেন। তার বদলে রবি শঙ্করের তৈরি করা একটা তিন মিনিটের দেশ রাগ প্রয়োগ করেছিলেন। পৃথিবীর কোন দেশের বৃষ্টিতেই সেতার বাজে না, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের বৃষ্টিতে সেতার বাজলো। পথের পাঁচালীকে যারা বাস্তব ছবি বলেন তারা আসলে বলতে চান সেটা আক্ষরিক অর্থে বাস্তবতা নয়। দুর্গা যখন জলে ভিজে তার চুলটাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে বা আকাশের দিকে যখন তাকাচ্ছে তখন দেখবেন ফ্রেমের নাম্বার বেড়ে যাওয়ায় ছবিটা স্লো হয়ে যাচ্ছে। উপন্যাসে রয়েছে দুর্গা আশ্বিনের বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর হয় এবং তাতে মারা গিয়েছিল। কিন্তু সিনেমায় এটা হয়ে গেল গরমের বৃষ্টি। এই যে আকাশে মহাপ্রলয় এবং তা থেকে দুর্গার মৃত্যু, একে আমরা আলাদা একটা গল্প বলে মনে করতে পারি। কিন্তু তা করবো কি করবো না সেটা অন্য কথা। এবং তারপর যে দুর্গা মারা গেল, সেই দৃশ্য প্রসঙ্গে আমি পরে দুর্গা আন্টি (উমা দাসগুপ্ত)কে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এখানে আপনার অভিনয়টা কি ছিল? এটা এমন একটা মৃত্যুর দৃশ্য যা বলা যায় আজ পর্যন্ত বাংলা সিনেমায় সবচেয়ে বিখ্যাত মৃত্যুর দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি। দুর্গাকে শুধু বলা হয়েছিল যে তুমি শুয়ে পড়ো আর তোমাকে কিছু করতে হবে না। শুধু যখন বলব তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলবে। চড়া একটা লাইট, তাই দুর্গার মুখটা ঘেমে যাচ্ছে। দুর্গা বারবার নিঃশ্বাস ফেলছে এবং মাথা নাড়ছে। ক্যামেরার ক্লোজ শটে দুর্গার মুখের দিকে তাক করে আছে। আর পাশে একটা ফ্যান চালিয়ে জানালার পর্দাগুলোকে নাড়ানো হচ্ছে। আমরা আজও যখন সেই দৃশ্যটা দেখি তখন মনে হয় দুর্গার শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তাঁর শেষ মুহূর্ত সমাগত। ফ্যানের হাওয়ায় পর্দা নড়ছে তাতে মনে হচ্ছে ঝড় ঢুকে পড়ছে ঘরে। এরপর একটা আলোর ঝলকানি হল মানে বাজ পড়ল, তারপরেই দুর্গা চলে গেল। এই যে অসাধারণ দৃশ্য এটা সত্যজিৎ রায় করেছিলেন খুব অল্প পয়সায়। এমনকি তারপরের দিনের দৃশ্য করতে সত্যজিৎ রায়ের হয়তো আরও বেশি খরচা হয়েছিল। কারণ চারিদিকে জল জমে আছে, নানারকম আবর্জনা তার মাঝে একটা ব্যাঙ মরে উল্টো হয়ে পড়ে আছে। সত্যজিৎ রায় জানতেন যে এই যে মরা ব্যাঙটা পড়ে আছে এটা দেখাতে গেলে ব্যাঙটা কিনতে হবে আর কিনতে গেলে পয়সার দরকার। এবং এই দাম যেটা লাগে সেটা কিন্তু খরচা করতে হয় সিনেমায়। এটা সত্যজিৎ রায় শিখলেন।
আরেকটা বিষয় হল স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের কিন্তু কিছু ভুল হয়েছিল। যেমন পথের পাঁচালী কথাই বলা যায়। পথের পাঁচালী প্রথম দৃশ্যের কথা ভাবুন। আমি যখন কলামন্দিরে ছিলাম তখন সৌম্যেন্দুদা আসতেন পড়াতে। মাঝে মাঝে সৌমেন্দুদার সাথে কথা হত। অনেক গল্প হত পথের পাঁচালী নিয়ে, কারণ তিনি ছিলেন পথের পাঁচালীর অপারেটিভ ক্যামেরাম্যান। সৌমেন্দুদা বলেছিলেন একেবারে ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শট তোলা হয়েছিল জগদ্ধাত্রী পূজার দশমীর দিন। তখনো কাশবন আছে, কাশবনের সবটাই প্রথম শট। এই ভুলটা অবশ্য সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছিলেন। দুর্গাকে কাশবনে দেখে সত্যজিৎ রায়ের খুব ভাল লেগেছিল। তিনি অনেকগুলো ক্লোজ সট নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন পরে এগুলোকে জুড়ে দেবেন। ফলে সেদিন অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যায়। যে ছবি তিনি একদিনে তুলবেন ভেবেছিলেন সেটা পরের সপ্তাহে তোলার প্রয়োজন পড়ে গিয়েছিল। যেহেতু তখন তিনি চাকরি করতেন তাই প্রতিদিন শুটিং করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই পরের সপ্তাহে তিনি গেলেন কিন্তু গিয়ে আর জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। জায়গাটা ছিল বর্ধমানের পালসিট, যেখানে আমরা ল্যাংচা খাই অর্থাৎ শক্তিগড় তার ঠিক আগে। সে যায়গাটা ছিল পালসিটের রেল লাইনের ধারে একটা কাশবন। তিনি তো জায়গাটা খুঁজছেন, তখন এক বৃদ্ধ সেখানে ঘোরাঘুরি করছিলেন। জানতে চাইলেন আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন? তারপর নিজেই বললেন যে, আপনারা তো গত রবিবার এখানে এসেছিলেন অনেক ছবি তুললেন। তখন ওই বৃদ্ধকে সত্যজিৎ রায় জিজ্ঞাসা করলেন এখানের কাশবনটা গেল কোথায়? বুড়ো তখন হেসে বললেন আপনারা তো শহরের লোক, তাই জানেন না। কাশতো সিজেনাল ফ্লাওয়ার। সে তো কবেই গরু-মোষ খেয়ে গেছে। সে কি আর এতদিন থাকে! এর ফলে ছবিটা এক বছর পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল, কারণ কাশ তো আর কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যাবে না। হিন্দি সিনেমা হলে হয়তো কৃত্রিম কাশ করে নেওয়া হত, কিন্তু তাতে তো আর এই ইফেক্ট আসতো না। কিন্তু সত্যজিৎ রায় একগুঁয়ে। তিনি ‘এ লং টাইম অন আ লিটিল রোড’ নামে একটি লেখা লিখেছিলেন এবং তাতে নিজেই ব্যাখ্যা করেছিলেন যে শহরের মানুষ হওয়ায় এবং জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় কোথায় কোথায় তার সমস্যা হয়। এ ছবিতে তিনি সংলাপ খুব কম রেখেছিলেন কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল পিকটরিয়ালকে চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়া। পরবর্তীকালে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কনভোকেশনে তিনি বলেছিলেন ফিল্ম ইজ টু ন্যারেট উইথ ইমেজেস, নট ইন আইডিয়াস। অর্থাৎ ফিল্ম ইমেজ দিয়ে কথা বলবে, ধারণা দিয়ে নয়। একটা গল্প আছে যাকে মুখে বললেই হল না বা পাত্র-পাত্রী দিয়ে বলে গেলেই হল না তাকে দৃশ্য দিয়ে বোঝাতে হবে। কিভাবে দৃশ্য দিয়ে বোঝাতে হবে তার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ওর ধারণা ছিল। একটা জিনিস জানবেন সংলাপ অত্যন্ত ঝামেলার জিনিস। সংলাপ যদি স্টুডিওর বাইরে নেওয়া হয় তাতে অনেক নয়েজ আসে আর এই নয়েজের জন্য যদি সংলাপ ঠিক ঠিক ভাবে বোঝা না যায় তাহলে সেই দৃশ্যগুলি স্টুডিওতে রিটেক করতে হয়। সাউন্ড রিরেকর্ডিং অত্যন্ত খরচের ব্যাপার। তিনি চাইছিলেন যত কম খরচে সরাসরি এই শব্দকে তোলা যায়। কারণ অত্যন্ত কম খরচে তিনি ছবিটা তৈরি করেছিলেন। এমনকি সত্যজিৎ রায়ের যিনি আজন্মসঙ্গী মানে পথের পাঁচালী থেকে আগন্তুক পর্যন্ত তার প্রতিটি ছবি এডিট করেছেন অর্থাৎ দুলাল দত্তের একটি বড় ইন্টারভিউ এখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। এই ছবিতে শটের সংখ্যা কম ছিল সেটা দুলালবাবু পয়েন্ট আউট করেছিলেন সত্যজিৎ রায়কে। কিন্তু ছবিটা নিউইয়র্কে দেখানোর জন্য তৈরির তখন এতই তাড়াহুড়ো যে আর ছবি রিশুট করা যাবে না তাই ওই কম সর্ট নিয়েই ছবিটা তৈরি হয়ে যায় এবং ছবিটা হয়ে ওঠে এশিয়ার মুখ। আমাদের গর্ব লাগে এটাই ভাবতে যে যারা পৃথিবীর সিনেমার যে ইনস্টিটিউটেই যান না কেন, তার দেওয়ালে কাশবনের মাঝে অপু দুর্গার মুখ এবং এই ছবিটাই এশিয়ার ছবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

সত্যজিৎ রায় আসলে আমাদের যেটা শেখালেন সেটা হল ইমেজের গুরুত্ব। ইমেজ দিয়ে কথা বলা এবং সেই কথার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন ধরুন ‘অপরাজিত’ সিনেমাটা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা উদ্দেশ্যে অপরাজিত উপন্যাসটি লিখেছিলেন আর সত্যজিৎ রায় এটা নিয়ে সিনেমা তৈরি করছেন ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতা উত্তর একটা দেশ যেখানে প্রথমবারের মত নির্বাচন হয়ে গিয়েছে, সাথে সংবিধান, পার্লামেন্ট, প্ল্যানিং কমিশন – এগুলো তৈরি হয়েছে, একটা ডেমোক্রেটিক, নন ক্যাপিটালিস্ট ডেভলপমেন্ট-এর কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তিনি মিক্সড ইকনোমির কথা বলছেন, একটা উন্নয়নের রেখা দেখা যাচ্ছে। তখন যদি একটা সাধারণ নাগরিকের কথা ভাবা যায় তিনি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের নাগরিক হবেন এমন ভাবাটা কঠিন এবং সত্যজিৎ রায়ের কোন দায় নেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলা। আপনারা মিলিয়ে দেখবেন, সত্যজিৎ রায় অপুর যে প্রজেক্টটি নিচ্ছেন সেটা একেবারেই এনলাইটেনমেন্টের অপু অর্থাৎ যে পরিবার থেকে সত্যজিৎ রায় এসেছিলেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং সুকুমার রায়ের পরবর্তী প্রজন্মের সত্যজিৎ রায় তারা পারিবারিকভাবে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, এমনকি বাংলায় তাদের মত বেশ কিছু পরিবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাকে আমরা নাইন্টিন সেঞ্চুরি রেনেসাঁস বলতাম এবং ভুল করে বলতাম কিন্তু বলতাম, সেটা যে স্তরেরই হোক, এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা আজকাল চলছে ইতিহাসের নানা স্তরে, এমনকি আমরা আগে যত সহজে সুশোভন সরকারের ‘নোটস অন বেঙ্গলি রেনেসাঁস’ পড়তাম তা আজকাল পড়ি না, কারণ নতুন নতুন অনেক ধরনের জ্ঞানের রূপান্তর ঘটছে। তো যাই হোক, অপুকে একজন মডেল সিটিজেন করার জন্য গ্রামের মনসাপোতা হাই স্কুলে যখন একজন স্কুল ইনস্পেক্টর এলেন, আপনারা ভাবুন, সত্যজিৎ রায় কতটা সুপরিকল্পিতভাবে সিনেমাটি করছেন, তিনি ক্লাসে এসে অপুদের জিজ্ঞাসা করলেন, একটা কবিতা বল তো। তখন প্রথম ছেলেটি পারল না, অপু উঠে দাঁড়িয়েই ‘কোন দেশেতে তরুলতা/ সকল দেশের চাইতে শ্যামল?/ কোন দেশেতে চলতে গেলেই/ দলতে হয় রে দুর্বা কোমল’ শুনেই ইন্সপেক্টর খুশি হয়ে গেলেন এবং কিছু গ্রান্ট দিয়ে দিলেন। আসলে তখন দেশ বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে তা ধরার চেষ্টা করছেন। লক্ষ্য করবেন, আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কিন্তু ‘দেশ’ শব্দটা well-defined নয়। যখন আমাদের বাড়ির কাজের মানুষরা ‘দেশে’ যান, সেই দেশটা কিন্তু ভারতবর্ষ নয়। সেটা লক্ষীকান্তপুর, জয়নগর, বারুইপুর এইরকম। আমাদের ছোটবেলায় হাজারিবাগ ঘুরতে যাওয়ার সময় যখন মা বলেছিলেন, ‘বিদেশ বিভূঁইয়ে যাচ্ছিস, একটা আলোয়ান নিয়ে যা’ তখন কিন্তু এই বিদেশ জায়গাটা ইংল্যান্ড, আমেরিকা ছিল না। তখন হাজারিবাগটাও ছিল বিদেশ, জয়নগরটাও বিদেশ, এমনকি কলকাতাটাও হয়তো বিদেশ হতে পারে।
এই যে দেশের ফর্মেশন অর্থাৎ কান্ট্রি বা মডার্ন স্টেটের কনসেপ্ট তৈরি হচ্ছে, এটাই ইংরেজদের অবদান। এটা আধুনিকতারও একটা কম্পনেন্ট ছিল। সত্যজিৎ রায় কম্পনেন্টটা আনতে চেয়েছিলেন। এমনকি অপুকে সেই ইন্সপেক্টর এপ্রিশিয়েট করে বলছেন, যদি ভাল ছেলে হতে চাও তাহলে কেবল টেক্সট বই পড়লেই হবে না, বাইরের বইও পড়তে হবে। এই ‘বাইরের বই’ বলতে তিনি অ্যাডভেঞ্চার, দেশভ্রমণ এমনকি বিজ্ঞানের বইও উপহার দিলেন। এর ফলে যেটা হল, অপু বাড়িতে গিয়ে সাইফুনের টেস্ট করল, অপু মাকে গ্রহণ বোঝালো, যে এটা রাহু-কেতুর ব্যাপার নয়, ছায়া পড়ে ইত্যাদি। অপু জুলু উপজাতির মানুষ হয়ে মাকে দেখালো অর্থাৎ কার্ল মার্কস ভেবেছিলেন কাস্ট ভিলেজ কমিউনিটি সোশ্যাল সেটআপ অর্থাৎ গ্রামগুলো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিট, সেই ইউনিট ভেঙে পড়ছে এবং দেশের মাত্রাটা বড় হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে আমরা আধুনিক যুগে ঢুকে যাচ্ছি এবং আমাদের আধুনিকতা সম্বন্ধে একটা ধারণা হল, আমরা অ্যালবার্ট হলে দেশ উদ্ধার করলাম জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্ল রায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন, এই যা হল এতে অপু একটা জগত থেকে অন্য একটা জগতে প্রবেশ করল। গ্রামের জীবনে অপুর মা অপুকে ছাড়ছিল না কারণ তার ধারণা ছিল পুরুতের ছেলে পুরুত হবে। অর্থাৎ এইযে জন্মানুক্রমিক পেশা, সে সম্পর্কে কালমার্কস তার প্রলেতারিয়েত এন্ড বুর্জোয়াতে বলছেন বুর্জোয়াজি এসে নির্মমভাবে এই বাঁধাটাকে ভেঙে ফেলছে। অর্থাৎ এখন পুরুতের ছেলে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারে। এছাড়াও প্রিস্ট বা ল-ইয়ার ইত্যাদি পেশা যা কিনা একটা নির্দিষ্ট মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ওয়েজ লেবারে রূপান্তরিত হতে লাগলো। অপু কলকাতা এল হাতে একটা গ্লোব নিয়ে। সে হ্যারিসন রোডের সামনে এসে দাঁড়ালো। দেখবেন সত্যজিৎ রায় এই হ্যারিসন রোড লেখা সাইনবোর্ডটা অনেকক্ষণ ধরে দেখিয়েছেন। এর কারণ হ্যারিসন রোড ১৯৫৬ সালে হাওড়া এবং কলকাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পথ এবং এই রাস্তার উপর এশিয়ার সবচেয়ে বড় ট্রেডিং সেন্টার বড়বাজার অবস্থিত। অর্থাৎ গ্রাম থেকে এসে এই যে শহর এবং একটা বাণিজ্যপথ, এনিয়ে কার্ল মার্কস, জর্জ সিমেল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের প্রত্যেকটি তাত্ত্বিক যেমন ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বিস্তর লিখেছেন। কিন্তু অপরাজিত ছবিটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব এটা মূলত গ্রাম থেকে শহরে আসার রূপকথা। এটাকে অনেক ভাবে বলা যায়। একভাবে সত্যজিৎ রায় বলেছেন অন্যভাবে বলেছেন উত্তম কুমার।
১৯৫৫ সালে নির্মিত শাপমোচন যদি দেখেন তাহলে দেখবেন, সেই একই গল্প যেখানে গ্রাম থেকে শহরে একজন মানুষ আসেন। একটা পপুলার প্লেনে শাপমোচন যেমন দেখিয়েছে আর্টের প্লেনে অপরাজিত সেই কাজটাই করে এবং উত্তম কুমার ও অপূর্ব কুমার রায় এই দুজনই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকতার কথা বলে। বিভূতিভূষণের মূল গল্পে অখিলবাবু যে প্রেসের ম্যানেজার তা কোথাও উল্লেখ করা নেই। সত্যজিৎ রায় অখিলবাবুকে একটা জীবিকা দিলেন। অপু হেঁটে চলে এল পটুয়াটোলা লেন। সেখানে এসে সে রয়েল প্রেস দেখল। প্রেসে এসে সে ম্যানেজারের কাছে হেডমাস্টারমশায়ের চিঠি দেখালো এবং আশ্রয় পেল দোতালায়। দোতলায় এসে জানালার পাশে গ্লোবটাকে রাখল এবং তার পরে মাকে চিঠি লিখল। এই চিঠির শেষ লাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল, ‘আমার ঘরে একটি বৈদ্যুতিক বাতি আছে’। এই কথাটা দেখে আমাদের গাঁ শিউরে ওঠে। অর্থাৎ এই যে বৈদ্যুতিক বাতি যা কিনা আসলে একটা সভ্যতার স্তর; মনসাপোতা গ্রামে তো আর বৈদ্যুতিক বাতি ছিলনা। সত্যজিৎ রায় গল্পে প্রেস এনেছেন তারও একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। মার্শাল ম্যাকলনের দ্বিতীয় বই অর্থাৎ ‘গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি’ সত্যজিৎ রায় সম্ভবত পড়েননি। তাতে দেখা যায় গুটেনবার্গ অক্ষর আবিষ্কার করার পর পাদরিদের হাত থেকে বাইবেল সাধারণ মানুষের হাতে চলে গেল। অর্থাৎ খ্রিস্ট কি বলেছেন তা আর রিলিজিয়াস এজেন্সি থেকে আমাদের জানতে হল না। আমাদের শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ শুরু হল। আজ আমরা সাক্ষর হিসেবে একটা কাজ অন্তত করতে পারি, একজন নোবেল প্রাপ্ত মানুষ যে বইটা পড়তে পারেন আমিও সেই বইটা পড়তে পারি কারণ সেটা ছাপা অবস্থায় আমার হাতে আসতে পারে।
অপরাজিততে অপু প্রতিটি নতুন জিনিসের মধ্যে একটি অর্থ বের করছে। তার ক্লাসের মধ্যে মেটোনিমি এবং মেটাফর এর অর্থ খুঁজছে। বিজ্ঞানের গবেষণাগারগুলিতে গবেষণার মাধ্যমে সত্য নির্মাণ হচ্ছে। এর ফলে অপুর ভোকাবোলারি পাল্টে যাচ্ছে। সে বলছে ‘দুটাকা দিয়ে মাকে ম্যানেজ করে নেব’। ১৯৫৬ সালে মাকে ‘ম্যানেজ করা’ মোর দ্যান আ রেভোলিউশন। ভাবুন কি অসভ্য ছেলে, যে বামুনের ঘরের বউ হওয়া সত্যেও এমনকি বিধবা হয়েও পরের বাড়ীতে কাজ করছে টাকা রোজগারের জন্য তাকে ‘ম্যানেজ করে নেওয়া’র কথা বলছে। আর অপুর তো কোন প্রলোভন নেই, সে তো গরিবের ছেলে। রাতে প্রেসের কাজ করে আর দিনেরবেলায় পড়াশোনা করে। সে তো বিলাসবহুল জীবনযাপন করে না, তাহলে শহরে তার এত আকর্ষণ কেন? সে কেন মাকে ভুলে যেতে চায়? সে কেন গ্রামের গণেশ পুজোতে গ্রামে যেতে চায় না? এর উত্তর যদি আপনি খুঁজতে চান তাহলে দেখবেন সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসের অনেক প্রশ্ন এই ছবিটির মধ্যে লুকিয়ে আছে। গ্রাম জীবন থেকে শাহরিক রূপান্তরের যে ইতিবৃত্ত অপরাজিত রচনা করে তা বোঝার দরকার আছে।
বা ধরুন, নিজের সিনেমা দেখে যে প্রতিক্রিয়া ১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ রায় করেছিলেন, কারণ তিনি এই সময় এই অংশের তৃতীয় ছবিটি করেন অর্থাৎ ‘অপুর সংসার’, সেখানে একটি দৃশ্য আছে যে নববিবাহিত দম্পতি একটি সিনেমায় যাচ্ছে। অপূর্ব কুমার রায় এবং তার স্ত্রী অপর্ণা অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং শর্মিলা ঠাকুর। সেখানে শর্মিলা ঠাকুর অবাক হয়ে একটা সিনেমা দেখছে এই সিনেমাটার নাম হচ্ছে ‘ভক্ত ধ্রুব’। সেখানে একটা স্পেক্টকেল ফর্মেশন অর্থাৎ ধ্রুবর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য বিভিন্ন দেবতারা বজ্র ইত্যাদি ইত্যাদি ফেলছেন অর্থাৎ মিথিক্যাল এবং রিলিজিয়াস ছবি।
স্বয়ং সত্যজিৎ রায় এই ছবিটি দেখেছিলেন, যখন তিনি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে পড়তে যান। তার কলাভবনে পড়তে মোটেই ভাল লাগেনি কারণ তখন তিনি শহরের ছেলে ছিলেন। নেহাত পড়াশোনার জন্য শান্তিনিকেতন যান। কিন্তু কলকাতায় তিনি সিনেমা দেখতেন আর তখন শান্তিনিকেতন ছিল নেহাতই গ্রাম। এখানে সিনেমা ছিল না। তিনি একবারই শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে খড়ের ছাউনি দেয়া একটা ঘরে সিনেমা দেখেছিলেন এবং সেই সিনেমাটা ছিল ভক্ত ধ্রুব। স্বাভাবিকভাবেই সেসব বাংলা ছবি দেখে তার খুব একটা আশাপ্রদ মনে হয়নি, এমনকি ভক্ত ধ্রুব দেখেও তার ভাল লাগেনি। তিনি লিখেছিলেন কলকাতার হলে ‘কেন সিটিজেন’ এল এবং চলে গেল আর আমি এখানে বসে পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার ছবি আঁকছি। এটা আসলে খুব আক্ষেপের কথা, আনন্দের মোটেই নয়।
যাইহোক এই ভক্ত ধ্রুবতে ডিজলভ করছে, এখানে ডিজলভ বলতে আসলে কাট নয়, মানে সাহিত্যের ভাষায় দাড়ি ফুলস্টপ নয় বরং কমা বলতে পারা যায় অর্থাৎ একটা দৃশ্য থেকে আরেকটা ঢোকা, সেই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে অপু এবং অপর্ণা এককা গাড়ির মধ্যে ‘ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,/ কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে/ বাঁধি নীড়,থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,/ নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম। অর্থাৎ আধুনিক প্রেমের গল্প। এখানে অপর্ণা সন্তানসম্ভবা এবং সে বাপের বাড়ি চলে যাবে এবং অপু তার নিষেধ অমান্য করে একটা সিগারেট জ্বালিয়েছে এবং তাদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে আজ এককাগাড়িতে অনেক খরচা হয়ে গেল ইত্যাদি। এর মধ্যে অপর্ণা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দেয়, আর সেই দেশলাই কাঠির আলোতে অপর্ণার কি সুন্দর মুখ, যেন মনে হচ্ছে বাংলার মুখ, রূপসী বাংলার। এই যে দৃশ্য এটা দু’ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এটা সত্যজিৎ রায় সুব্রত মিত্রদের আন্তর্জাতিক অবদান। একটা নিউ রিয়ালিস্টিক লাইভলিহুড। একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে কিন্তু কখনোই অপর্ণার মুখ বা অপুর মুখ দেখা সম্ভব নয়। এটা আসলে সত্যজিৎ রায়ের একটা প্রিটেনশন বা ভান। এটা যদিও একটা বানানো আলো কিন্তু আপনি বুঝতেই পারবেন না সেটা বানানো। মনে হবে একেবারেই ন্যাচারাল লাইট। অর্থাৎ এই যে একটি সামাজিক রূপান্তর, ধর্মীয় আখ্যাণ থেকে পারিবারিক জীবনে বা পৌরাণিক থেকে দাম্পত্য জীবনে এই জায়গাটা আধুনিকতার অন্যতম প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটা তিনি সম্পন্ন করেন অপুর সংসার চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে। এসব ছবিগুলোর গুণ অসাধারণ, যা বলে শেষ করা যাবে না।
আসলে এখানটায় বলার চেষ্টা হচ্ছে যে আজ যখন সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে তাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে তখন সেই দেখাটা একটা ইতিহাসের পথ ধরে হতে পারে। যদি একটা হঠাৎ করে সিনেমা বেছে নেওয়া হয় যেমন ধরুন ‘দেবী’ যেটা ১৯৬০ এর ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পায়, এই ছবিতে আপনি যদি দেখেন দেবী কুসংস্কারের শিকার এবং সত্যজিৎ রায় সেটা দেখাচ্ছেন। এতে কোন ভুল নেই কারণ পৃথিবীর অনেক মানুষই এই ধরনের জিনিসে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ছবিটি যখন আপনি আজকের সময়ে দেখবেন, তখন দেখবেন তখন আরও বড় ক্যানভাসে তা ধরা পড়বে। দেবী দয়াময়ী তার শ্বশুরের সেবা-যত্ন করছেন। তিনি সন্ধেবেলায় শ্বশুরমশাইয়ের পায়ে তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন এবং শ্বশুরমশাই জিজ্ঞাসা করছেন সে কলকাতা থেকে চিঠি লিখে তো? অর্থাৎ শ্বশুর এবং পুত্রবধূর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে। শ্বশুরের সব কথাতেই দয়াময়ী কাঁধ নাড়ছেন, ঘোমটা দেওয়া কারণ সেইসময় শ্বশুরের সাথে সরাসরি কথা বলার কোন রেওয়াজ ছিল না। যাই হোক, এই দৃশ্যটিতে মনে রাখবেন অন্তত সিনেমায় ছবি বিশ্বাস তত বৃদ্ধ নন। খেয়াল করবেন সেই রাতেই ঘুমের ঘোরে ছবি বিশ্বাসের স্বপ্নে দেবীর যে ত্রিনয়ন তা আমাদের দয়াময়ীর মুখের সাথে মিলে গেল। এবং তার পরক্ষণেই শ্বশুরমশাই দরজা খুলে ঘুমন্ত পুত্রবধূর পায়ে জড়িয়ে ধরল এবং ‘মা তুই ছলনা করেছিস’ ইত্যাদি বলতে শুরু করল। এতে পুত্রবধূ লজ্জায় সংকোচে কুঁকড়ে গেল এবং পরক্ষণেই তার পূজা শুরু হয়ে গেল। ছবিটি একটি অ্যাক্সিডেন্টে শেষ হল। দয়াময়ী পাগল হয়ে সরষে খেতের মধ্যে ছুটে গেল। ছবিতে দয়াময়ীর মৃত্যু আমরা দেখিনি কিন্তু এই ছুটে যাওয়াটা আমরা দেখেছি। আজ, অর্থাৎ সিনেমাটা তৈরি হওয়ার ষাট বছর পরে আমরা ছবিটার আলাদা ইন্টারপ্রেট করতে পারি। প্রভাত কুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি দিয়েছিলেন এবং এই গল্পটির চিত্রনাট্য তৈরি করে সত্যজিৎ রায় ছবি তৈরি করেন। এটাকে একটা পিরিয়ড পিস হিসেবে ভাবা যায় কারণ সেই যুগের কুসংস্কার এবং দয়াময়ীর স্বামী কলকাতায় পড়াশোনা করেন তিনি বাড়িতে এসে বলছেন যে ‘কি সব পাগলামি হচ্ছে’ ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ কলকাতার উচ্চশিক্ষিত নব্যশ্রেণীর মানুষ এবং ইয়ং বেঙ্গলের সময় যা যা হয়েছিল সেসব। কিন্তু এই ঘটনার অনেকগুলো মানে আছে। তার একটি মানে যদি আপনি দেখেন, ধরুন ফ্রয়েডীয় সাইকোএনালিসিস দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখবেন দয়াময়ীর এই পায়ে হাত দিয়ে তেল দেওয়ায় শ্বশুরমশাইয়ের কোন একটা প্লেজার তৈরি হচ্ছে। দয়াময়ীর সেই তৈলমর্দনে শ্বশুরমশাইয়ের যে শারীরিক আহ্লাদ তৈরি হচ্ছে সেই নিষিদ্ধ আহ্লাদের ফ্রয়েডীয় ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে পুত্রবধূকে দেবীতে রূপান্তরিত করা, ঘুমের মধ্যে আনকনসাসলি, যদিও এই দেবীতে রূপান্তর তার জীবনে অভিশাপ ডেকে আনল। অর্থাৎ এইভাবে যদি আমরা সিনেমাকে দেখি তাহলে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে সিনেমা কেবলমাত্র একটি আর্টফর্ম নয় বরং তার মধ্যে একটি সামাজিক বয়ান আছে। সেটা একটা টেক্সট হিসেবে কাজ করতে পারে বা একটা কালচারাল অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। শুধুমাত্র একটা আর্ট অবজেক্ট নয়, সাইট অফ কালচারাল রেফারেন্স অর্থাৎ কেউ শুধুমাত্র সাইকোএনালাইসিস করার জন্যই এই ছবিটি দেখতে পারেন। সেখানে সত্যজিৎ রায় ছোট আর্টিস্ট নাকি বড় আর্টিস্ট – তা বিবেচনা করার দরকার নেই।
এই আলোচনা আমরা এখানেই আপাতত ছেদ টানছি, যদিও এটা হঠাৎ করলাম এমন নয়, কারণ ঠিক যে সালে দেবী তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ ১৯৬০ সালে, ঠিক একই সময়ে পাশাপাশি আরেকটা ঘরে আরেকটা একই ধরনের ছবি তৈরি হচ্ছিল। দেবী মুক্তি পায় ফেব্রুয়ারিতে, আর পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল মুক্তি পেল দ্বিতীয় ছবিটি। এই দ্বিতীয় ছবিটি তৈরি করছিলেন ঋত্বিক ঘটক, ছবিটি হল ‘মেঘে ঢাকা তারা’। আসলে সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক দুজন ছিলেন আধুনিকতার বিপরীতমুখী পিতা মাতা, অর্থাৎ হরগৌরী বলতে পারেন। এই দুজনেই আধুনিক সময়ের নারী সমাজকে একই সময় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন’ দুটো ছবির মধ্যে দিয়ে এবং এদের পরিণতি প্রায় একই হয়েছিল। মেঘে ঢাকা তারা ছবিতে নিতার মৃত্যু আমরা দেখিনি কিন্তু তাকে বলতে শুনেছি ‘দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম’, যদিও বাঙালি দর্শকদের কাছে ‘বাঁচতে চাই’ এমনই একটা সংলাপ আমর হয়ে আছে, সে যাই হোক, অন্যদিকে দেবী দয়াময়ী সেও পাগল হয়ে সরষে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলে গেল অর্থাৎ কারও মৃত্যুই আমরা দেখিনি কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে তাদের সেখানটাতেই শেষ পরিণতি হয়েছিল। আপনারা যদি একই দিনে এই দুটো ছবি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন দুজন পরিচালকই নারীর সমস্যা এবং সামাজিক সমস্যা দুটো ভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখেন। সত্যজিৎ রায় দেখেন আমাদের আটপৌরে বাস্তবতার ভেতর কবিতার মধ্যে দিয়ে আর ঋত্বিক ঘটক আমাদের রিলিজিয়াস ফ্রেমে দুটো আর্টিকুলেশন, একটা হল কুমারসম্ভবম্-এর শিব পার্বতীর উপাখ্যান, একটা বিরাট হিন্দু কালচারাল কমপ্লেক্স-এর প্রেমের মধ্য দিয়ে আজাদগড়ের কলোনির একটি মেয়ের ট্রাজেডিকে জুড়ে দেন। এইযে দেখাটা, এটা একটা ঐতিহাসিকভাবে অন্যরকম দেখা। দেবীর দয়াময়ী এবং মেঘে ঢাকা তারার নিতা, দুজনেই খুব নির্মম পরিণামের শিকার। কিন্তু দেখার চোখটা ভিন্ন এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতটাও আলাদা, এমনকি মেকিংটাও আলাদা।
আমরা দেখতে পাই ১৯৬০ সালে চারটে খুব হিট ছবি হয়েছিল, তার প্রথমটি শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে ‘দেবী’ দিয়ে, দ্বিতীয়টি এপ্রিল মাসে ‘মেঘে ঢাকা তারা’, তৃতীয়টি হল ‘বাইশে শ্রাবণ’ এবং চতুর্থটি নভেম্বর মাসে ‘গঙ্গা’। এখানে চার জন নায়িকা অর্থাৎ দেবীতে শর্মিলা ঠাকুর, মেঘে ঢাকা তারায় সুপ্রিয়া চৌধুরী, বাইশে শ্রাবণে মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং গঙ্গায় সন্ধ্যা রায় – এই চারজন নায়িকাকেই চার পরিচালক বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন। একই বছরের এই চারটে ছবিকে ভালভাবে দেখলে আমরা বাংলা সিনেমার আধুনিকতা সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট হলেও ধারণা পেতে পারি। কিন্তু ইতিহাস লেখার সমস্যা হল এই দেখার পুরোটাই আসলে অথার-ভিত্তিক অর্থাৎ পরিচালক ভিত্তিক হয়ে গেল। এছাড়াও অভিনয়ভিত্তিক হতে পারে, টেকনোলজিভিত্তিক হতে পারে আরও অনেক ভাবে হতে পারে।
যাই হোক, আমরা এতদিন ইতিহাস লেখার কোন চেষ্টাই করিনি, শুধু গল্পটাকে জুড়ে দিতাম আর ক্রেডিট টাইটেলটা দিয়ে দিতাম। ইদানীং আমরা এসব নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি এবং আশা করি এই ভাবনা থেকে আমরা কোথাও একটা জায়গায় পৌঁছাবো।
সহায়ক গ্রন্থঃ
১. কালীশ মুখোপাধ্যায়, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস, পত্রভারতী
২. গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, সোনার দাগ, যোগমায়া প্রকাশনী
৩. সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অনভিজাতদের জন্য অপেরা, প্রতিভাস

ভীষণ ভালো তথ্যপূর্ণ এবং মূল্যবান লেখা।
রাশিয়ার পত্রিকার নাম কি পাবদা নাকি Pravda?
খুব ভাল লেখা।
অনেক ধন্যবাদ। আমরা যথাসাধ্য এডিট করে দিলাম।
খুব ভালো লাগল। অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা। সমৃদ্ধ হলাম। লেখককে ধন্যবাদ।
অত্যন্ত উঁচু মানের লেখা । খুব ভাল লাগল । অনেক সমৃদ্ধ হলাম । একটি নিবেদন – ১৯৩৭ সালের “মুক্তি” সিনেমায় কানন দেবীর গানটি ছিল – “ওগো আমার প্রিয় তোমার রঙ্গীন উত্তরীয়” । লেখার সময় কিছু শব্দের ক্রমে কিছু গোলযোগ হয়েছে – যদি সংশোধন করে দেন ভালো হয়। এই গানটির প্রথম কলি টি ছিল – “ আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে ”।
এই তথ্যসমৃদ্ধ লেখাটির পাঠে মগজাস্ত্রকে শানিত করার সুযোগ পেলাম। সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ স্যার🙏🙏🙏
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধটি, যা শেষ পর্যন্ত মগজাস্ত্রকেই শানিত করে। ইতিহাস সময়ের আখ্যান, সময়কেই সে প্রতিনিধিত্ব করে, এই রচনায় সেকথাই বারংবার স্পষ্ট হয়েছে। 🙏🙏🙏 সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই আপনাকে স্যার।
এই লেখা নিঃসন্দেহে বাংলা সিনেমার বিবর্তনের এক নজির। ভীষণ তথ্য বহুল। তবে রেনোযা-র প্রভাব যেমন সত্যজিতের ওপর পরেছিল তেমন পুদস্কিন ঋত্বিককে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল তা না জানতে পারায় সামান্য খচখচানি রয়ে গেল।
অত্যন্ত উঁচু মানের লেখা । খুব ভাল লাগল । অনেক সমৃদ্ধ হলাম । একটি নিবেদন – ১৯৩৭ সালের “মুক্তি” সিনেমায় কানন দেবীর গানটি ছিল – “ওগো আমার প্রিয় তোমার রঙ্গীন উত্তরীয়” । লেখার সময় কিছু শব্দের ক্রমে কিছু গোলযোগ হয়েছে – যদি সংশোধন করে দেন ভালো হয়। এই গানটির প্রথম কলি টি ছিল – “ আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে ”।
‘দেবী’ গল্পটি প্রভাত কুমার রায় নয়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা।
‘দেবী’ গল্পটি প্রভাতকুমার রায়ের নয়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা।