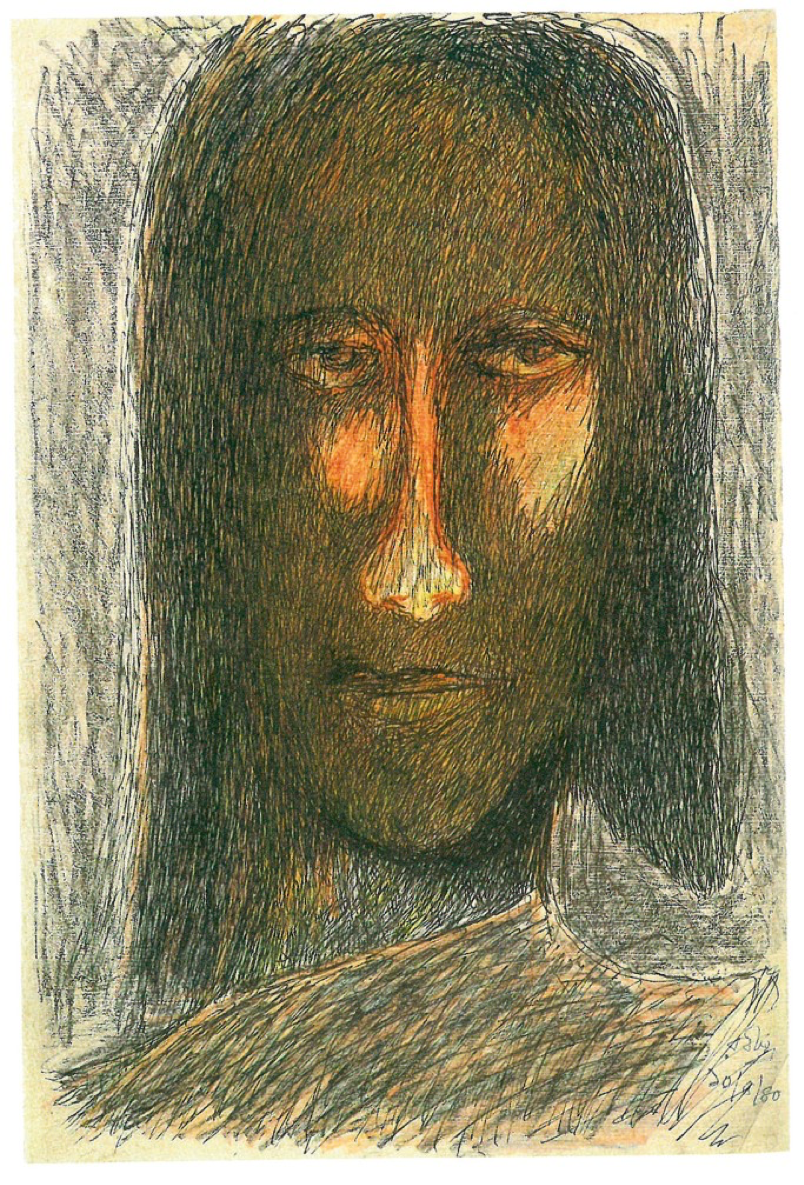
একটি উত্তরণের ইতিকথা
বহুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশ্ন তুলেছিলেন মহুয়া কাব্যগ্রন্থে ‘সবলা’ শীর্ষক কবিতায়, ২৩শে আগস্ট ১৯২৮ সালে।
“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
নত করি’ মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি’ পণ।” [১]
পুরুষতন্ত্রের কাছে এই প্রশ্ন ছিল তাঁর। স্বভাবতই সযত্নে গড়া পুরুষ-অনুশাসন এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিধবা পত্নী সাহানা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ কি নিজেই এর জবাব দিতে পেরেছিলেন?
এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় একশো কুড়ি বছর। বিংশ শতকের প্রথম বছর। সদ্য মৃত্যু ঘটেছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পর তরুণী পত্নী সুশীতলা তখন ফিরে গেছেন এলাহাবাদে, তাঁর বাপের বাড়িতে। আমাদের কাহিনীর যবনিকা উঠছে ঠিক সেই সময়ে।
রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বইতে লিখেছেন, “১৩০৮ সালের পৌষ-উৎসবের সময়ে যথাবিধি অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রথীন্দ্রনাথ বোর্ডিংএ থাকিলেন। মৃণালিনী দেবী ও অন্যান্য সন্তানদের কবি শান্তিনিকেতনে আনিতে পারিলেন না ; কারণ তখন একমাত্র অতিথিশালা ছাড়া আর কোনো থাকিবার-মত বাড়ি ছিল না। ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়ে’ ছাত্র-অধ্যাপকরা কোনোমতে থাকিতেন। সুতরাং মৃণালিনী দেবীকে সাময়িকভাবে শিলাইদহেই গিয়া বাস করিতে হইল। পূর্বে কবিকে শিলাইদহ-কলিকাতা যাওয়া-আসা করিতে হইত, এখন বোলপুর যোগ হইল। মৃণালিনী দেবী শিলাইদহে তিনটি শিশু লইয়া প্রায়ই একা পড়েন ; তাই স্থির হইল বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী সাহানা দেবীকে (সুসি) এলাহাবাদ হইতে আনিয়া শিলাইদহে মৃণালিনী দেবীর কাছে রাখিয়া আসিবেন। তদনুযায়ী চৈত্রের গোড়ায় (?৫ই চৈত্র, ১৩০৮) কবি এলাহাবাদ যান ; সেখানে এডমণ্ডস্টোন রোডে এক হোটেলে থাকেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনবীমা-সংগঠন- কার্য লইয়া উত্তরভারত ঘুরিতেছিলেন, মোগলসরাইয়ে কবির সহিত দেখা। কবি স্ত্রীকে লিখিতেছেন, ‘ভাগ্যি সুরেন আমার সঙ্গ নিলে নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে কটা দিন কাটান আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।’ … এলাহাবাদ হইতে সাহানা দেবীকে লইয়া কবি কলিকাতা লইয়া শিলাইদহ যান ও তথা হইতে বোলপুরে ফিরিয়া যথাসময়ে বর্ষশেষের ও নববর্ষের উপাসনা করেন।” [২]
প্রভাতকুমার যেভাবে লিখেছেন, ব্যাপারটা কি এতোটাই সহজ সরল ছিল? আদৌ তা নয়। মাত্র তেরো বছরে বিয়ে হয়েছিল সাহানা ওরফে সুশীতলার, এবং ষোলো বছরেই সমস্ত স্বাদ আহ্লাদ ঘুচিয়ে বিধবার শুভ্র সাজে সাজতে হয়েছিল তাঁকে। সাহানা দেবী চলে গেলেন এলাহাবাদে, পিতার গৃহে। দিন বদলেছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনসম্মত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রচলিত বিধবা বিবাহরীতির তখন মধ্যযুগ। আদি ব্রাহ্মসমাজে চালু না হলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা এই আইনকে সামাজিক রূপ দেওয়ার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। আজকের দিনেও শুনলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগী দুর্গামোহন দাসের উদার বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার কাহিনী। নিজের বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পর “সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে তিনি নিজের তরুণী বিমাতার সঙ্গে একজন বন্ধুর বিয়ে দিয়েছিলেন।” [৩] যাইহোক, তরুণী বিধবা সাহানা দেবীর বিবাহের আয়োজন হল। উদ্যোগ করলেন তাঁর পিতা ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। খবর এল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে।
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও বিধবা বিবাহের পক্ষে কখনও সমর্থন করেননি শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষেই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুকে তিনি একসময় লিখেওছিলেন – এই বিধবা বিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে। আর তখন তো তিনি পরিচিত হিন্দু ব্রাহ্ম হিসেবে। একথা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও হিন্দুসমাজের বহু সংস্কার, (নাকি কুসংস্কার?) নিষ্ঠার সঙ্গে সারাজীবন পালন করে গেছেন। ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’ গ্রন্থে চিত্রা দেব দেখিয়েছেন, “বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা কোনোটাই তাঁর সমর্থন পায় নি।” [৪] কাজেই দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিধবা বিয়ে মেনে নেয়া অসম্ভব। হাজার হোক ঠাকুর বাড়ির বিধবা, তার একটা সম্মান নেই !
অতএব, ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রগতিশীল পরিবার হয়েও ঠাকুরবাড়ি তরুণী সাহানা দেবীর বিধবা বিবাহকে মেনে নিতে পারলেন না। না, কথাটা একটু ভুল হল, ঠাকুরবাড়ির সবাই এই গড্ডলিকাপ্রবাহে যুক্ত হননি। মহর্ষি বড়ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বললেন এই বিয়ে যাতে না হয় তার ব্যবস্থা নিতে। হিন্দুমেলার পৃষ্ঠপোষক হলেও সংস্কৃতিবান দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ অপারগ হলেন পিতার এই অমানবিক নির্দেশ মান্য করতে। আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ তো কথাটা শুনেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি বিধবা বিয়ের ঘোর সমর্থক, সদ্য নারীমুক্তির মশাল জ্বেলে দিয়েছেন জীবনসঙ্গিনী জ্ঞানদানন্দিনীর জীবনে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পিতার ইচ্ছা পূরণে অসমর্থ হলেন, কারণ তিনিও চান না তরুণী সাহানা অকাল বৈধব্যের অভিশাপ কুড়িয়ে সারা জীবন কাটান। তখন মহর্ষি ডাকলেন রবিকে। এবং চরম পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠ পুত্র প্রগতিশীল রবীন্দ্রনাথ চললেন এলাহাবাদে পুনর্বিবাহে সম্মত একটি বিধবা তরুণীর বিয়ে ভাঙতে !
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটি হয়তো আজ বিশেষ পরিচিত নয়, তবে এটুকু বলা যায়, বিশ্বভারতী নামে যে মহীরুহটি আজ তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে অসংখ্য মানুষের মনে জ্ঞানের স্পৃহা জ্বালিয়ে চলেছে, সেই বীজ বপনের চিন্তাভাবনা এবং তাঁর নিয়মাবলী ও নির্দেশিকার খসড়া রূপায়ণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে হয়নি। সেটি প্রাথমিকভাবে রূপায়িত হয়েছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মস্তিষ্ক থেকেই।
১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্ম বলেন্দ্রনাথের। পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শোনা যায়, বীরেন্দ্রনাথ বিয়ের আগেই সামান্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ছিলেন, এবং সেটা জেনেও প্রফুল্লময়ীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এই ভেবে যে বিয়ের পর পাগলামি ভালো হয়ে যেতে পারে। এমন অমানবিক এবং অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ হয়তো শুধু আগেকার দিনে কেন, এখনও মাঝেমধ্যে শোনা যায়। রবি জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন যে ১৮৬৬ সালে তাঁদের বিয়ে হয় এবং বিয়ের দুই বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৬৮ সাল নাগাদ বীরেন্দ্রনাথ উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়েছেন প্রশান্তকুমার, ১৮৬৯ সালে “আহমদনগর থেকে ১৯শে জুলাই তারিখে লিখিত একটি পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লেখেন : ‘বীরেন্দ্রের বিষয়ে আমাদের যাহা ভয় ছিল, তাহাই কি ঘটিল – বড় আক্ষেপের বিষয়। তাকে কোথাও বেড়াইতে লইয়া গেলে হয়ত ভাল হয়।’ এই চিঠি থেকে বোঝা যায় এই পীড়ার লক্ষণ অনেক আগে থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল।” [৫] খুবই খারাপ অবস্থায় কেটেছে বীরেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। যাইহোক, বলেন্দ্রনাথ ছিলেন বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান, ঠাকুরবংশের আর একজন বিস্ময়কর প্রতিভাধর মানুষ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বলেন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিতান্ত অল্প বয়সেই তার সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ হয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত ‘বালক’ পত্রিকার ১২৯২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তার প্রকাশিত ‘একরাত্রি’ প্রবন্ধ এবং ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত ‘সন্ধ্যা’ কবিতাই তার প্রথম গদ্য ও পদ্য রচনা। তার জীবিতাবস্থায় মাত্র তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, প্রবন্ধ সংকলন ‘চিত্র ও কাব্য’ (১৮৯৪) এবং কাব্যগ্রন্থ ‘মাধবিকা’ (১৮৯৬) ও ‘শ্রাবণী’ (১৮৯৭)। কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যও সমালোচনা করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ। ‘ভারতী’, ‘বালক’ , ‘সাহিত্য’, ‘সাধনা’ ইত্যাদি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। এই সকল রচনায় তার মননশক্তি, চিন্তার গভীরতা ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।
জমিদারি দেখাশোনা করাবার ভার পেয়ে ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে সস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথ গেলেন শিলাইদহে। সঙ্গে ছিলেন তরুণ বলেন্দ্রনাথ। এই শিলাইদহেই রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীজীবনের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সান্নিধ্যে আসেন। শিলাইদহে থাকাকালীন তাঁরা দুজনেই স্থানীয় কবি ও ফকিরদের প্রচুর গান শুনতেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন সুনাউল্লাহ। শোভন সোম তাঁর ‘বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে লিখেছেন, “বলেন্দ্রনাথ সুনাউল্লাহর মুখ থেকে শুনে বারোখানি গান লিখে রেখেছিলেন। তার মধ্যে একটি গান গগন মণ্ডল বা গগন হরকরার। গগন মণ্ডলের নামে পাশে বলেন্দ্রনাথ ‘শিলাইদহের ডাক-হরকরা’ লিখে রেখেছিলেন। গগন মণ্ডলের’আমি কোথায় পাব তারে’ গানটি এইভাবে বলেন্দ্রনাথ উদ্ধার করেছিলেন। এই গানটির সুরের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’।” [৬]
কেবলমাত্র সাহিত্যচর্চাতেই দিন কাটেনি বলেন্দ্রনাথের। শোভন সোম বিরচিত ‘বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ’ থেকে উদ্ধৃত করে কালি ও কলম পত্রিকায় অভিজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, “রবিকাকার সঙ্গে পত্রিকার অনেকখানি দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া ছাড়াও যৌথ ব্যবসায় (রবীন্দ্রনাথ-বলেন্দ্রনাথ-সুরেন্দ্রনাথ) যুক্ত হয়ে পাট, ভুসিমাল, আখমাড়াই ইত্যাদির কারবার শুরু করেন। আবার এই একই উৎসাহ নিয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার আদর্শে বলেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-সাধনাশ্রমে ছয় শ্রেণীর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করিলেন।” [৭]
এই শান্তিনিকেতনের কাহিনীতে জানতে গেলে আমাদের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র দুই বছর অর্থাৎ ১৮ই ফাল্গুন, ১২৬৯ বঙ্গাব্দে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের সিংহদের থেকে বোলপুরের কাছে কুড়ি বিঘে জমি কেনেন। তিনি সেখানে একটা বড়মাপের বাড়ি তৈরি করেন, যা শান্তিনিকেতন নামে পরিচিত ছিল। এর পঁচিশ বছর পর ১২৯৪ বঙ্গাব্দে দেবেন্দ্রনাথ একটি ট্রাস্ট-ডিড করে ওই অট্টালিকা সংলগ্ন জমি উৎসর্গ করেন এবং নিজ জমিদারির কিছু অংশ শান্তিনিকেতনের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবত্র করে দেন। ওই ডিডে বলা হয়েছিল, “তথায় কোনো মূর্তি বা প্রতিমা বা প্রতীক পূজা হইতে পারে না। কোনো ধর্মের শিক্ষা, মদ্য মৎস্য মাংস-ভোজন ও জীবহত্যা নিষিদ্ধ ; নিন্দনীয় আমোদ আহ্লাদও হইতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথের আশা ছিল শান্তিনিকেতন নির্জন সাধনকামীদের আশ্রম হইবে। সাধনকামীদের উপাসনার জন্য ১২৯৮ সালে শান্তিনিকেতনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সঙ্গে সাতই পৌষের উৎসব ও পরে মেলা প্রবর্তিত হয়।” [৮] এরপর আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আরও ছয় বছর, অর্থাৎ ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। সেই সময়ে মহর্ষির পৌত্র বলেন্দ্রনাথ পঞ্জাবের একেশ্বরবাদী আর্যসমাজের সঙ্গে বঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মিলন স্থাপন এবং ধর্ম বিষয়ে একত্রে কাজ করার অভিপ্রায়ে পঞ্জাব গিয়েছিলেন। “কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁদের বেদসর্বস্ব মনোভাব ও মতবাদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যুক্তি ও ভক্তিমিশ্রিত ব্রহ্মবাদের মিলন সম্ভব নয় বুঝতে পেরে, পঞ্জাব থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন।” [৯] এরপর বলেন্দ্রনাথ স্থির করেন, ব্রহ্মসমাজের আদর্শকে সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে দিতে গেলে একটি শিক্ষাকেন্দ্রের সবিশেষ প্রয়োজন। শান্তিনিকেতনে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করবার ভাবনার কথা তিনি মহর্ষিকে জানালে মহর্ষি সেই ভাবনাকে যথোপযুক্ত মনে করে সম্মতি দিলেন। নব উদ্যমে বলেন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হন। মহর্ষির অনুমতি পেয়ে তিনি এই পরিকল্পনার বিস্তারিত খসড়া তৈরি করেন এবং শান্তিনিকেতনে তিনটি ঘর সমেত একতলা গৃহও নির্মাণ করেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর সেই খসড়াটি প্রভাতকুমার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তা রবীন্দ্র-জীবনীর চতুর্থ খণ্ডের সংযোজনীতে বর্ণিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এর আগে বলেন্দ্রনাথের বিভিন্ন উদ্যোগে, সে সাহিত্যই হোক বা ব্যবসা ; সকল কাজেই রবীন্দ্রনাথের সরাসরি যোগদান ছিল। ব্যতিক্রম এই ব্রহ্মবিদ্যালয়। প্রভাতকুমার স্পষ্টভাবে বলেছেন, “কিন্তু এই ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ পাই না। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় হইতে শিলাইদহে নিজ সন্তানদের জন্য গৃহবিদ্যালয় স্থাপনে পরিকল্পনারত। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে (ভাদ্র ১৩০৬) তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী হয় নাই।” [১০] ১৮৯৯ সালের ২০শে আগস্ট তাঁর অকালমৃত্যুতে প্রকল্পটি বাধাগ্রস্ত হলেও পরিত্যক্ত হয় নি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই বছরেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বছর দুই পরে রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনারই পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা লিখেছেন রবি জীবনীকার প্রশান্তকুমার। তিনি জানিয়েছেন, প্রকল্পের উদ্বোধনের পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রিপোর্টে মহর্ষির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলেও বলেন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করা হয় নি। এমনকি, “দুবছর পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে বা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও বলেন্দ্রনাথের প্রয়াসকে স্বীকৃতি জানান নি।” [১১]
অবশ্য আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদক লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক কালে জমিদারির কাজে শিলাইদহে থাকছিলেন। সে সময়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তিনি দিতে পারেননি। যে কারণে তিনিও সে সময়ে মনে মনে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবছিলেন। যদিও তিনি শিলাইদহে গৃহবিদ্যালয় চালু করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত শিক্ষা পরিকল্পনার প্রতি কবিগুরুর পূর্ণ সমর্থন ছিল বলেই তিনি তাঁর মনে ভাবনাকৃত বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করার কথা ভেবে লিখেছিলেন – ‘আমি পিতাকে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি এক আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।’ পিতার সম্মতি পাওয়ার পরে বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত কাজের পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছরেই ১৩০৬ সনে ৭ পৌষ মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষাদান দিনের উৎসবের মধ্যে দিয়েই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং, সেই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়টি বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। তাই এর গড়ে ওঠার নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদানের সঙ্গে সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদানকেও অস্বীকার করা যাবে না।” [১২] প্রশান্তকুমারের মতে “শান্তিনিকেতন আশ্রমের তিনি (রবীন্দ্রনাথ) একজন ট্রাস্টি ছিলেন ও শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট ভাবনারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে – সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের সংকল্প তাঁর সোৎসাহ সমর্থন লাভ করবে। … তিন বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তাঁর ব্যবহারিক ও আত্মিক প্রয়োজন ছিল ভিন্নতর, কিন্তু তা অবলম্বন করেছিল বলেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রস্তুত ভিত্তিটিতে – দুঃখের বিষয়, এই ‘সলতে পাকানো’ ইতিহাসটিকে তিনি কোথাও স্বীকৃতি দিয়ে যান নি।” [১৩]
বলেন্দ্রনাথের পরিবারের উপর ঠাকুরবাড়ির অবিচারের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তাঁর মা প্রফুল্লময়ীর সঙ্গেও কিছু অসম আচরণ করেছেন ঠাকুরবাড়ি। সত্যি কথা বলতে কি প্রফুল্লময়ীর মতো হতভাগিনী নারীর সংখ্যা এই ধরণের অভিজাত পরিবারে হাতে গোনা। চিত্রা দেবের ভাষায়, “নাম তাঁর প্রফুল্লময়ী কিন্তু সারাটি জীবন তিনি চোখের জল ফেলে ঘরের কোণে বসে কাটিয়েছেন। রূপকথার রাজপ্রাসাদের মতো এই বিশাল ঠাকুরবাড়ির একটা ঘরে যে এত অশ্রুবিন্দু জমাট বেঁধে পাথর হয়ে উঠেছে সে কথাই বা কে জানতো?” [১৪]
বিয়ের বছর দুই পর স্নান আহার ত্যাগ করে অস্বাভাবিক হয়ে উঠলেন বীরেন্দ্রনাথ। লোকে বলে অঙ্ক কষতে কষতে বীরেন্দ্র পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের চার দেওয়ালে বড় বড় অঙ্ক করে রাখতেন কাঠকয়লা দিয়ে। এত দুঃখের মধ্যেও প্রফুল্লময়ীর সান্ত্বনা ছিল বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে। তার টুকটুকে বউ সাহানাকে নিয়ে। কিন্তু সুখ সইল না তাঁর। নিজের শরীরের উপর সীমাহীন অত্যাচার করে কালব্যাধি ধারণ করলেন বলেন্দ্র। অবশেষে ৩রা ভাদ্র, ১৩০৬ (১৯শে আগস্ট, ১৮৯৯) এর ভোরবেলা সব শেষ হয়ে গেল। প্রফুল্লময়ীর ভাষায়, “যেদিন সে জন্মের মত আমাকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, সেইদিন রবি, (আমার ছোট দেওর) আসিয়া আমাকে বলিলেন তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে মা মা করিয়া ডাকিতেছে। আমি এক এক সময়ে তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে বসিলাম তখন তার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহার পর একবার বমি করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। সূর্যদেব ধীরে ধীরে তাঁহার কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাহার দীপ নিভিয়া গেল।” [১৫]
বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কারণ বিভিন্ন জনের মতে বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়, পথকষ্ট ও অনিয়মে তাঁর স্বাভাবিক দুর্বল দেহে কঠিন রোগের সূত্রপাত হয়। তবে শোভন সোম রথীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তথ্যসূত্র উদ্ধৃত করে লিখেছেন, “বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অপর একটি কারণ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : ‘Baludada died young – one of the first victims in Bengal of Hindu-Moslem Communal tension … his death was due to the after-effects of a wound he received in the head.’ রথীন্দ্রনাথের এই অভিমত রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের মন্তব্য থেকে ভিন্ন।” [১৬]
দুঃখের এখানেই শেষ নয়। ছেলে বলেন্দ্রনাথ মাত্র ২৯ বছরে মারা গেলে মহর্ষির উইলের শর্ত মোতাবেক অপুত্রক ছেলে বীরেন্দ্রনাথ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। তবে মাথাপিছু ১০০ টাকা করে মাসোহারা বরাদ্দ ছিল বীরেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লময়ী ও সাহানা দেবীর জন্য। অথচ “আমরণ মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্য ১২৫০ টাকা।” [১৭] দেবেন্দ্রনাথের এই উইলের অন্যতম এক্সিকিউটার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও !মহর্ষির এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে আদৌ কি প্রশ্ন তুলেছিলেন কবি?কোনোদিন?
প্রফুল্লময়ী সব দুঃখ সহ্য করলেন ষোড়শী পুত্রবধূর মুখ চেয়ে। চিত্রা দেব লিখেছেন, “এমনই তাঁর কপাল যে পুত্রবিয়োগ ব্যথায় তিনি শোকে তাপে ভেঙে পড়েননি বলে বাড়ির সবাই আশ্চর্য বুঝি-বা বিরক্তও হলেন।” [১৮] তাঁদের প্রতি যে সুবিচার হয়নি একথাটি, মানুষের মন নিয়ে যিনি সারাজীবন কত কবিতা গান উপন্যাস রচনা করে গেছেন স্বয়ং সেই রবীন্দ্রনাথেরও মনে এল না, বরং ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ২৮শে আগস্ট, ১৮৯৯ (১২ই ভাদ্র, ১৩০৬) মৃনালিনীকে চিঠি লিখে অভিযোগ করলেন, “নবোঠানের এক ছেলে, সংসারের একমাত্র বন্ধন নষ্ট হয়েছে তবু তিনি টাকাকড়ি কেনাবেচা নিয়ে দিনরাত্রি যে রকম ব্যাপৃত হয়ে আছেন তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হয়ে গেছে – কিন্তু আমি মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্য আলোচনা করে সেটা শান্তভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করচি – এক একসময় ধিক্কার হয় কিন্তু সেটা আমি কাটিয়ে উঠতে চাই। আমাদের বাইরে কে কি রকম ব্যবহার করচে সেটাকে নির্লিপ্তভাবে সুদূরভাবে দেখতে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের শোকদুঃখ, বিরাগ অনুরাগ, ভাললাগা না লাগা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, সংসারের কাজকর্ম্ম, সমস্তই আমাদের বাইরে ; – আমাদের যথার্থ ‘আমি’ এর মধ্যে নেই – এই বাইরের জিনিসকে বাইরের মত করে দেখতে পারলে তবেই আমাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয় – সে খুব শক্ত বটে কিন্তু পদে পদে সেইটে মনে রেখে দেওয়া চাই। যখনি কাউকে খারাপ লাগে, যখনি কোন ঘটনায় মনে আঘাত পাওয়া যায় তখনি আপনাকে আপনার অমরত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া চাই।” [১৯] প্রফুল্লময়ীর এমনতর ব্যবহারের কারণ রবীন্দ্রনাথ না বুঝলেও চিত্রা দেব বুঝেছেন, “কবি চিঠিটা লিখেছিলেন বলেন্দ্রের শ্রাদ্ধের আগের দিন। প্রফুল্লময়ীর স্মৃতিকথা পড়ে মনে হয় কেনা বেচা কাজ কর্ম নিয়ে তিনি দুঃখ ভোলার চেষ্টা করছেন। নয়তো তিনি জল-ঝড় উপেক্ষা করে বলেন্দ্রের ঘরের সামনে দিনরাত পড়ে থাকতেন কেন?” [২০] ‘আমাদের কথা’-তে প্রফুল্লময়ী লিখেছিলেন, “তাহার মৃত্যুর পর সেই ঘরেই দরজা করিয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম। মনে হইত সে যেন পূর্বেকার মত আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই ঘরের সামনের বারান্দায় একটি মাদুরের উপর দিনরাত্রি শুইয়া কাটাইতাম। জল ঝড় বৃষ্টি সবই আমার উপর দিয়া যাইত, কিন্তু আমার তখন কোন দিকেই হুঁশ ছিল না, কেবল সর্বদা মনে হইত আমি না থাকায় তাহার আহারের না জানি কতই কষ্ট হইতেছে।” [২১] হৃদয়ের কবি স্রেফ বাহ্যিক কেনা বেচাটা দেখলেন, মায়ের অন্তরের কান্নাটা বুঝলেন না, ভেবেও অবাক লাগে। রবি জীবনীকার প্রশান্তকুমারের মতে, “মনে হয়, বৈষয়িক চিন্তায় বিব্রত রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবিক সহানুভূতি হারিয়ে প্রফুল্লময়ী দেবীর উপর কিছুটা অবিচার করেছেন। উন্মাদ স্বামীকে নিয়ে কষ্ট পাওয়া এই গৃহবধূর একটিমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল পুত্র বলেন্দ্রনাথ। চিররুগ্ন এই সন্তানটিকে নিয়েও তাঁর উদ্বেগের অবধি ছিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজ-আর্যসমাজের মিলনের এবং ঠাকুর-কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্যের অর্থহীন প্রয়াসে যখন প্রফুল্লময়ীর সেই একমাত্র অবলম্বন অকালে ঝরে গেল, তখন প্রবল শোকের মধ্যেও উন্মাদ স্বামী, বিধবা অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ ও নিজের স্বার্থরক্ষার জান্তব প্রয়োজনে বৈষয়িক হয়ে ওঠা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর ফলে দেবেন্দ্রনাথের শেষ উইলে বীরেন্দ্রনাথ সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হন ও তাঁর পরিবারের জন্য মাথাপিছু মাত্র ১০০ টাকা মাসোহারা নির্দিষ্ট হয় এবং মহর্ষির মৃত্যুর পর এই মাসোহারা পাওয়া গিয়েছে অবিবেচক ট্রাস্টীদের হাত থেকে, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন !” [২২] শেষ জীবনে আর্থিক দুর্দশায় পড়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রফুল্লময়ী।
চলুন আবার ফিরে আসা যাক সাহানা দেবীর কাহিনীতে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার কবির এলাহাবাদ যাত্রা নিয়ে মুল গ্রন্থে কি জানিয়েছিলেন, আমরা তা পড়েছি। ওই দ্বিতীয় খণ্ডেরই সংশোধনীতে প্রভাতকুমার আবার লিখেছেন, “বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (২২শে আগস্ট, ১৮৯৯) পর বিধবা পত্নী সাহানা তাঁহার পিতার নিকট এলাহাবাদে চলিয়া যান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় শুনিতে পান যে, ‘বলেন্দ্রের বিধবা পত্নীর বিবাহ দিবার জন্য বলেন্দ্রের শ্বশুরপক্ষ আয়োজন’ করিতেছেন। মহর্ষি সমাজসংস্কারাদি ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী ছিলেন ; তিনি অত্যন্ত উদবিগ্ন হইয়া উঠেন। ইতিমধ্যে বলেন্দ্রের শ্বশুর ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটিল ; তখন দেবেন্দ্রনাথ পৌত্রবধূকে নিজেদের সংসারে আনাইয়া রাখিবেন স্থির করিলেন। মহর্ষির নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদে রওনা হইয়া যান।” [২৩]
মুল লেখা এবং সংশোধনীতে প্রভাতকুমার একবারের জন্যেও কিন্তু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের অপরাপর ভাইদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে রা কাড়েন নি, যে কথা প্রখ্যাত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অমিতাভ চৌধুরী খোলাখুলি জানিয়েছেন তাঁর ‘অন্য রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে। “রবীন্দ্রনাথ নিজের ছেলের বিয়ে দিয়েছেন এক বিধবার সঙ্গে, কিন্তু পিতৃআজ্ঞা পালন করতে এক বিধবা-বিবাহ ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওই রবীন্দ্রনাথই। আদরের ভাইপো বলু – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাত্র ২৯ বছর বয়সে মারা গেলেন তিনি, রেখে গেলেন কিশোরী বিধবা সাহানা দেবীকে। সুন্দরী ফুটফুটে মেয়ে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির অনেকেই ভাবেন, আহা মেয়েটির আবার বিয়ে দিলেই হয়। মেয়ের বাবা থাকেন এলাহাবাদে, সকলের পরামর্শে তিনিও রাজি হলেন। কিন্তু তখনও ঠাকুর বাড়ির বড় কর্তা দেবেন্দ্রনাথ – নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম। তিনি এই বিবাহে মত দিতে নারাজ। বড় দ্বিজেন্দ্রনাথ আত্মভোলা মানুষ। এই বিবাহ বন্ধ করবার ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিনি দিতে চাইলে দ্বিজেন্দ্রনাথ আমতা আমতা করে বলেন, এই ভার নিতে তিনি অপারগ, কারণ তিনিও চান বিয়েটা হোক। মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত ফেরত আই সি এস, নারীমুক্তির বড় উকিল। তিনিও প্রত্যাখ্যান করলেন পিতার অনুরোধ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বক্তব্যও তাই। অবশেষে ডাক পড়ল কনিষ্ঠ পুত্র রবির। দেবেন্দ্রনাথ বললেন, তিনি চান না যে তাঁর পৌত্রবধূর পুনর্বিবাহ হোক। হাজার হোক ঠাকুরবাড়ির বউ। দেবেন্দ্রনাথ আদেশ দিলে, রবীন্দ্রনাথ যেন যেভাবেই হোক এই বিয়ে বন্ধ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ পড়লেন মহা বিপদে। নীতিগতভাবে তিনি এই বিয়ে সমর্থন করেন। অথচ পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করবার কোনো উপায় নেই। মানসিক দ্বন্দ্বে জীর্ণ রবীন্দ্রনাথ শেষমেষ স্থির করলেন, পিতৃআজ্ঞা পালনই শ্রেয় এবং উদ্যোগী হয়ে এলাহাবাদ গেলেন, সাহানা দেবীর বিবাহ বন্ধ করে দিলেন, ভ্রাতস্পুত্রবধূকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে এলেন।” [২৪]
একই কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রামাণ্য জীবনীকার, প্রশান্তবাবু। “১৫ই কার্তিক (বুধ ৩১শে অক্টোবর) তিনি এলাহাবাদ রওনা হন বলেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী সাহানা দেবীকে নিয়ে আসার জন্য। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : বলেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার শ্বশুর সার্জন-মেজর ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া যান এবং তাহার পুনরায় বিবাহের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় মহর্ষির ব্যবস্থায় পৌত্রবধূকে আপনার কাছে আনিয়া রাখাই স্থির হয় এবং রবীন্দ্রনাথকে সেই দৌত্যে পাঠানো হইল।” [২৫]
এতক্ষণ পর্যন্ত পড়লে বুঝবেন, এইখানে সাল-তারিখ নিয়ে মস্ত একটা বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র জীবনীকারদের মধ্যে, তবে তারিখ নিয়ে দ্বিমত থাকলেও সাহানা উদ্ধারের ঘটনাটি সত্যি কারণ এলাহাবাদ হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্ত্রী মৃণালিনীকে ১৯০১ সালের ৩১শে জানুয়ারি লিখেছিলেন “আজ এলাহাবাদে এসে পৌঁচেছি। সুসি (সাহানা) এবং তার মার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুসি যেতে রাজি হয়েচে, তার মাও সম্মতি দিয়েচেন। কলকাতা হয়ে শিলাইদহে যাওয়াই স্থির হল। যে রকম বাধা পাব মনে করেছিলুম তার কিছুই নয়। ভাল করে বুঝিয়ে বলতেই উভয়েই রাজি হল। পর্শু অর্থাৎ শনিবার এখান থেকে ছাড়বো। ভাগ্যি সুরেন মোগলসরাই থেকে আমার সঙ্গ নিলে নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে কটা দিন কাটান আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।” [২৬] তবে প্রশান্তকুমারের মতে এই চিঠির তারিখ ১৬ই কার্তিক অর্থাৎ ১ নভেম্বর ১৯০০। প্রভাতকুমার লিখছেন, কবি সাহানাকে লইয়া ৩ ফেব্রুয়ারি (১৯০১) ফিরিয়া আসেন, পক্ষান্তরে প্রশান্তকুমারের মতে ফিরে আসবার তারিখ ১৮ই কার্তিক অর্থাৎ ৩ নভেম্বর (১৯০০) !
সাল-তারিখের বিভ্রান্তিতে না জড়িয়ে বরং মৃণালিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্বটা দিন। অবশ্য তার আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি পরপর একটু গুছিয় নেওয়া যাক। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সাহানাকে নিয়ে তাঁর মা এলাহাবাদে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। তিনি তরুণী বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের আয়োজন করছেন শুনে রক্ষণশীল’ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম’ দেবেন্দ্রনাথ চরম বিচলিত হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখা বিধবাবিবাহের প্রচলন সম্বন্ধে উৎসাহী থাকলেও আদি ব্রাহ্মসমাজ এর সমর্থন করে নি, এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা হলেন দেবেন্দ্রনাথ। মহর্ষির অন্যান্য পুত্রেরা তাঁর আদেশ মানতে অস্বীকৃতি জানালে মহর্ষি পৌত্রবধূকে ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব অর্পণ করলেন রবীন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ আদেশের ন্যায় নীতি প্রগতিশীলতা কিছুই ভাবলেন না। এলাহাবাদে পৌঁছে তিনি সাহানার অভিভাবকদের বুঝিয়ে বললেন মহর্ষির বার্তা। কি ছিল সেই বার্তায়? ঠাকুরবাড়ির বধূ বিধবা বিবাহ করলে ঠাকুরবাড়ির মর্যাদায় আঘাত লাগবে, এই কথাই কি ছিল?এমন কি, পরের দিন এলাহাবাদ থেকে স্ত্রী মৃণালিনীকে লেখা চিঠিতে কি লিখলেন তিনি?অকাল বৈধব্যের অনিশ্চিত জীবনের নরকে ষোলো বছরের একটি তরুণীকে ঠেলে দেয়ায় তাঁর ভূমিকার জন্য কোনোরকম অনুশোচনা কি দেখা গেল তাঁর পত্রে? বরং প্রায় সহজেই পুনর্বিবাহে সম্মত একটি তরুণীকে ও তার অভিভাবকদের অতি সহজেই সে কাজে বিরত করতে পেরে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুনলাম প্রগতিশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
আমাদের দেশের পুরানো সমাজব্যবস্থায় নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতায় নানাদিক থেকে বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার – এই জগতের মাঝেই বন্দী হয়ে থাকতে বাধ্য করা হত তাঁদের। নারীর এই দুর্দশার সর্বপ্রথম প্রতিকার করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা। তাঁরাই নারীশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, নারী স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের এক অগ্রগামী পুরুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথও একাধিকবার তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বোঝাতে প্রচেষ্টা করেছিলেন – নারী পুরুষের যোগ্য সহচরী হওয়ার অধিকারিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ‘চিত্রাঙ্গদা’ কাব্যগ্রন্থে চিত্রাঙ্গদার জবানীতে তাঁর বক্তব্য,
“… দেবী নহি, আমি নহি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।” [২৭]
কবি চিত্রাঙ্গদা লিখেছিলেন ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।
এক্ষেত্রে একটা কথা হল, কোনও সামাজিক বিষয়ে একটি প্রগতিশীল মত প্রকাশ করা এক বস্তু, আর ব্যক্তিগত জীবনে তাকে কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। আমাদের দেশে সামাজিক সংস্কারের যা প্রয়াস হয়েছে তা হয়েছে প্রধানত কাগজে-কলমে, তাই বিধবা বিবাহ অথবা অসবর্ণ বিবাহ এ-সবই, আইন মোতাবেক স্বীকৃত হলেও, আজও তা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। বলা বাহুল্য, একেবারেই রক্ষণশীল ব্যক্তি বাদে, এই সব পথ ও মতের উপযোগিতা আমরা সকলেই স্বীকার করি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এদের অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলি। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও কি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পেরেছিলেন সবসময়ে? বিশেষত সাহানা দেবীর ক্ষেত্রে?
কারণ, সাহানাদেবীর ইতিহাস কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। সাহানার দুঃখ কোনোদিনও ঘোচে নি। শ্বশুরবাড়ী ফিরে এসে তিনি মন দিলেন লেখাপড়ায়। শাশুড়ি প্রফুল্লময়ী সাহানাকে স্কুলে পড়ালেন, এমনকি টিচার্স ট্রেনিং নেবার জন্য বিলেতেও পাঠিয়ে ছিলেন। “আমার পুত্রবধূ সাহানাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম, ভাবিলাম লেখাপড়ায় নিজের মনকে নিয়োগ করিতে পারিলে মনে অনেকটা শান্তি পাইবে, শিক্ষার দ্বারা মনের উন্নতি লাভ হওয়া সম্ভবপর – অবশ্য যদি প্রকৃত শিক্ষা পায়। কিছুদিন পরে সে বিলাতে ট্রেনিং পড়িবার জন্য গিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন থাকিবার পর শরীর অসুস্থ হওয়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। সে যাহা করিতে চাইত আমি কখনই তাহাতে বাধা দিই নাই, তাহার শরীর মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে তাহারই চেষ্টা করিতাম।” [২৮]
শাশুড়ি প্রফুল্লময়ী বাধা না দিলেও, বাধা দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ! ১৯০৮ সালের জুন মাসে (বাংলা আষাঢ়, ১৩১৪) সাহানা পিতৃগৃহ এলাহাবাদ থেকে চিঠি লিখে শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহের কথা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছিলেন জানেন? ১০ই আষাঢ় (২৫শে জুন) রবীন্দ্রনাথ সাহানাকে জানালেন, “আমাদের বিদ্যালয়ে Science পড়াইবার সুবিধা আছে বটে কিন্তু বিদ্যালয়ের Laboratoryতে তোমাকে শিক্ষা দিতে গেলে সকলের সামনে তোমাকে বাহির হইতে হইবে – সে কি সম্ভব হইবে?” [২৯] রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি সম্ভবত বিশ্বভারতী থেকে ছাপা চিঠিপত্রের কোনো খণ্ডে প্রকাশিত হয় নি, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। মনে রাখতে হবে, এই রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লেখবার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর প্রভাব সম্ভবত তখনও রবীন্দ্রনাথের মনে কাজ করছে। অন্ততপক্ষে সাহানার বিষয়ে। ভেবে দেখুন, শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সাহানাকে প্রবেশাধিকার দিলেন না, স্রেফ বিধবা হওয়ার অপরাধে! অথচ সেই কবে জ্ঞানদানন্দিনী কলকাতায় লাটসাহেবের বাড়ি গেছেন, বিদেশ গেছেন, উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, চাকরি করেছেন সরলা দেবী। আর বিংশ শতকের প্রথম দশকে কেবলমাত্র প্রকাশ্যে আসতে হবে এই অজুহাত দিয়ে নারীমুক্তির মহিমা কীর্তনকারী রবীন্দ্রনাথ সাহানাকে বঞ্চিত করলেন। এ কি স্রেফ বিধবা হওয়ার অপরাধে? নাকি অন্য কোনো গূঢ় কারণ আছে? স্বভাবতই প্রশ্ন তুলেছেন সাদ কামালী, মুক্তমনা ব্লগের প্রবন্ধে, “সাহানা যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী হবে তখন সে কিন্তু শুধু ছাত্রী পরিচয়ে নয়, তার পরিচয় ঠাকুর বাড়ির বিধবা রূপে। এই সেই বিধবা, যার বাবা মা বিধবা বিবাহের আইন পাস ও সামাজিক সংস্কারের যুগে অকাল বৈধব্যের অভিশাপ মুক্ত করতে আবার বিয়ের আয়োজন করেছিলেন তা থেকে সাহানাকে চির বৈধব্যের বেশে ঠাকুর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লোকে এই কথা মনে করবে তাকে দেখলে।” [৩০] তাই কি এই বাধাদান?
চিত্রা দেব সত্যি কথাই লিখেছেন, “সাহানার কথা ঠাকুরবাড়ির কেউ কোনোদিন ভাবেন নি, এমনকি রবীন্দ্রনাথও নয়। একথা ভাবলে সত্যিই কষ্ট হয়। মনে হয় সকলের নিষ্ঠুর ঔদাস্যে সায়াহ্নের সকরুণ সাহানা হারিয়ে গেলেন অকালে।” [৩১]
মহর্ষিচিত নয়, দেবেন্দ্রনাথের এমন অনেক অনৈতিক এবং অমানবিক সিদ্ধান্ত আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে মুখ বুঝে মেনে নিতে। এর একটা কারণ, নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক। রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটা বড় অংশ দেবেন্দ্রনাথের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছে, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে তাঁর সময় লেগেছে। তাই হয়তো দুই দেবেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে থাকতেই দুই কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা তাঁকে করতে হয়েছিল যাতে যৌতুকের টাকার ব্যবস্থাটা ঠাকুরবাড়ির ফান্ড থেকে হয়ে যায়। না হলে তড়িঘড়ি মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মাধুরীলতা আর দশ বছর বয়সে মীরার বিয়ে দেওয়ার আর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ রবীন্দ্র গবেষকরা দেখিয়েছেন বলে আমি অন্ততঃ জানি না। বরং এই প্রসঙ্গে জীবনীকার প্রশান্তকুমার লিখেছেন, “ঠাকুরবাড়িতে গত কয়েকবছর ধরে অনেকগুলি বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, এর মধ্যে পরিবারের কর্তাদের কিছু সূক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি কাজ করেছে। … বহুব্যয়সাপেক্ষ বিবাহের খরচটি এসেছে সরকারি ক্যাশ থেকে … মহর্ষির জীবৎকালে তাঁর পরিবারে এইটেই রীতি ছিল। সুতরাং তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও ২৩শে ভাদ্র ১৩০৬ (৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯) তারিখে তাঁর শেষ উইলে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পরিবারভুক্ত কেউ কেউ যদি কন্যাদায় থেকে অসময়েই উদ্ধার পেতে চান তাহলে তাঁদের বৈষয়িক বিচক্ষণতার প্রশংসা করতেই হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও চৌদ্দ বছরের কমবয়সী মাধুরীলতার বিবাহের জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ত হওয়াতে আশ্চর্যবোধ না করে পারা যায় না। ‘হিন্দু বিবাহ”অকাল বিবাহ’ প্রভৃতি সম্বন্ধে ও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বিতর্কে তিনি বাল্যবিবাহরোধে আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা স্বীকার না করলেও তাঁর স্পষ্ট সমর্থন ছিল যৌবন বিবাহের প্রতি। … কেবল কবি নয়, বাঙালি সমাজে তাঁর ভূমিকা ছিল চিন্তানায়কের। তাই ব্যক্তিস্বার্থে তাঁর সামাজিক ভূমিকা বিস্মরণের ইতিবৃত্তটি কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর।” [৩২]
আর একটা কারণ হল, আমরা রবীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি পড়লেই বুঝতে পারি, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শের একটা গাঢ় প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যতোটা গভীরভাবে পড়েছিলো, পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর ততটা পড়েনি। সম্ভবত তাই, দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও আরও কয়েকটি বছর প্রভাবের সেই কালো মেঘ মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও চিন্তার আকাশকে ঢেকে রেখেছিল।
এইখানে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, চিন্তার ক্ষেত্রে এই অন্ধত্ব, এই দৈন্যতা কি শতাব্দীর সূর্যকে মানায়? মানায় না বলেও ভাবতে হয় যে জীবনের প্রথম অর্ধাংশ কিছু কিছু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি থেকে গিয়েছিলেন রক্ষণশীল, সনাতনপন্থী। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে (১৮৯১) লিখিত তাঁর ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্য’ প্রবন্ধের অংশবিশেষ পড়লেই এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে।
“বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী, কখনো দুহিতা, কখনো সখী। এইজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবাতৎপর হয়ে থাকেন। বাড়ির শিশুরা তাঁরই চোখের সামনে জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁরই কোলে কোলে বেড়ে ওঠে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখদুঃখময় প্রীতির সখিত্ববন্ধন, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে স্নেহভক্তিপরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ ; গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। এবং ওরই মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো-একটা পুরাণ পড়বার কিংবা শোনবার সময় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলায় ছোটো ছোটো ছেলেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে উপকথা বলাও একটা স্নেহের কাজ বটে। … এই-সকল কারণে, তোমাদের যে-সকল মেয়ে প্রমোদের আবর্তে অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান কিংবা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিংবা দুটো একটা কুকুরশাবক এবং চারটে পাঁচটা সভা কোলে করে একাকিনী কৌমার্য কিংবা বৈধব্য যাপনে নিরত, তাঁদের চেয়ে যে আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা অসুখী, এ কথা আমার মনে লয় না। … আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই করবার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ, এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের রমণীদের শিক্ষার অঙ্গহীনতা আছে এবং অনেক বিষয়ে তাদের শরীরমনের সুখসাধন করাকে আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসযোগ্য জ্ঞান করি। এমন-কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন করানোকে আমাদের দেশের পরিহাসরসিকেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে স্থির করেন ; কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায়, আমাদের স্ত্রীকন্যারা সর্বদাই বিভীষিকারাজ্যে বাস করছেন না এবং তাঁরা সুখী।” [৩৩]
প্রবল বিস্মিত হই বুঝলেন, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধাংশটি পড়ে, মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ কি করে ভুলে গেলেন আজও, গ্রামের বিধবা পিসিমা সদ্য স্ত্রী হারানো ভাই এর কাছে ‘মাংসের ঝোল কেমন হয়েছে?’ জানতে চাইলেও, নিজের চেখে দেখার অধিকারটুকু নিজের নেই! কিংবা, স্ত্রী বিয়োগের পর ভাই এর দ্বিতীয় বিয়েতে ব্রাত্য থাকেন বিধবা বোনটি; কারণ বিধবা মানেই ‘অকল্যাণ’! এখনও দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর দিনে যখন সধবারা সিঁদুর খেলায় উন্মত্ত ঠিক তখনই দেখি পুজোয় চারদিন ধরে অষ্টপ্রহর কাজকরা বিধবা মেয়েটি এককোণে ম্রিয়মান হয়ে দাঁড়িয়ে। তার অধিকার নেই ওই আনন্দউৎসবে যোগ দেওয়ার! আর একশো ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের সময়ে বিধবা নারীদের পরিস্থিতির কথা নিশ্চয়ই এর থেকে মন্দ বই ভালো ছিল না।
সত্যি কথা বলতে কি এই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিন্দুমাত্র তফাত পেলাম না ওকল্যাণ্ডে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ ‘ভারতের মানুষ’ শীর্ষক বক্তৃতায় বলা বিবেকানন্দের বক্তব্যের যেখানে তিনি দাবী করেছিলেন, “ভারতে সাধারণভাবে বিধবাদের বিস্তর প্রতিপত্তি, কারণ সে-দেশে সম্পত্তির বড় অংশ বিধবাদের করায়ত্ত। বস্তুতঃ বিধবারা এমন একটা স্থান অধিকার করে আছে যে, মেয়েরা এবং হয়তো পুরুষরাও পরজন্মে ‘বিধবা’ হবার জন্য সম্ভবতঃ প্রার্থনাও করে থাকে!” [৩৪] অথবা ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫, ব্রুকলিনে বলা তাঁর মন্তব্য, “স্বামী মারা গেলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার বিধবা পত্নী পান। দরিদ্রের ঘরে বিধবার কষ্ট অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতেও সেইরূপ। কখনও কখনও বৃদ্ধেরা বালিকা বিবাহ করে। এইরূপ স্বামী ধনী হইলে যত শীঘ্র মারা যায়, তাহার বিধবা স্ত্রীর পক্ষে ততই মঙ্গল। আমি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বিধবাদের প্রতি যে রূপ নির্যাতনের কথা প্রচার করা হইতেছে, ঐরূপ একটিও দেখিতে পাই নাই।” [৩৫]
এখানে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টা আর একটু স্পষ্ট হবে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (১৯০১/০২) রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রবন্ধগুচ্ছের ‘সমাজভেদ’ প্রবন্ধ থেকে কটি লাইন তুলে দিচ্ছি। “য়ুরোপের প্রথাগুলিকে যখন বিচার করিতে হয় তখন য়ুরোপের সমাজতন্ত্রের সহিত তাহাকে মিলাইয়া বিচার না করিলে, আমাদের মনেও অনেক সময় অন্যায় অবজ্ঞার সঞ্চার হয়। তাহার সাক্ষী, বিলাতি সমাজে কন্যাকে অধিক বয়স পর্যন্ত কুমারী রাখার প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করি; আমাদের নিকট এ প্রথা অভ্যস্ত নহে বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকি। অথচ বালবিধবাকে চিরজীবন অবিবাহিত রাখা তদপেক্ষা আশঙ্কাজনক, সে কথা আমরা বিচারের মধ্যেই আনি না। কুমারীর বেলায় আমরা বলি মনুষ্যপ্রকৃতি দুর্বল, অথচ বিধবার বেলায় বলি শিক্ষাসাধনায় প্রকৃতিকে বশে আনা যায়। কিন্তু আসল কথা, এ-সকল নিয়ম কোনো নীতিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয় নাই, প্রয়োজনের তাড়নে দাঁড়াইয়া গেছে। অল্প বয়সে কুমারীর বিবাহ হিন্দুসমাজের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, চিরবৈধব্যও সেইরূপ। সেইজন্যই আশঙ্কাসত্ত্বেও বিধবার বিবাহ হয় না এবং অনিষ্ট-অসুবিধাসত্ত্বেও কুমারীর বাল্যবিবাহ হয়। আবশ্যকের নিয়মেই য়ুরোপে অধিক বয়সে কুমারীর বিবাহ এবং বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে লইয়া স্বাধীন গৃহস্থাপন সম্ভবপর নহে, সেখানে বিধবা কোনো পরিবারের আশ্রয় পায় না বলিয়া তাহার পক্ষে অনেক সময়েই দ্বিতীয়বার বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক।” [৩৬]
এই প্রবন্ধেই তিনি নিজের বক্তব্যের জাস্টিফিকেশনও দিয়েছেন, “ইংরেজপরিবার ব্যক্তিবিশেষের জীবিতকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের পরিবার কুলের অঙ্গ। এইটুকু প্রভেদে সমস্তই তফাত হইয়া যায়। ইংরেজ এই প্রভেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে হিন্দুপরিবারের দরদ কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং অনেক বিষয়ে অসহিষ্ণু ও অবজ্ঞাপরায়ণ হইয়া উঠিবে। কুলসূত্রে হিন্দুপরিবারে জীবিত মৃত ও ভাবী অজাতগণ পরস্পর সংযুক্ত। অতএব, হিন্দুপরিবারের মধ্য হইতে কেহ যদি কুলত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা পরিবারের পক্ষে কিরূপ গুরুতর আঘাত, ইংরেজ তাহা বুঝিতে পারে না। কারণ, ইংরেজ-পরিবারে দাম্পত্যবন্ধন ছাড়া অন্য কোনো বন্ধন দৃঢ় নহে। এইজন্য হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হইয়াও সমাজে প্রচলিত হইল না। কারণ, জীবিত প্রাণী যেমন তাহার কোনো সজীব অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, হিন্দুপরিবারও সেইরূপ বিধবাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে বিক্ষত করিতে প্রস্তুত নহে। বাল্যবিবাহও হিন্দুপরিবার এইজন্যই শ্রেয়োজ্ঞান করে। কারণ, প্রেমসঞ্চারের উপযুক্ত বয়স হইলেই স্ত্রীপুরুষে মিলন হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত পরিবারের সঙ্গে একীভূত হইবার বয়স বাল্যকাল।
বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্য দিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে গিয়া ইংরেজকে যেমন ব্যয়বাহুল্যসত্ত্বেও জিব্রল্টার মাল্টা সুয়েজ এবং এডেন রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুকে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও এই-সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।” [৩৭] আশ্চর্য লাগে পরবর্তীকালের মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ একবারও বাল্যবিধবার শারীরিক ও মানসিক চাহিদার কথা ভাবলেন না, অথচ এর পঞ্চাশ বছর আগে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেগুলি ভেবেছিলেন, লেখালেখি করেছিলেন।
এমনকি ‘চোখের বালি’ সহ একাধিক উপন্যাসে নারী হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষাের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে বড় হয়ে উঠেছিল সমাজের রীতিনীতি, নিয়মকানুন। অবশ্য এই প্রশ্নে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে নারীবাদী শরৎচন্দ্র কেউই সাহস করে (বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিম তো সরাসরি বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলে ভূষিত করেছিলেন) সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করতে পারেন নি, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত ‘সংসার’উপন্যাসে তিনি নায়কনায়িকার বিধবা বিবাহ সংঘটন করবার হিম্মত দেখিয়েছিলেন।
সব দেখেশুনে কি মনে হয় না, বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত নয়, অনৈতিক – বহুদিনের সঞ্চিত এই বিশ্বাসের প্রতি সামান্য হলেও দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল কবির?
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় ভাই গিরীন্দ্রনাথ।এই গিরীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভাই হলেন গুণেন্দ্রনাথ। এই গুণেন্দ্রনাথেরই মেয়ে বিনয়িনীর কন্যা হলেন প্রতিমা। বিনয়িনীর বিয়ে হয়েছিল শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হিসেব করলে দেখা যাবে প্রতিমা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের অনেক দূর সম্পর্কের দৌহিত্রী। সুন্দর ফুটফুটে প্রতিমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন মৃণালিনী দেবী। তাঁর ইচ্ছে ছিল পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে দেওয়ার। অন্তরঙ্গদের বলেছিলেন, “এই সুন্দর মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করবো। আশা করি ছোটদিদি তাঁর নাতনীটিকে আমায় দেবেন।” [৩৮] কবিও জানতেন মৃণালিনীর এই ইচ্ছার কথা। শোনা যায়, প্রতিমা দেবীর যখন দশ বছর বয়স সেইসময় তাঁর অভিভাবকরা বিয়ের কথা বলতে জোড়াসাঁকোতে এসেছিলেন, কথাও বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কিন্তু তখন রথীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র পনেরো বছর। তাই কবি তাঁদের অনুরোধ করেছিলেন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য। কিন্তু সমাজের কথা ভেবে প্রতিমা দেবীর পিতা-মাতা আর অপেক্ষা করতে রাজি হননি। মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁরা মেয়ের বিয়ের ঠিক করে ফেললেন “রবীন্দ্রনাথের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সহপাঠী নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র” [৩৯] তথা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবোন কুমুদিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সঙ্গে।
তবে এই বিয়ে মোটেই সুখের হল না। ফাল্গুন মাসে বিয়ে হল, বৈশাখ মাসে প্রতিমা শ্বশুরবাড়ী গেলেন। ঠিক কয়েকদিন পরেই গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে মারা গেলেন নীলানাথ। শ্বশুরবাড়ী অপয়া অপবাদ মাথায় নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলেন প্রতিমা। হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথির সিঁদুর মুছে, পরনের রঙিন কাপড় খুলে সাদা থান পরে বিধবার সাজে সাজতে বাধ্য হলেন এগারো বছরের প্রতিমা।
পাঁচ বছর কেটে গেল। রবীন্দ্রনাথের মন এই বিধবা বালিকাটিকে দেখে হুহু করে কেঁদে ওঠে। ইতিমধ্যে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ। প্রাপ্তবয়স্ক রথীর বিয়ের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর প্রথমেই মনে পড়ল প্রতিমার কথা। জীবনসঙ্গিনী মৃনালিনীর মনোবাসনার কথা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না, তাছাড়া বিধবাবিবাহের প্রতিবন্ধক দেবেন্দ্রনাথ ও সৌদামিনী – তখন দুজনেই মারা গেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত অর্থেই এখন স্বাধীন। নিজের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর হয়েছে। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ৪ঠা আষাঢ় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৮ই জুন ১৯০৮) “বিপত্নীক মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিধবা কন্যা ছায়ার বিবাহ দেন।” [৪০] বিধবা বিবাহ প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের মানসিক উত্তরণের চাকা এবার গড়াতে আরম্ভ করেছে।
এরপর তুলে দেওয়া যাক গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে। “… রথীকাকা বিলেত থেকে ফিরে এলে রবিদাদা … বাবাকে বললেন, ‘তোমাদের উচিত প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়া। বিনয়িনীকে বল যেন অমত না করে। ওর জীবনে কিছুই হল না। এ বয়সে চারিদিকের প্রলোভন কাটিয়ে ওঠা মুশকিল। এখন না হয় মা বাপের কাছে আছে। এর পরে ভাইদের সংসারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে সেইটাই কি তোমাদের কাম্য? না বিয়ে দেওয়া ভাল, সেটা বুঝে দেখ।” [৪১]
রথীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পর্কে অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন, “অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রবধূ অমিতা ঠাকুরের কথায় আরও জানতে পারি, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ নাকি স্ত্রীকে অনেকবার এনেছিলেন। এমন কি প্ল্যানচেটে মৃণালিনী দেবীর সম্মতি না পাওয়ায় পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহের বহু সম্বন্ধ ভেঙে যায় এবং মৃণালিনী দেবীর ইচ্ছানুসারেই অবনীন্দ্রনাথের বিধবা ভাগিনেয়ী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। প্ল্যানচেট ও মিডিয়াম নিয়ে শ্রীযুক্তা অমিতা ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি আমাকে বলেন, তাঁকে এই কথা বলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, দীপেন্দ্রনাথের স্ত্রী ‘বড়মা’ হেমলতা দেবী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, ১৩৫২ সালের বৈশাখ-আষাঢ় মাসে প্রকাশিত ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় দেশবন্ধু ভগ্নী ঊর্মিলা দেবীর রচনার একটি অংশ। তাতে তিনি লিখছেন যে, তাঁর মেজদিদি অমলা দাসকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে বলেন, ‘মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি (স্ত্রী) এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো একটা সমস্যায় পড়ি, যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।” [৪২] এই প্রসঙ্গে দুটো কথা মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ আত্মা এবং প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর অবচেতন মনে সাজেসান হিসেবে ছিল মৃণালিনী এই বিয়েতে উৎসাহী ছিলেন।
যাইহোক, উদারহৃদয় গগনেন্দ্রনাথ তখনই রাজি হলেন। শুধু তাই নয়, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ের আয়োজন করলেন। অবশেষে ১৯১০ সালের ২৭ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার অবশেষে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর বিয়ে সম্পন্ন হল। দিনটি স্মরণীয় করে রাখবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই তারিখ দিয়েই পুত্র রথীন্দ্রনাথকে গোরা উপন্যাসটি উৎসর্গ করলেন। প্রতিমা দেবী পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, “১৩১৬ সাল ১৪ মাঘ আমার বিয়ের দিন। বয়স তখন ষোলো। আমার স্বামীর বয়স একুশ। পাঁচ নম্বর মামার বাড়ির পাশেই ছয় নম্বর শ্বশুর বাড়ি – তার পরদিন ১৫ মাঘ শ্বশুরবাড়ি এলুম …।” [৪৩]
প্রতিমার বিয়েতে সামাজিক বাধা কিছু এসেছিল। ঠাকুর পরিবারের কোনো কোনো শরিক নিজের বাড়ির উৎসবে রবীন্দ্র পরিবারকে নিমন্ত্রণ করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ সে সব পাত্তা দেন নি। বিয়ের চারদিন পর ২০শে মাঘ রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখলেন, “বিবাহটি বিধবাবিবাহ হয়েছে তাও বোধহয় শুনেছো। তা নিয়ে গোড়ায় একটা ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ না করাতে সেটা কেটে গেল।” [৪৪]
বর্তমান পত্রিকায় অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “পুত্রের বিবাহবাসরে পূর্ব কথা স্মরণ করে অবশ্যই কবির মনে বেদনার ঝড় উঠেছিল! একদিন তিনিই পিতার আদেশ পালন করার জন্য ভেঙে দিয়েছিলেন আর এক বিধবার বিবাহ। তাঁর আদরের ভাইপো বলেন্দ্রনাথ মারা যান মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে। পরিবারের অনেকের ইচ্ছা ছিল বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী সাহানা দেবীকে পুনরায় পাত্রস্থ করার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুনরায় বিবাহে মত ছিল না। অন্য পুত্ররা সেদিন পিতার আদেশ পালন করতে চাননি, কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, ভেঙে দিয়েছিলেন সেই বিয়ে। এজন্য তাঁর অবশ্যই আক্ষেপ ছিল। পরবর্তীকালে তাই বোধহয় তিনি বলেছিলেন, আমি ব্রাত্য, আমি সমাজচ্যুত।” [৪৫]
এই ঘটনার কিছুদিন বাদেই ঢাকার গুহঠাকুরতা পরিবারের মেয়ে লাবণ্যরেখা বিধবা হয়ে ফিরে এলে প্রিয় শিষ্য অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে কবি তার বিয়ে দিলেন। নিজের মানসিক দ্বিধা সংস্কার কাটিয়ে ক্রমাগত উত্তরণের পথে এগিয়ে যাওয়া মানবতাবাদী এই রবীন্দ্রনাথই তো আমাদের বড় আপনার। এই রবীন্দ্রনাথই চারিত্রপূজা গ্রন্থে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ, অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে এমারল্ড্ থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত বক্তৃতায় তাঁর বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত উদ্যোগের জন্য মন্তব্য করেন, “বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ ; তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার বিধবাবিবাহগ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে। – ‘হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ ! … অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবা-দিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ ; তাহারা দুর্নিবার-রিপু-বশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য ! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ !’ রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই ; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সেই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাকপটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না, এবং আমরাও তাহার চতুর্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সেও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ, সেই অকল্যাণ-নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না। আমরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা-প্রয়োগ-পূর্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।” [৪৬] এই রবীন্দ্রনাথই ‘স্ত্রীর পত্র’ লেখেন, এই রবীন্দ্রনাথই প্রশ্ন করেন,
“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?”
তথ্যসূত্র :
১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৪১-৪২
২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪
৩) চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৪৪
৪) প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৯
৫) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯৪
৬) শোভন সোম, বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৪
৭) অভিজিৎ দাশগুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ : সাহিত্যের নিঃসঙ্গ রূপকার, কালি ও কলম, ৯ জুন ২০১৫
৮) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৩১
৯) রাহুল হালদার, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় গড়তে চাইলেন বলেন্দ্রনাথ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারি ২০১৯
১০) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৩২
১১) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃষ্ঠা ২৭২
১২) রাহুল হালদার, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় গড়তে চাইলেন বলেন্দ্রনাথ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারি ২০১৯
১৩) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃষ্ঠা ২১৮
১৪) চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৯
১৫) দেবদাস জোয়ারদার, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৩১
১৬) শোভন সোম, বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৮৪
১৭) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃষ্ঠা ২৭১
১৮) চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৬৩
১৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩২
২০) চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৬৩
২১) দেবদাস জোয়ারদার, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৩২
২২) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃষ্ঠা ২৪৯
২৩) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৫৬৬
২৪) অমিতাভ চৌধুরী, একত্রে রবীন্দ্রনাথ, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১৯০
২৫) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৩০১
২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪৮
২৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ২০০
২৮) দেবদাস জোয়ারদার, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪
২৯) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৬৬
৩০) সাদ কামালী, আমার রবীন্দ্রনাথ : মৃণালিনী দেবীর পত্রকথা, মুক্তমনা ব্লগ, ১ ডিসেম্বর ২০১৪
৩১) চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ১৯১
৩২) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃষ্ঠা ২৯০
৩৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ২৪১-২৪২
৩৪) স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৪০৮
৩৫) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১২
৩৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪৮৭
৩৭) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮৬
৩৮) চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ১৯১
৩৯) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৬৯
৪০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৭
৪১) প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১১৭
৪২) অমিতাভ চৌধুরী, একত্রে রবীন্দ্রনাথ, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১১
৪৩) অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, ছায়া আছে কায়া নেই, বর্তমান, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৪৪) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ২৩৯
৪৫) অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, ছায়া আছে কায়া নেই, বর্তমান, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৪৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৪৯৮-৪৯৯

সত্যিই একবার নয় বার তিনেক লেখাটা পড়লাম। এত বিশদে একদম জানতাম না। প্রচুর পরিশ্রমের ফল আপনার এই লেখাটা। কত চরিত্র চোখের সামনে চিত্রায়িত হোলো – আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।
অনেক ধন্যবাদ।
অনেক ধন্যবাদ গৌতম বাবু।
সেই সময়ের রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক প্রতিকুলতাই প্রধান কারণ ছিল। পরবর্তী কালে তাঁর যে উত্তরণ সেটাই আমাদের ভালোবাসার রবীন্দ্রনাথ। তাই আমরা মনে রাখব।
অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে ছিল দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব।
অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে ছিল দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব।
অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা কবিগুরুর মত মানুষকে আপোষ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।তিনি আপাদমস্তক একজন হিসেবী সাংসারিক মানুষও ছিলেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁর উত্তরণ ঘটে, যাঁকে আমরা কবি, দার্শনিক হিসাবে পেয়েছি।সেই মানুষটিকেই মনে রাখি আমরা।
এমন একটি তথ্যবহুল উপহার এর জন্য অনেক ধন্যবাদ রুপকারকে।